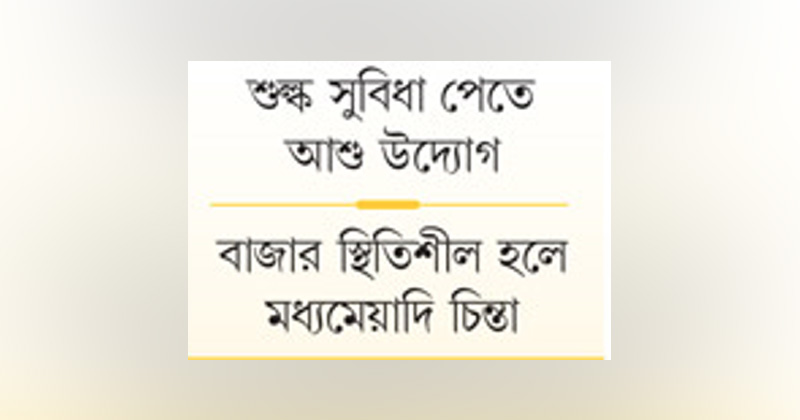মার্কিন শুল্ক দাপটে বিভিন্ন পণ্যের বিশ্ব বাজার তছনছ হয়ে গেছে, এ অবস্থায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের রফতানি বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভারতের পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্কের ওঠা-নামা এবং দেশটি থেকে ক্রয়াদেশ বাতিলের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ ও আমলারা এক হয়ে নামবে।
চীনের ওপর ৩০ শতাংশ এবং ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ছয় মাসের মধ্যে দেশদুটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে যাবে। চীন ও ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি হলে স্থায়ী শুল্ক নির্ধারণ হয়ে যাবে। এমন ঘোষণা হয়ে গেলে বাংলাদেশ কয়েক বছরের জন্য মার্কিন বাজারে রফতানির মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা করবে। আর সংশ্লিষ্ট সবাই মিলে ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে রফতানির ১০ বছরের মহাপরিকল্পনা সাজাবে।
মার্কিন বাজারে সুবিধা পাবে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। দেশটির বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর এ শুল্ক হার ঠিক করা হয়েছে। এর সঙ্গে বিদ্যমান ১৬.৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক যোগ হবে। বিজিএমইএ-এর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হওয়া তৈরি পোশাকে কার্যকর শুল্ক হার দাঁড়াচ্ছে ৩৬.৫ শতাংশ।
শুরুতে শুনতে বেশি মনে হলেও বাস্তবতা হলো অন্য দেশগুলোর তুলনায় মোটেও খারাপ অবস্থানে নেই বাংলাদেশ। যেখানে প্রতিযোগী দেশগুলোকে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের বোঝা সামলাতে হচ্ছে, সেখানে ৩৬.৫ শতাংশকে সুবিধাজনক বলেই মনে হয়।
২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৮৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাকের বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা ছিল ৯.৩ শতাংশ, যা এখন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, নতুন শুল্ক বিভিন্ন দেশকে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে এবং বাংলাদেশের জন্য এটি সুবিধাজনক হয়েছে।
সরকার এবং দেশের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা এ নিয়ে বেশ আশাবাদী। বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্ক প্রতিযোগী ভিয়েতনাম, ভারত ও চীনের চেয়ে কম। তারা বলছেন যে, নতুন কার্যকর হওয়া শুল্ক হার যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রফতানি বাড়াতে সাহায্য করবে। কারণ, মার্কিন পোশাক ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতারা তুলনামূলক কম শুল্কের জন্য বাংলাদেশকে বেছে নেবে।
বৈশ্বিক পোশাক বাজারে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিযোগী ভিয়েতনাম বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১৮.৯ শতাংশ হিস্যা নিয়ে আছে এবং তাদের ওপরও ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে তাদের পণ্যের মোট শুল্ক এর চেয়ে অনেক বেশি হবে।
ভিয়েতনামের রফতানি তালিকায় বেশিরভাগই উচ্চমূল্যের সিনথেটিক পোশাক, যেগুলোর ওপর আগে থেকেই গড়ে ৩২ শতাংশ শুল্ক ছিল। এর সঙ্গে নতুন শুল্ক যোগ হওয়ায় তাদের কার্যকর শুল্ক হার ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের বাজারে আরেক প্রধান প্রতিযোগী দেশ ভারতের হিস্যা আছে ৫.৯ শতাংশ। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রাখায় ট্রাম্প প্রশাসন দেশটির ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। তৈরি পোশাকে যুক্তরাষ্ট্রের গড় শুল্ক মিলিয়ে ভারতের কার্যকর শুল্ক হার এখন ৬৬.৫ শতাংশ।
অন্যদিকে, বিশ্বের বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী দেশ চীনের যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হিস্যা ২০.৮ শতাংশ। দেশটির কার্যকর শুল্ক হার এখন ৫৫ শতাংশ।
এদিক থেকেই ভিয়েতনাম ও চীনের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে বাংলাদেশ।
ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, কোনো রফতানি পণ্যে যদি ২০ শতাংশ মার্কিন কাঁচামাল, যেমন আমেরিকায় উৎপাদিত তুলা ব্যবহার করা হয়, তবে পণ্যের মূল্যের ওই অংশের ওপর ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক মওকুফ করা হবে।
এর মানে হলো, বাংলাদেশে তৈরি ১০ ডলারের একটি শার্টে যদি ২০ শতাংশ মার্কিন তুলা ব্যবহার করা হয়, তবে পাল্টা শুল্ক শুধু ৮ ডলারের ওপর প্রযোজ্য হবে, পুরো ১০ ডলারের ওপর নয়। কিছু বাংলাদেশি রফতানিকারক তাদের পণ্যে ইতোমধ্যে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত মার্কিন তুলা ব্যবহার করছেন, যার ফলে তাদের পণ্যে আরো কম শুল্ক প্রযোজ্য হবে।
যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ বিলিয়ন ডলার রফতানির লক্ষ্য
কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হচ্ছে। কারখানা মালিক ও ব্যবসায়ী নেতারা এ বিষয়ে আশাবাদী।
দেশে সংকটের মধ্যে আছে দুর্বল ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ, উৎপাদন ও জাহাজীকরণে বাধা এবং গ্যাস ও বিদ্যুৎ ঘাটতি।
বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির চাপ ও রফতানির মূল বাজারগুলোয় পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে।
আগামী বছর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় এলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা তুলে নেওয়া হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) হিসাবে এ সুবিধা সাত দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার।
বর্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে।
জাপান, ভারত, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের রফতানি আশাব্যঞ্জক। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি এসব অপ্রচলিত বাজারে রফতানি বর্তমান গতিতে চললে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।
বিনিয়োগ বাড়ানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে
বিদেশি বিনিয়োগেও স্থবিরতা এখনো কাটেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১১ মাসে বৈদেশিক বিনিয়োগ ২৭৭ কোটি ডলারে নেমে এসেছে, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় অর্ধেক। দেশীয় বিনিয়োগ সামান্য বাড়লেও একই সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবৃদ্ধি নেমেছে মাত্র ৬.৪ শতাংশে, ২০০৩ সালের পর যা সর্বনিম্ন। একই সঙ্গে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায়, যা ব্যাংক ঋণের ২৭ শতাংশেরও বেশি।
মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানিও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। চলতি অর্থবছরে এ খাতে এলসি খোলা কমেছে ২৫ শতাংশের বেশি। কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানিও সংকুচিত।
দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর মূল কাজগুলো এগিয়ে রেখে যেতে চায় অন্তর্বর্তী সরকার। পরে যারা ক্ষমতায় আসবে, তারা যাতে এসব পদক্ষেপে ভর করে বিনিয়োগে নতুন ঢেউ আনতে পারে।
কারখানায় গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট কাটানোর চেষ্টা
অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পেরিয়ে গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, আগের সরকারের রেখে যাওয়া বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে পুরোপুরি না পাল্টাতে পারলেও অন্তত কিছুটা স্বস্তির জায়গায় আনতে পেরেছেন তারা।
সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিল্প খাত এখনো হাঁপাচ্ছে। ভয়াবহ জ্বালানি সংকটে একের পর এক কারখানা থেমে গেছে, আর যেগুলো চালু আছে, সেগুলোর উৎপাদনশক্তি অর্ধেকে ঠেকেছে। গ্যাস আর বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় বড় শিল্পাঞ্চলগুলোতে উৎপাদন খরচ বেড়েছে হু হু করে। তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাজারে। দাম বাড়ছে পণ্য ও সেবার, আর রফতানি বাজারে প্রতিযোগিতার জায়গা হারাচ্ছে বাংলাদেশ।
এরই মধ্যে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও মালিকরা বলছেন, একটি অঞ্চলে গ্যাসের যদি কিছুটা সরবরাহ বাড়েও, অন্য জায়গায় তা কমে যায়। এ এলোমেলো বিতরণ ব্যবস্থায় কারখানাগুলো তাদের উৎপাদন পরিকল্পনা ধরে রাখতে পারছে না। অনেক প্রতিষ্ঠান ৩-৪ ঘণ্টা করে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে, আবার কোথাও দিনে ৮-১০ ঘণ্টাও গ্যাস না থাকায় কার্যত উৎপাদন হচ্ছে না।
ফলে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে প্রায় সব খাতেই। বিশেষত তৈরি পোশাকশিল্প, রফতানিমুখী প্লাস্টিক, সিরামিকস এবং স্টিল খাতে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে। এ সংকট নিরসনে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা সরকারের সঙ্গে কথা বলবে। গ্যাস-বিদ্যুতের বিকল্প সংস্থান নিয়েও তারা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবে।
কেকে/ এমএস