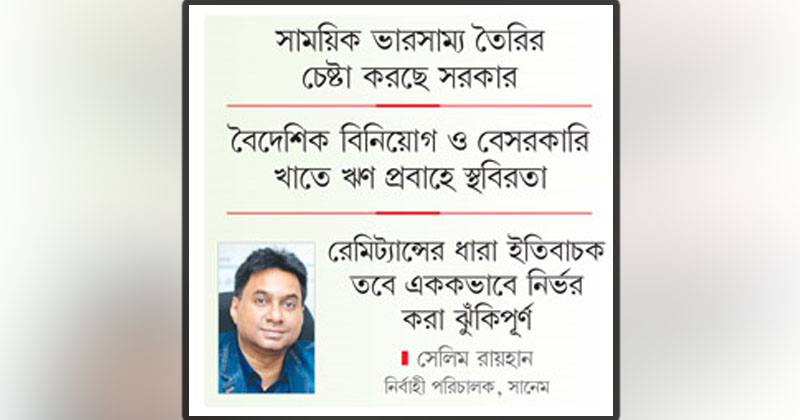চলমান অর্থনৈতিক সংকটে রেমিট্যান্সে আশার আলো দেখছে সরকার। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অনেকটা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, ফলে বিনিয়োগে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। শেয়ার বাজারে আস্থাহীনতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব আহরণে ক্রমাগত ঘাটতি এবং উন্নয়ন ব্যয়ে ধীরগতিও ভোগাচ্ছে অর্থনীতিকে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রত্যাশার তুলনায় কম ঋণ প্রবৃদ্ধি এবং রফতানি, আমদানি ও বৈদেশিক সহায়তার মন্থর গতি, যা সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির গতি কমিয়ে দিচ্ছে।
এই যখন দেশের পরিস্থিতি তখন অভাবনীয় হারে বেড়ে চলা প্রবাসী আয় সরকারকে কিছুটা স্বস্তির জায়গা করে দিয়েছে। একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখা যাচ্ছে, অন্যদিকে আমদানি ব্যয়ের চাপ সামাল দিতেও রেমিট্যান্স হয়ে উঠেছে মূল অবলম্বন। চলমান অর্থনৈতিক চাপে সরকার এখন রেমিট্যান্সনির্ভর একটি সাময়িক ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করছে, যার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর একটি সম্ভাব্য পথ খুঁজছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসের প্রথম ২৪ দিনে দেশে ২২৪ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ৬৬ কোটি ৫২ লাখ ৬০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। এর আগে গত এপ্রিলে দেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৭৫ কোটি ১৯ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এবং গত মার্চে দেশের ইতিহাসে যেকোনো এক মাসের চেয়ে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স ৩২৮ কোটি ৯৯ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৫২ কোটি ৭৬ লাখ ৫০ হাজার ডলার এবং জানুয়ারিতে ২১৮ কোটি ৫২ লাখ ৩০ হাজার ডলার। এমন ধারাবাহিক প্রবাহই প্রমাণ করে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় বর্তমানে মূলত প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে বাড়তি রেমিট্যান্স, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, টাকার অবমূল্যায়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে আস্থার পুনঃস্থাপন এই সবকটি কারণে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে। তবে রফতানি আয়ের গতি বাড়ানো, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং স্থানীয় উৎপাদন খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে রেমিট্যান্স নির্ভরতা কমাতে হবে। অন্যথায় এই একক উৎসের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভবিষ্যতে অর্থনীতিকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।
অন্যদিকে, এই বিপুল রেমিট্যান্স প্রবাহ সত্ত্বেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবস্থা খুব একটা উন্নত হয়নি। চলতি বছরের ২৭ মে পর্যন্ত মোট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৫.৮০ বিলিয়ন ডলার এবং বিপিএম৬ অনুযায়ী তা ২০.৫৬ বিলিয়ন ডলারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমদানি বিল পরিশোধ, ঋণের কিস্তি এবং রফতানি আয়ের দুর্বল প্রবাহের কারণে রেমিট্যান্সের সুফল পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ) নিয়ে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) প্রকাশিত সাম্প্রতিক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির নানা দিক উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, রফতানি আয় ও প্রবাসী আয়ের ইতিবাচক প্রবাহ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে এবং এতে করে গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীলতাও ধীরে ধীরে ফিরতে শুরু করেছে। সামষ্টিক অর্থনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, তৃতীয় প্রান্তিকে কৃষি ও শিল্প খাতে কিছুটা প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও কৃষিঋণের পরিমাণ ৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা উদ্বেগজনক। অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ে ২ দশমিক ৭৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও তা কাক্সিক্ষত মাত্রায় পৌঁছেনি।
এমসিসিআই দেশের ব্যাংকিং খাতের দুরবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলছে, গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক অনিয়ম, ঋণ কেলেঙ্কারি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুর্বলতার ফলে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। এসব অনিয়ম অর্থনীতির অগ্রগতির বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা ব্যাংকিং খাতে আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং সামগ্রিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারে সহায়ক হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে এমসিসিআই।
বৈদেশিক খাতে আশাবাদের পাশাপাশি কিছু গুরুতর দুর্বলতাও চিহ্নিত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় ১৪ শতাংশের বেশি কমেছে। একই সময়ে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে (এফডিআই) ২৬ শতাংশ হ্রাস দেখা গেছে, যা প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এমসিসিআই-এর মতে, বিদেশি বিনিয়োগের বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয় এবং এতে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হুমকির মুখে পড়তে পারে।
মার্চ ২০২৫ শেষে দেশীয় ঋণের মোট প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.১৯ শতাংশ, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১২.১৪ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ৭.৫৭ শতাংশে, যেখানে আগের বছর ছিল ১০.৪৯ শতাংশ। লক্ষ্য ছিল ৯.৮০ শতাংশ। অন্যদিকে, সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে হয়েছে ১৫.১২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় (১৮.৬৩ শতাংশ) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত ১৯.৮০ শতাংশের লক্ষ্য থেকে কম।
২০২৫ সালের মার্চ মাসে এনবিআর ৩৪,৬৬৯.৭৫ কোটি টাকা কর আদায় করে, যা আগের বছরের মার্চের তুলনায় ৯.৬৪ শতাংশ বেশি। তবে এই মাসের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪২,০৯৩.৪৩ কোটি টাকা যেখানে ১৭.৬৪ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে।
চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়নের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৬.৬৫ শতাংশ, যা গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছর একই সময়ে এই হার ছিল ৪২.৩০ শতাংশ।
চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে উন্নয়ন সহযোগীদের বৈদেশিক সহায়তার প্রাপ্তি কমে দাঁড়িয়েছে ৪.৮১ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের বছরের তুলনায় ১৪.৫৬ শতাংশ কম। একই সময়ে বৈদেশিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি আরও কমে ৩.০১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫৮.৪৩ শতাংশ কম।
তবে তৈরি পোশাকশিল্পে সাম্প্রতিক সময়ে স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা রফতানি প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্চ ও এপ্রিল মাসে রফতানি আয় ও প্রবাসী আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যা ডলার সরবরাহে কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে। এর পাশাপাশি মার্চ মাসে আমদানির প্রবৃদ্ধিও বেড়েছে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর মার্চে আমদানি ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দেয়।
মূল্যস্ফীতি নিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, টানা তিন মাস নিম্নমুখী থাকার পর মার্চ মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে, যা ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ।
এমসিসিআই-এর প্রতিবেদনে সার্বিক মূল্যায়নে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি কিছুটা পুনরুদ্ধারের পথে থাকলেও এই অগ্রগতি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করতে হলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সেগুলো হলো ব্যাংকিং খাতের কাঠামোগত সংস্কার, নীতিনির্ধারণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি। এই তিনটি শর্ত পূরণ না হলে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার দীর্ঘস্থায়ী হবে না।
সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) এর নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম রায়হান বলেন, ‘গত কয়েক মাসের রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই খাতে তেমন কোনো তাৎক্ষণিক ঝুঁকি তৈরি হওয়ার সম্ভবনা নেই। এর একটি বড় কারণ হলো বিভিন্ন কারণে হুন্ডি ব্যবসা বড় ধাক্কা খেয়েছে। ফলে প্রবাসীরা এখন বেশি করে ফরমাল চ্যানেল ব্যবহার করছেন। যার ফলেই আমরা রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করছি এবং ধারণা করছি, এই ধারা কিছুটা সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।’
তিনি বলেন, ‘দেশের অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যস্ফীতি ও দারিদ্র্যের চাপের সময় অতীতেও দেখা গেছে, প্রবাসীরা তাদের পরিবারকে সহায়তা করতে বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলেও রেমিট্যান্সে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। তবে ঈদের মৌসুম পার হওয়ার পর সাময়িকভাবে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা কমে আসতে পারে।’
সেলিম রায়হান বলেন, যদিও রেমিট্যান্স বর্তমানে অর্থনীতির একটি শক্তিশালী দিক হিসেবে কাজ করছে, তবে শুধু এই একটি উৎসের উপর ভিত্তি করে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে নির্ভর করাকে আমি সঠিক মনে করি না। কারণ, এই প্রবৃদ্ধি সাময়িকও হতে পারে, এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটও খুব একটা অনুকূল নয়। ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহ হঠাৎ কমে গেলে তা অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি করতে পারে। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই বিকল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উৎস খুঁজতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, রফতানির বহুমুখীকরণ খাতগুলোতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’
কেকে/ এমএস