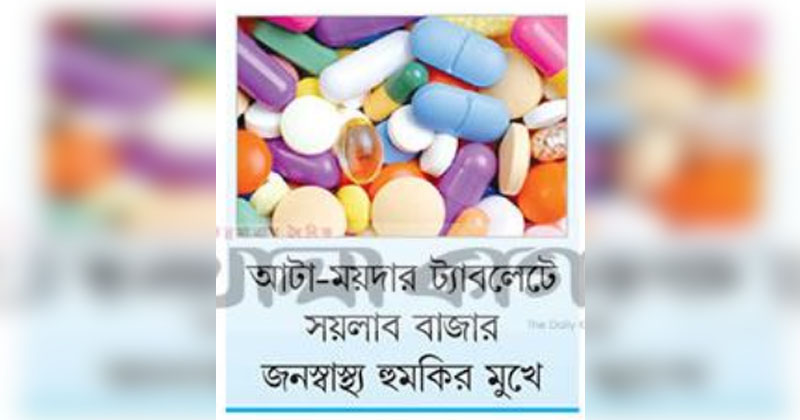জুলাই অভ্যুত্থানপরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে আবারো সক্রিয় হয়ে ওঠেছে ভেজাল ও নকল ওষুধের কারবারিরা। শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চল, সবখানেই ছড়িয়ে পড়ছে নকল ও ভেজাল ওষুধ। এতে উদ্বিগ্ন রোগী ও চিকিৎসকরা। কিছু কিছু ওষুধের ক্ষেত্রে ভেজাল ও নকলের উপদ্রব এতটাই বেড়েছে যে, চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকে ওষুধগুলোর ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন, এমনকি কেউ কেউ বন্ধও করে দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।
অ্যালবুমিন ইনজেকশন নামের একটি বর্তমানে ব্যাপকভাবে নকল হচ্ছে। অষুধটি বড় ধরনের অস্ত্রপচার বা গুরুতর আঘাত পরবর্তী চিকিৎসায় রক্তে প্লাজমার পরিমাণ বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে অনেক চিকিৎসক এ অষুধ ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ বলেন, ‘বাজারে এর নকল এতটাই বেড়ে গেছে যে, আমরা এটা দেওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছি।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ফার্মেসি বিভাগের সঙ্গে ওই গবেষণায় যৌথভাবে কাজ করেছে জাপানের কানাজাওয়া ইউনিভার্সিটি এবং জার্মানির এবাহার্ড কার্ল ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক। গবেষণাটিকে তারা দুইভাগে ভাগ করছেন, যেখানে প্রথমভাগে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিন ধরনের গ্যাস্ট্রিক ও অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের ১৮৯টি নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলোর মান পরীক্ষা করে দেখেন গবেষকরা। সেগুলো হলো ইসোমিপ্রাজল, সেফিক্সিম এবং অ্যামোক্সিসিলিন-ক্লাভুলানিক অ্যাসিড। এর মধ্যে ইসোমিপ্রাজল গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় নিরসনে ব্যবহার হয়। আর সেফিক্সিম এবং অ্যামোক্সিসিলিন-ক্লাভুলানিক অ্যাসিড মূলত অ্যান্টিবায়োটিক, যা সাধারণত নিউমোনিয়া ও প্রস্রাবের সংক্রমণের মতো রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
নমুনাগুলোর মধ্যে ৭৮ দশমিক ছয় শতাংশ খুচরা বিক্রেতাদের থেকে এবং ২০ দশমিক নয় শতাংশ সংগ্রহ করা হয় ওষুধের পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে। ২০২২ সালে গবেষণাটির প্রধম ধাপের ফলাফলে প্রকাশিত হয়। সেখানে ঢাকায় সংগৃহীত নমুনায় নকল, ভেজাল এবং নিম্নমানের ওষুধের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ শতাংশ। গবেষণার দ্বিতীয় ধাপে ঢাকার বাইরের জেলাগুলো থেকে গ্যাস্ট্রিক ও অ্যান্টিবায়োটিকে ওই তিন ধরনের ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে ঢাকার থেকে প্রায় দ্বিগুণ, অর্থাৎ প্রায় ২০ শতাংশের মতো নকল, ভেজাল এবং নিম্নমানের ওষুধ পেয়েছেন গবেষকরা।
বিজ্ঞানবিষয়ক আন্তর্জাতিক সাময়িকী নেচারে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র ঢাকা শহরে বিক্রি হওয়া অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ ওষুধই নকল, ভেজাল এবং নিম্নমানের। ঢাকার বাইরে এ পরিস্থিতি আরো খারাপ বলে জানাচ্ছেন গবেষকরা। অনেক ক্ষেত্রে আটা-ময়দা দিয়ে বানানো নকল বড়ি বিক্রির ঘটনাও দেখা যাচ্ছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ফার্মেসি বিভাগের সঙ্গে ওই গবেষণায় যৌথভাবে কাজ করেছে জাপানের কানাজাওয়া ইউনিভার্সিটি এবং জার্মানির এবাহার্ড কার্ল ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক। গবেষণাটিকে তারা দুইভাগে ভাগ করছেন, যেখানে প্রথমভাগে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিন ধরনের গ্যাস্ট্রিক ও অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের ১৮৯টি নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলোর মান পরীক্ষা করে দেখেন গবেষকরা। সেগুলো হলো ইসোমিপ্রাজল, সেফিক্সিম এবং অ্যামোক্সিসিলিন-ক্লাভুলানিক অ্যাসিড। এর মধ্যে ইসোমিপ্রাজল গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় নিরসনে ব্যবহার হয়। আর সেফিক্সিম এবং অ্যামোক্সিসিলিন-ক্লাভুলানিক অ্যাসিড মূলত অ্যান্টিবায়োটিক, যা সাধারণত নিউমোনিয়া ও প্রস্রাবের সংক্রমণের মতো রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নমুনাগুলোর মধ্যে ৭৮ দশমিক ছয় শতাংশ খুচরা বিক্রেতাদের থেকে এবং ২০ দশমিক ৯ শতাংশ সংগ্রহ করা হয় ওষুধের পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে। ২০২২ সালে গবেষণাটির প্রধম ধাপের ফলাফলে প্রকাশিত হয়। সেখানে ঢাকায় সংগৃহীত নমুনায় নকল, ভেজাল এবং নিম্নমানের ওষুধের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ শতাংশ।
গবেষণার দ্বিতীয় ধাপে ঢাকার বাইরের জেলাগুলো থেকে গ্যাস্ট্রিক ও অ্যান্টিবায়োটিকে ওই তিন ধরনের ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে ঢাকার থেকে প্রায় দ্বিগুণ, অর্থাৎ প্রায় ২০ শতাংশের মতো নকল, ভেজাল এবং নিম্নমানের ওষুধ পেয়েছেন গবেষকরা।
নকল ও ভেজাল ওষুধ ঠেকাতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে ২০২৩ সালে ওষুধ ও কসমেটিক আইন পাস করে বাংলাদেশ সরকার। এরপর ওই আইনে এখন পর্যন্ত কাউকে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়ার নজির নেই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নকল ও ভেজাল অষুধ রোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) ভাইস-প্রেসিডেন্ট এস এম নাজের হোসাইন বলেন, ‘আমরা সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি। যার কারণে কঠোর আইন থাকার পরও বাজারে ভেজাল ও নকল ওষুধের দৌরাত্ম্য দেখা যাচ্ছে।’
স্বাস্থ্য খাতের গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেসব ওষুধের চাহিদা এবং দাম বেশি, সেগুলোরই নকল ও ভেজাল বাজারে বেশি দেখা যাচ্ছে।
বাংলাদেশের ওষুধের মান নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক আন্তর্জাতিক সাময়িকী নেচারে যে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশে সেটির নেতৃত্বে ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের স্কুল অব মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মহিউদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ‘ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের জেলা, সবখানেই আমরা এটা পেয়েছি। তবে ঢাকার বাইরে আটা-ময়দার এ রকম নকল ওষুধ বেশি দেখা গেছে।’
২০২৪ সালের মার্চে ঢাকা ও বরিশালে অভিযান চালিয়ে আটা, ময়দা এবং সুজি ব্যবহার করে নকল ওষুধ উৎপাদনকারী একটি দলের পাঁচজন সদস্যকে গ্রেফতার করেছিল গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের কাছ থেকে তখন বিভিন্ন ধরনের প্রায় পাঁচ লাখ নকল অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ধার করা হয়। দলটির সদস্যরা প্রায় ১০ বছর ধরে নকল ওষুধ তৈরি ও বিক্রি করে আসছিল বলে জানান পুলিশের কর্মকর্তারা।
গবেষক ও ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষক ড. মহিউদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, ‘যেহেতু চাহিদা রয়েছে এবং দামও ভালো পাওয়া যাচ্ছে, ফলে সহজে লাভবান হওয়ার চিন্তা থেকেই একশ্রেণির মানুষ এসব ওষুধের নকল বের করছে।’
নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়াকে জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, ‘টাকা খরচ করে এসব ওষুধ কিনে মানুষ কেবল প্রতারিতই হচ্ছে না, বরং এর ফলে তাদের ভোগান্তি বাড়ছে; এমনকি অনেকে মারাও যাচ্ছেন।’
কেকে/এআর