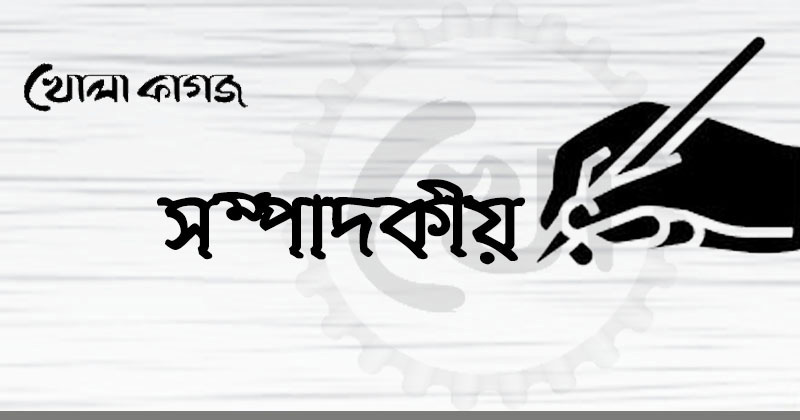বাংলাদেশের অর্থনীতি এক ভয়াবহ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) এবং শেয়ারবাজার- এই তিনটি আর্থিক খাতই বিপর্যয়ের মুখে। খেলাপি ঋণের দুষ্টচক্র, দুর্বল নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি এবং বাজারে জাঙ্ক কোম্পানির আধিপত্য- সব মিলিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেশের অর্থনীতি।
ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অস্থিরতা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। এই খাতগুলোর মধ্যে ব্যাংক খাতকে ‘অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড’ বা চালিকাশক্তি বলা হয়। কিন্তু এই খাতই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিগত বছরগুলোতে। বর্তমানে দেউলিয়ার পর্যায়ে আছে ১২টি ব্যাংক এবং অতিমাত্রায় দুর্বল অবস্থায় রয়েছে আরো ১৫টি ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী- ২০২৪ সালে ব্যাংক খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার নেমে এসেছে মাত্র ৩ দশমিক ০৮ শতাংশে- ২০২৩ সালে এ হার ছিল ১১ দশমিক ৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ কমেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় এ হার সবচেয়ে কম। বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন-২০২৪’ অনুযায়ী, পাকিস্তানে ব্যাংক খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার ২০ দশমিক ৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ভারতে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ।
অথচ বাংলাদেশে মাত্র ৩ দশমিক ০৮ শতাংশ। যেখানে কমপক্ষে ১০ শতাংশ মূলধন থাকলে ব্যাংক খাতকে টিকে থাকার মতো অবস্থায় আছে বলে ধরা হয়। ফলে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় এক ডজন ব্যাংককে মার্জারের ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে শুধু এক্সিম ব্যাংক, পদ্মা ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংক-বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিডিবিএল) চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে। এসব ব্যাংকের পাশাপাশি তালিকায় থাকা অন্য ব্যাংকগুলো তখন পড়ে যায় বিপাকে।
বিশেষ করে দুর্বল ব্যাংকগুলো থেকে গ্রাহকরা আমানত তুলে নেওয়ায় দেউলিয়ার পথে চলে যায় ব্যাংকগুলো। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর মার্জার বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রতি রেজল্যুশন অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট-২০২৫ প্রণয়ন করেছে। এর মাধ্যমে যেকোনো ব্যাংক টেকওভার করতে পারবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই ক্ষমতাবলে দুর্বল ৫টি ব্যাংক মার্জারের সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যে ব্যাংক খাতে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। ওই সব ব্যাংক থেকে গ্রাহকরা টাকা তুলে নিচ্ছেন। ব্যাংক খাতের একাধিক ক্ষত সামাল দিয়ে যখন ব্যাংকগুলো ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল তখনই আবারো মার্জার ইস্যু সামনে এনে এসব ব্যাংককে খাদের কিনারে নিয়ে আসা হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চাপিয়ে দেওয়া মার্জারে আর্থিক খাত বা ব্যাংক খাত স্বাভাবিক হবে না। এ জন্য সরকারের নানামুখী সেবা যেমন- বিদ্যুৎ-গ্যাস বিল, ভূমি রেজিস্ট্রেশনের বিল, পাসপোর্ট-সংক্রান্ত সেবার কাজ এবং যে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের টাকা গচ্ছিত আছে, তা এসব দুর্বল ব্যাংককে সহায়তায় ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ব্যাংককে বাঁচানো সম্ভব। তবে সরকার এ পথে হাঁটছে না। এই সরকার ঘোষণা দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মধ্যেই নির্বাচন হবে। অথচ গভর্নরের মার্জারের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগবে ৩-৪ বছর। ফলে আগামীর নির্বাচিত সরকারকেও ব্যাংক একীভূতকরণের বিষয়টি বিপাকে ফেলতে পারে। এই বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।
দুর্বল ব্যাংকগুলোকে বাঁচানোর সমাধান একীভূতকরণ নয় বরং আন্তর্জাতিক আর্থিক দাতা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন-আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইডিবি থেকে অর্থায়ন বা ঋণের টাকা নিয়ে ব্যাংকগুলোকে সচল করা। মার্জার খারাপ নয়; তবে এটা হতে হবে ভলান্টারি। ব্যাংক ইচ্ছে করলে যাবে। চাপিয়ে বা জোর করে একীভূত করতে গেলে সেটি হিতে-বিপরীত হবে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। দুর্বল ব্যাংকগুলোর প্রতি গ্রাহকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং ব্যাংকগুলোকে বাঁচাতে কেবল মার্জারই যথেষ্ট নয়- নিতে হবে বাস্তবমুখী আর্থিক পরিকল্পনা।
কেকে/ এমএস