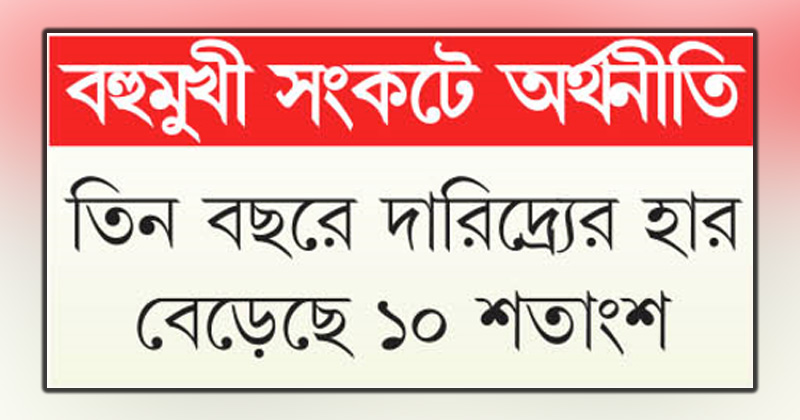দেশে দারিদ্র্যের হার গত তিন বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে। অথচ ২০২২ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয় ও ব্যয় জরিপে এ হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। একই সময়ে অতি দারিদ্র্যের হারও বেড়েছে। ২০২২ সালে এ হার ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, যা তিন বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্য দুটিই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
এখনো দেশের প্রায় ১৮ শতাংশ পরিবার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে; অর্থাৎ যে কোনো সময় তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে পারে। সরকারি কাজে আগের চেয়ে ঘুষের প্রবণতা কমলেও ৫২ শতাংশ মানুষ বলেছেন, এখনো ঘুষ ছাড়া কাজ হচ্ছে না আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ভোগ করতে হচ্ছে ৩৬ শতাংশ মানুষকে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার এলজিইডি মিলনায়তনে দেশের অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা নিয়ে দেশব্যাপী সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে দারিদ্র্য বৃদ্ধির এই চিত্র প্রকাশ করে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিশিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)। ‘ইকনোমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউজহোল্ড লেবেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক গবেষণার ফলাফল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান।
ঘুষ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা
গবেষণায় আরো উঠে এসেছে, সরকারি কাজে আগের তুলনায় ঘুষের প্রবণতা কিছুটা কমলেও এখনো সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। জরিপে অংশ নেওয়া ৫২ শতাংশ মানুষ বলছেন, ঘুষ ছাড়া সরকারি কাজ করা যায় না। একই সঙ্গে ৩৬ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, নানা ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তাদের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে।
গবেষণা পত্রে বলা হয়, জুলাই অভ্যুত্থানের এক বছর পর এবং এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের বাস্তব অর্থনীতি বহুমুখী সংকটের মুখোমুখি। গত কয়েক বছরে একের পর এক ধাক্কা সামলাতে হয়েছে অর্থনীতিকে। প্রথমে ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত কোভিড সংকট, এরপর ২০২৩ সালে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি এবং ২০২৪-২৫ সালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সব মিলিয়ে একটি ধারাবাহিক সংকটের মধ্য দিয়ে দেশ এগোচ্ছে।
দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের উল্টোযাত্রা
গত তিন বছরে দারিদ্র্যের চিত্র উদ্বেগজনকভাবে উল্টো পথে গেছে। দারিদ্র্যের হার প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২৭.৯৩ শতাংশে। একই সঙ্গে অতি দারিদ্র্যের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের মোট পরিবারের প্রায় ১৮ শতাংশ এখনো দারিদ্র্যসীমার ওপরে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে, যে কোনো সময় তারা দরিদ্র শ্রেণিতে নেমে যেতে পারে।
পিপিআরসির গবেষণায় নতুন কিছু ঝুঁকির দিকও উঠে এসেছে। দীর্ঘমেয়াদি রোগ ও তার আর্থিক চাপ এখন অর্ধেকের বেশি পরিবারকে ভোগাচ্ছে ৫১ শতাংশ পরিবারের অন্তত একজন সদস্য ক্রনিক অসুস্থতায় আক্রান্ত। চরম দরিদ্র পরিবারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বা ২৪ শতাংশ নারীপ্রধান, যা বৈষম্যের এক নতুন মাত্রা যোগ করছে।
ঋণের বোঝা ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা
ঋণের বোঝাও বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে, সবচেয়ে নিচের ৪০ শতাংশ পরিবারের ঋণ তাদের সঞ্চয়ের অন্তত দ্বিগুণ, আর দরিদ্রতম ৪ শতাংশ পরিবারের ঋণ গত ছয় মাসেই বেড়েছে ৭ শতাংশ। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাও প্রকট হয়েছে; দরিদ্রতম ১০ শতাংশ পরিবারের ৮.৮ শতাংশ গত মাসে অন্তত একদিন পুরোপুরি না খেয়ে ছিল এবং ১২ শতাংশ পরিবারকে গত সপ্তাহে খাবার বাদ দিতে হয়েছে। পাশাপাশি এসডিজি অগ্রগতিও থমকে গেছে; এখনো ৩৬ শতাংশ পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে।
কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি নাজুক
কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি নাজুক। কাজে যুক্তদের মধ্যে ৩৮ শতাংশই প্রকৃত অর্থে ছদ্মবেশী বেকার, তারা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার কম কাজ করছে। নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার এখনো মাত্র ২৬ শতাংশে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে, কর্মরতদের প্রায় ৪৫ শতাংশ স্ব-কর্মসংস্থানে যুক্ত, যা আয়ের অনিশ্চয়তা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।
রেমিট্যান্স ও ভোক্তা বাজারের স্থিতি
এই সংকটের মাঝেও কিছু স্থিতিস্থাপকতার কথা জানিয়েছে পিপিআরসি। ১৫ শতাংশ পরিবার মাসে গড়ে ২৯ হাজার টাকা রেমিট্যান্স পাচ্ছে, যদিও এর বেশিরভাগই প্রবাহিত হচ্ছে আয়ের শীর্ষ ৫০ শতাংশ পরিবারের দিকে। গড় বার্ষিক পারিবারিক ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা, যা মিলে প্রায় ২১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অভ্যন্তরীণ ভোক্তা বাজার তৈরি করেছে। একই সঙ্গে ডিজিটাল সক্ষমতার বিস্তার ঘটেছে, ৭৪ শতাংশ পরিবার এবং যুবসম্পৃক্ত পরিবারগুলোর ৮০ শতাংশের হাতে স্মার্টফোন রয়েছে। প্রায় ৪৫ শতাংশ পরিবার এখন সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করছে এবং পারিবারিক প্রয়োজনে জ্বালানির উৎস কাস্টমাইজ করছে।
আশাবাদ ও হতাশার মধ্যেও একটি স্পষ্ট শ্রেণি বৈষম্য দেখা গেছে। নীচের ১০ শতাংশ পরিবারের ৩৩ শতাংশ এবং নীচের ২০ শতাংশ পরিবারের ২৪ শতাংশ ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হলেও, শীর্ষ ২০ শতাংশ পরিবারের ৬২ শতাংশ আশাবাদী। তারপরও সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, দেশের ৫৪ শতাংশ মানুষ এখনো হাল ছাড়তে রাজি নয়।
অনুষ্ঠানে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, জবাবদিহীতামূলক রাষ্ট্র গড়তে মানুষের জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সে বিবেচনা থেকেই নীতি পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। প্রায়ই বিভিন্ন আলোচনায় অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা বলা হয়। তবে জনগণের হয়রানির কথা বলা হয় না। অথচ হয়রানির কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি কমে যায়। এ প্রেক্ষিতে অর্থনীতির পরিকল্পনায় জনমুখী দৃষ্টি থাকা খুবই জরুরি। শুধু জিডিপির ওপর আলোচনাটা সীমাবদ্ধ না রেখে সমতা, ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীনতা ও নাগরিকের কল্যাণ নিয়ে আলোচনা বাড়াতে হবে।
তিনি বলেন, এখন পাঁচটি নতুন ঝুঁকির বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। প্রথমত, দীর্ঘস্থায়ী রোগের বোঝা বাড়ছে, এর জন্য নতুন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দরকার। দ্বিতীয়ত, নারীপ্রধান পরিবারগুলো সবচেয়ে ঝুঁকিতে আছে, যাদের আলাদা সহায়তা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, ঋণের চাপ বাড়ছে, যা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চতুর্থত, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে, যা ভবিষ্যতের জন্য বড় উদ্বেগ। পঞ্চমত, এখনো ৩৬ শতাংশ মানুষ নন-স্যানিটারি টয়লেট ব্যবহার করছে, যা নিরাপদ স্যানিটেশনের বড় চ্যালেঞ্জ।
তিনি আরো বলেন, এছাড়া দেশে কর্মসংস্থানের জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেকারত্ব এখন এক ধরনের দুর্যোগে রূপ নিয়েছে। এ সংকট মোকাবিলায় এখনই বড় ধরনের উদ্যোগ এবং কার্যকর নীতিমালা প্রয়োজন।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পরে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রত্যাশা বেড়েছে। একই সময়ে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা পরিবার পর্যায়ে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির আশঙ্কা তৈরি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে হালনাগাদ ও ব্যাপক ডেটার অভাব ছিল, যা নীতি নির্ধারণের জন্য জরুরি ছিল। এ গবেষণাটি সেই ডেটার অভাব পূরণে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।
কেকে/ এমএস