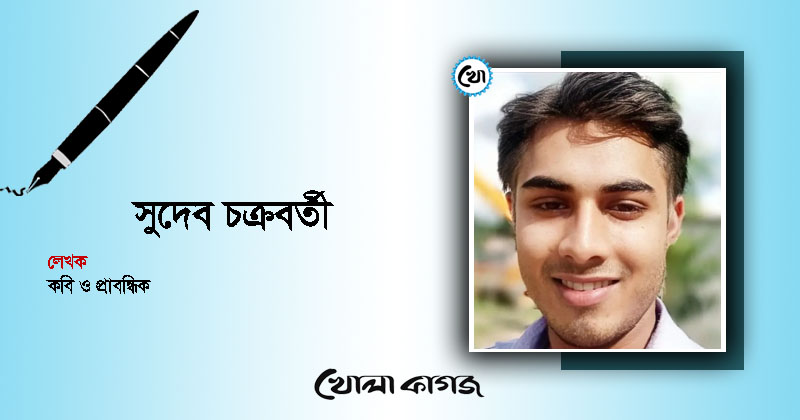আবারো রাজপথে শিক্ষকরা। ৩ দফা দাবিতে তারা আন্দোলন করছেন। কিন্তু শিক্ষকদের এ অহিংস বা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন রূপ নিল সহিংসতায়। বহু শিক্ষক আহত হলেন, রক্তাক্ত হলেন এবং গ্রেফতার হলেন। এবারের আন্দোলনে শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান দাবি হলো ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণের দাবি। কিন্তু শিক্ষা উপদেষ্টা জানিয়ে দিলেন এ দাবি পূরণের কোনো যৌক্তিকতা নেই। শিক্ষা উপদেষ্টার এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মাধ্যমে কেউ কেউ তার বক্তব্য সমর্থন করছে, আবার কেউ কেউ তীব্র সমালোচনা করছে।
ফলে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই কি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণের দাবি অযৌক্তিক? কয়েকটি পেশার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের যোগ্যতা তা হলো স্নাতক বা সমমানের দ্বিতীয় বিভাগ। তাদের বেতনের গ্রেড ১৩তম। কিন্তু সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একই যোগ্যতায় সহকারী বেতনের গ্রেড ১০ম। সুতরাং এখানে বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট। আবার এই যে পুলিশ শিক্ষকদের পেটাল, রক্তাক্ত করল, সেই পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের যোগ্যতাও স্নাতক বা সমমান। তারাও কিন্তু ১০ম গ্রেডের বেতন পান। এই যে আহত শিক্ষকদের হসপিটালে যারা সেবা দিচ্ছেন, সেই নার্সদের নিয়োগ পদে যোগ্যতা এইচএসসি (ডিপ্লোমা ইন নার্সিং)। তাদের বেতন গ্রেডও ১০ম। কৃষিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও আমরা যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাই উপ-সহকারী কৃষি অফিসার পদে নিয়োগের যোগ্যতা (চার বছরের কৃষি ডিপ্লোমা) এইচএসসি। তাদের বেতন গ্রেডও ১০ম প্রস্তাবিত। আবার মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগের যোগ্যতা স্নাতক বা সমমানের। তাদের বেতন গ্রেড ১০ম ও ৯ম। সবচেয়ে বড় কথা, যেটা বললে বৈষম্যের চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একই কারিকুলাম একই পাঠ্যক্রম ও একই ক্লাসের শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষাদান করা হয় পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে, তাদেরও শিক্ষক পদে নিয়োগ যোগ্যতা স্নাতক দ্বিতীয় বিভাগ। তারা ১০ম গ্রেড পান।
এখন কথা হলো শিক্ষকদের দাবি যৌক্তিক না অযৌক্তিক, সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারত, বিতর্ক হতে পারত। কিন্তু শিক্ষকদের পেটানো হলো কেন? রক্তাক্ত করা হলো কেন? শিক্ষকরা কি ভাঙচুর করেছিল? অগ্নিসংযোগ করেছিল? সরকার পতনের লক্ষ্যে অবরোধ করে দেশের সম্পদ বিনষ্ট করেছিল? তাহলে তাদের অহিংস আন্দোলনকে রাষ্ট্র কেন সহিংস বানাল? এটা রাষ্ট্রের অন্যায়। এটাই ফ্যাসিবাদ। ২০২৪-এ রেজিম চেঞ্জের পর তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা হলো ফ্যাসিবাদের পতনে। এখন যেটা হচ্ছে সেটা কি ফ্যাসিবাদ নয়? এর আগে আমরা দেখেছি শিক্ষকরা বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করেছেন। সেখানেও রাষ্ট্র কর্তৃক দমন-পীড়ন করা হয়েছে। মূলত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন শিক্ষক এ সমাজেরই অংশ। ফলে অন্যদের বেতন বৃদ্ধি পেলে শিক্ষকদের বেতন কেন বাড়বে না?
সুতরাং শিক্ষকদের দাবি যৌক্তিক। তাদের রক্তাক্ত করা শুধু অযৌক্তিকই নয়, অন্যায়ও বটে। এ চিত্র শুধু বাংলাদেশে। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে তাকালেও আমাদের লজ্জা পেতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষকদের যে বেতন কাঠামো তা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো বিশেষকরে ভারত, নেপাল, ভুটান এমনকি আফগানিস্তানের চেয়েও নিচে। মানে অন্যসব দেশে শিক্ষকতাকে অন্তত মধ্যবিত্ত পেশা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হলেও আমাদের দেশে সহকারী দাপ্তরিক মান বা একেবারে নিম্নস্তরে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষকরা যখন বেতন বৃদ্ধির জন্য কথা বলেন, তখন তাদের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃক নিপীড়ন করা হয়। শিক্ষকের সম্মান তখন রাজপথে লুটিয়ে পড়ে। অথচ চীন, তাইওয়ান, মালেশিয়ায় শিক্ষকদের উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়। এ কারণেই তারা উন্নত। ইসরায়েল বা ব্রিটেনে প্রায় সকল বাবা-মা চান তাদের সন্তানরা পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিক। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকদের ভিআইপি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের দেশে তার বিপরীত চিত্র।
অথচ আমাদের এই ভূখণ্ডে শিক্ষকের মর্যাদা সর্বোচ্চ ছিল। বিশেষকরে আমরা যদি প্রাচীন ভারতের দিকে তাকাই। তখন যারা পাঠদান করতেন তারা দরিদ্র ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থই তাদের আয়ের উৎস ছিল। বৈদিক যুগে শিক্ষার্থীগণকে দুই ভাগে ভাগ করা হত। একটি হল উপকুর্বাণ, অন্যটি হল নৈষ্ঠিক। যারা গুরুগৃহের পাঠ শেষ করে আপন গৃহে ফিরে যেত বা গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত তাদের বলা হতো উপকুর্বাণ, আর যারা পাঠ শেষে আচার্যের বাড়িতেই থেকে যেত বা সংসার জীবনে ফিরে যেত না এবং ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করত তাদের বলা হতো নৈষ্ঠিক। এবার আসি গুরুদক্ষিণা বা শিক্ষকের বেতন প্রসঙ্গে। প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা। বিদ্যা কি কখনো পয়সার মূল্যে বিক্রি হয়? তাই আচার্য কোনো মূল্য চেয়ে নিত না। যেহেতু সেসময়ে একটা কথা প্রচলিত ছিল-গুরু দক্ষিণা প্রদান না করে শিক্ষা লাভ করলে সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়, তাই গুরুগৃহ ত্যাগের মুহূর্তে শিক্ষার্থীরা যে যার সাধ্যমত গুরু দক্ষিণা দিয়ে গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করত। অবশ্য বিত্তশালী পিতা বা রাজার পুত্ররা গুরুকে গো সম্পদ বা ধন প্রদান করত, দরিদ্ররা সামর্থ্যানুযায়ী দিত আর যার সামর্থ্য নেই সে কুশগুচ্ছ গুরুর চরণে দক্ষিণা হিসেবে প্রদান করত। গুরু তাতেই খুশি।
এ প্রসঙ্গে বলে রাখি তৎকালীন সময়ে আচর্য শব্দের অর্থ ছিল যিনি বিনামূল্যে শিক্ষাদান করেন। এ আচার্যদের মধ্যে যারা আশ্রম খুলে স্থায়ীভাবে শিক্ষাদান করতেন বা কয়েক হাজার ছাত্রের ভরণ-পোষণের ব্যয় ভার গ্রহণ করতেন তাদের বলা হতো কুলপতি আচার্য। কুলপতি আচার্য হলো আজকের যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের Chancellor-এর নামান্তর। মৌর্য যুগেও বৈদিক যুগের মতন শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। এ সময়ে আমরা তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি। মধ্য যুগে গড়ে ওঠে পাঠশালা ও মক্তব। তখনো শিক্ষকরা আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না, কিন্তু তাদের মর্যাদা কম ছিল না। কিন্তু আজ শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা যেমন নেই, তেমনি মর্যাদাও নেই। ব্রিটিশ আমলে আমরা দেখেছি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারার পি. জে হার্টগকে উচ্চ বেতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়, কিন্তু কাজী মোতাহার হোসেনের মতো পণ্ডিতকে বেতন দেওয়া মাত্র ২০০ টাকা! কবি জসীমউদ্দীন তো শিক্ষকতা পেশা ছেড়েই দিলেন।
পাকিস্তান আমল থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বহু ধারা-উপধারায় বিভক্ত। অথচ প্রয়োজন ছিল একমুখী ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা, একটি কার্যকর শিক্ষানীতি। ১৯৬২ সালে শিক্ষানীতির জন্য আমাদের রক্তদানের ইতিহাস রয়েছে। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে ৫৪ বছর হলো। এত দিনেও আমাদের দেশে একটা শিক্ষানীতি নেই। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী একটা দেশের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত ৮ শতাংশ। আমাদের দেশে দেয়া হয় ২ শতাংশেরও কম। ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও শিক্ষা খাতে উন্নয়ন ঘটেনি। অপ্রয়োজনে যুদ্ধবিমান কেনার টাকা আমাদের রাষ্ট্রের কোষাগারে থাকে, মন্ত্রীদের বিলাসবহুল গাড়ি কেনার অর্থ জোটে, কিন্তু শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির কথা বললেই তা অযৌক্তিক হয়ে যায়। ঠিক এ কারণেই আমাদের দেশের শিক্ষার মান নিম্নগামী।
বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ শিক্ষক এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়োজিত, যাদের অনেকে মাস শেষে পূর্ণ বেতন পান না, নানা প্রশাসনিক জটিলতায়। ২০২২ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষকতাকে ‘আদর্শ পেশা’ হিসেবে বিবেচনা করে। বাকি ৮৭ শতাংশ চায় করপোরেট, প্রযুক্তি বা প্রশাসনিক খাতে যেতে। শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তার অভাবও স্পষ্ট। ২০২৩ সালের জরিপ অনুযায়ী, বেসরকারি স্কুলের ৪৩ শতাংশ শিক্ষক ১০ হাজার টাকার নিচে বেতন পান। অথচ এ শিক্ষকই সকাল ৮টা থেকে বিকাল পর্যন্ত ক্লাস নেন, বাড়ি ফিরে কোচিং করেন, কারণ সংসার চালাতে হয়।
বিশ্বের উন্নত দেশে যেখানে শিক্ষকরা ন্যূনতম আয়ের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি বেতন পান সেখানে আমাদের অনেক শিক্ষক ন্যূনতম জীবনমানও নিশ্চিত করতে পারছেন না। এ বাস্তবতায় শিক্ষকদের চলমান আন্দোলন মোটেই অযৌক্তিক নয়। বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল, তা কাঠিয়ে উঠতে যে বিষয়টি কাজ করেছিল তা হলো শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া। আমরা তার উল্টোটা করি। ফলে শিক্ষকরা পর্যাপ্ত বেতন পান না। বারবার তাদের রাস্তায় নামতে হয়। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচাতে, শিক্ষার মান বাড়াতে, শিক্ষকদের দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে শিক্ষকদের দাবি বিবেচনা করা উচিত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না শিক্ষায় বিনিয়োগই উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ।
লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক
কেকে/এআর