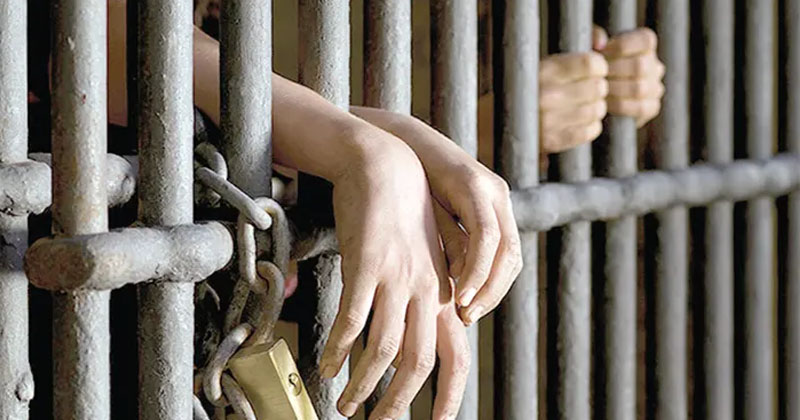বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা বর্তমানে এক গভীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে শাস্তিকেন্দ্রিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে গড়া এ ব্যবস্থায় আজ সবচেয়ে বড় সংকট সৃষ্টি করেছে কারাগারের ভয়াবহ অতিরিক্ত ভিড়। সরকারি হিসাবে জেলগুলোর ধারণক্ষমতা প্রায় ৪২,৮৮৭ জন, অথচ বর্তমানে বন্দির সংখ্যা ৭৭ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, যা ধারণক্ষমতার প্রায় দেড়গুণ বেশি অর্থাৎ মোট সংখ্যার বৃদ্ধি প্রায় একশ আশি শতাংশ। এ সংকট কেবল প্রশাসনিক সমস্যা নয়, এটি বিচারব্যবস্থা, মানবাধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলছে। ২০২৫ সালে কারা অধিদপ্তর জানায়, গত পাঁচ বছরে বন্দির সংখ্যা বার্ষিক গড়ে ছয় শতাংশ হারে বেড়েছে, যা বিচারব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে।
জনাকীর্ণ কারাগার বাস্তবে বন্দিদের মৌলিক অধিকারকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে পর্যাপ্ত ঘুমানোর জায়গা, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে কারাবন্দিদের যে পরিমাণে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম, মানসিক পরামর্শ বা দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পাওয়ার কথা, সেগুলো প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে বন্দিরা মানসিক চাপ, হতাশা, উত্তেজনা ও সহিংসতামুখী আচরণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে অন্তত ত্রিশ শতাংশ বন্দি নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হন যা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে।
বাংলাদেশের জেল ব্যবস্থায় পুনর্বাসনের তাত্ত্বিক ধারণা থাকলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতা ভীষণ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বন্দিদের প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং, ব্যক্তিগত উন্নয়ন কিংবা পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগগুলো অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে প্রায় অকার্যকর হয়ে যায়। ০২৫ সালের শুরুতে একটি যৌথ গবেষণা বলছে, দেশে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের প্রায় আটচল্লিশ শতাংশই কোনো না কোনো পর্যায়ে চাকরি বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাবে পুনরায় অপরাধের পথে চলে যান।
২০২৪ সালের আগস্টে প্রকাশিত ‘টাঙ্গাইল সেন্ট্রাল জেলে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের পুনঃএকত্রীকরণের চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক গবেষণায় দেখা যায়, মুক্তির পর বন্দিরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন তা হলো পরিবারিক সম্পর্কের অবনতি, সামাজিক সহায়তা অভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং আত্মবিশ্বাস হারানো। অনেক পরিবার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সামাজিক চাপ, ভয় বা অবিশ্বাসের কারণে গ্রহণ করতে আগ্রহী থাকে না। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, যাদের পারিবারিক সহায়তা ছিল না তাদের পুনর্মিলনের ব্যর্থতার হার প্রায় দ্বিগুণ। সমাজতাত্ত্বিকরা বলছেন, পরিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়া কোনো পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী সফলতা আনতে পারে না।
বাংলাদেশে পুনর্বাসনকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ থাকলেও অনেক জায়গায় তা অনিয়ম, অপ্রশিক্ষিত জনবল এবং ভুল ব্যবস্থাপনার কারণে ব্যাহত হচ্ছে। সম্প্রতি চাঁদপুরের একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি এবং প্রশিক্ষণের অভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। স্থানীয় তদন্তে উঠে আসে, কেন্দ্রটিতে পর্যাপ্ত মনিটরিং ছিল না এবং বন্দিদের কাউন্সেলিং বা প্রশিক্ষণ প্রায়ই অনিয়মিত ছিল। এ ঘটনা দেশের পুনর্বাসনব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ছাড়া পুনর্বাসনের কোনো প্রচেষ্টাই বাস্তবে কার্যকর হতে পারে না।
বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে অপরাধ মোকাবিলার প্রধান উপায় হিসেবে শাস্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কঠোর শাস্তি দিলে অপরাধ কমবে এ ধারণা এখনো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, শুধু শাস্তি দিয়ে অপরাধ রোধ করা যায় না। বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড, দুর্বিষহ জীবনযাত্রা এবং পুনর্বাসনের অভাব অপরাধীদের আরো কঠোর, প্রতিশোধপরায়ণ বা বিপজ্জনক করে তুলতে পারে। আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, মাত্র শাস্তিমুখী ব্যবস্থা পুনরায় অপরাধের ঝুঁকি অন্তত ত্রিশ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়।
প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের পাশাপাশি অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীরাও (ঔাঁবহরষব ঙভভবহফবৎং) জেল সংকটের একটি অংশ। যদিও আইন অনুযায়ী তাদের সাধারণ কারাগারে রাখা নিষেধ, তবুও সংশোধনমূলক কেন্দ্রগুলোতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ভিড় এবং সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা কর্মসূচির ঘাটতি রয়েছে। ফলস্বরূপ, এ কেন্দ্রে আসা অনেক কিশোর অপরাধী সংশোধিত না হয়ে আরো কঠোর অপরাধের পথে চালিত হতে পারে। তাদের সঠিক পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে বিশেষজ্ঞ জনবল ও কেন্দ্রগুলোর মানোন্নয়ন জরুরি।
প্রবেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬০ হলো এমন একটি আইন যা অপরাধীদের হেফাজতে না রেখে সমাজের মধ্যে নজরদারি ও শর্তযুক্ত মুক্তির সুযোগ দেয়। অ-সহিংস, ক্ষুদ্র বা প্রথমবার অপরাধকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ আইন অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। বিশ্বজুড়ে প্রবেশন ব্যবস্থার সফলতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রবেশনের মাধ্যমে অপরাধীরা সমাজে থেকেই সংশোধনের সুযোগ পান, পরিবার ও চাকরি হারান না, আর রাষ্ট্রের ওপরও আর্থিক চাপ কমে। বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হলেও এর বিস্তার এখনো অপর্যাপ্ত। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রবেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হলে কারাগারের ভিড় উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে দেশগুলো পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব দেয় তাদের পুনরায় অপরাধের হার কম। নরওয়েতে পুনরায় অপরাধের হার মাত্র কুড়ি শতাংশ, যেখানে কঠোর শাস্তিনির্ভর দেশগুলোতে সেই হার পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশের ওপরে। এই দেশগুলো অপরাধীর মূল কারণ বুঝতে চায়, তাদের দক্ষতা বাড়ায়, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেয় এবং সমাজে সম্মানজনকভাবে ফিরে যাওয়ার পথ তৈরি করে। তাদের জেলগুলোকে বলা হয় সংশোধন কেন্দ্র। বাংলাদেশের জন্য এ মডেল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারে।
সম্প্রতি কারা অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে ‘সংশোধন পরিষেবা বাংলাদেশ’ করা হয়েছে। এ পরিবর্তন শুধু নামের নয়, এটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। রাষ্ট্রচিন্তা এখন শাস্তির সঙ্গে সংশোধনকেও সমান গুরুত্ব দিতে চাইছে। নতুন নীতিমালায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কারা শিক্ষা কার্যক্রম, মনোবৈজ্ঞানিক কাউন্সেলিং এবং মুক্তির পর সমাজে পুনর্বাসন এসব বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবে এসব উদ্যোগ কতটা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে, তা নির্ভর করছে বাজেট, জনবল ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর।
অ-সহিংস এবং অপেক্ষাকৃত ছোট অপরাধের ক্ষেত্রে কমিউনিটি সার্ভিস বা সমাজসেবামূলক কাজকে কারাবাসের বিকল্প শাস্তি হিসেবে আরো বেশি ব্যবহার করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুদ্র চুরির দায়ে অভিযুক্তকে জেলে না পাঠিয়ে, তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থানীয় হাসপাতাল বা স্কুলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এ বিকল্প শাস্তির মাধ্যমে অপরাধী তার কৃতকর্মের জন্য সমাজের কাছে জবাবদিহি করে, সমাজে থেকেই সংশোধন হয় এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এটি কারাগারের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ভিড় কমানোর একটি বাস্তবসম্মত এবং মানবিক উপায়।
বাংলাদেশে জেল ভিড়ের অন্যতম বড় কারণ হলো বিচার-পূর্ব আটক। দেশের মোট বন্দির প্রায় ষাট শতাংশই হলো এমন ব্যক্তি যাদের মামলার বিচার এখনো শেষ হয়নি। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া ও আদালতের মামলার চাপ এ সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। দুই হাজার পঁচিশ সালে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, বিচার-পূর্ব আটক কমানো গেলে জেল সংকট অন্তত চল্লিশ শতাংশ কমবে।
অহিংস অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা, কমিউনিটি সেবা, প্রবেশন, পরামর্শপ্রদান প্রোগ্রাম বা পুনর্মিলন প্রক্রিয়া এসব ব্যবস্থাকে আরো বেশি প্রয়োগ করা গেলে কারাগারের চাপ কমবে। বিশ্বব্যাপী বহু দেশ অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তির ধরন ঠিক করে, কিন্তু বাংলাদেশে এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারাদণ্ডই প্রধান সমাধান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপরাধবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় বিকল্প শাস্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।
নিয়মিতভাবে নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার কর্মী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের দ্বারা কারাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে বন্দিদের অধিকার সুরক্ষিত হবে এবং প্রশাসনিক দুর্বলতাগুলো দ্রুত শনাক্ত করে সমাধান করা সম্ভব হবে।
কারা সংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় সংস্থা, আদালত, কারা প্রশাসন, এনজিও এবং সমাজ সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। পুনর্বাসন কার্যক্রম শুধু কারাগারে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, সমাজেও এর প্রসার ঘটাতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং স্থানীয় প্রশাসন যদি মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের গ্রহণে সহযোগিতামূলক ভূমিকা নেয়, তবে পুনঃএকত্রীকরণ সহজ হবে। বর্তমানে দেশে কয়েকটি এনজিও এ কাজে যুক্ত থাকলেও তাদের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন।
বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পথ হলো শাস্তি ও পুনর্বাসনের সমন্বয়। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি বজায় থাকা উচিত, তবে সাধারণ অপরাধে পুনর্বাসনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিচার-পূর্ব আটক কমানো, বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন, পুনর্বাসন কেন্দ্রের মানোন্নয়ন এবং পরিবার ও সমাজভিত্তিক সহযোগিতা এসবের সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া এ সংকট কাটানো সম্ভব নয়। একটি মানবিক, ন্যায়সঙ্গত এবং নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে পুনর্বাসনকে বিচারব্যবস্থার কেন্দ্রে আনতেই হবে।
লেখক : কলামিস্ট
কেকে/এমএ