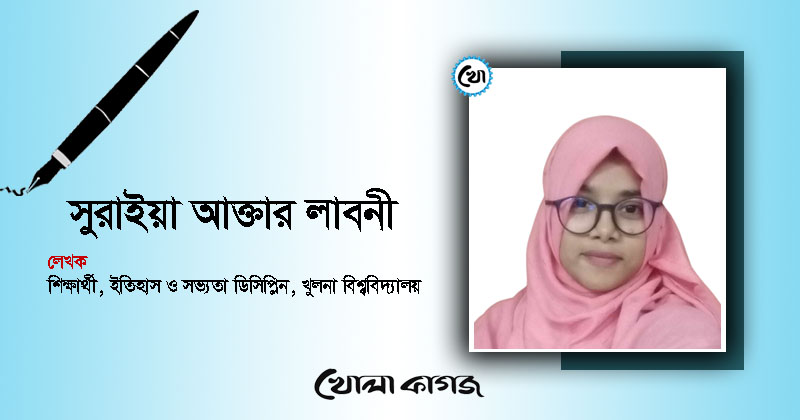বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও খুলনা খালিশপুরে এমন মানুষ আছে, যাদের মাতৃভাষা এখনো তাদের পরিচয়কে প্রভাবিত করে। খুলনা খালিশপুরের বিহারি জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাই সেখানকার বাচ্চারা বাংলায় কথা বলছে, অথচ তাদের দাদা-দাদিরা এখনো উর্দুতে। একই পরিবারের মধ্যে দুই প্রজন্ম, দুই ভাষার ভুবন। এই ভিন্নতা শুধু ভাষার নয়; এটি পরিচয় ও স্বীকৃতির এক অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি। তারা বলছে, ‘আমরা বিহারি, কিন্তু বাংলাদেশেই আমাদের জীবন।’
খালিশপুর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি শিল্পনগরী, যেখানে ১৯৪০-৫০-এর দশকে জুট মিল, কারখানা ও রেলওয়ের জন্য শ্রমিকদের আগমন ঘটে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় ভারতের বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য উর্দুভাষী মুসলিমরা সামাজিক ও ধর্মীয় নিরাপত্তার আশায় পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। তারা শুধু শ্রমিকই ছিলেন না; ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী হিসেবে কেউ কেউ এখানে তাদের জীবন গড়ে তুলেছেন। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর তারা স্থানীয় অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠলেও তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি আলাদা থেকে যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। যুদ্ধকালে রাজনৈতিক বিভাজন ও পাকিস্তানপন্থি কিছু গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা উর্দুভাষী সম্প্রদায়ের ওপর সন্দেহ ও অবিশ্বাস নেমে আসে। স্বাধীনতার পর অনেক বিহারি পাকিস্তানে চলে যায়, অন্যরা থেকে যায় বাংলাদেশে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাদের স্বদেশি হিসেবে স্বীকার করে না, আর বাংলাদেশ সরকার তাদের পূর্ণ নাগরিক মর্যাদা দিতে দেরি করে। ফলে দীর্ঘকাল কাটাতে হয় নাগরিকহীন হয়ে বিশেষ মর্যাদায়।
খালিশপুরের ১, ৩ ও ৮ নম্বর ক্যাম্পে আজও তিন প্রজন্মের বিহারি বাস করছে। প্রথম প্রজন্ম এখনো উর্দুভাষী, দ্বিতীয় প্রজন্ম উর্দু-বাংলার মিশ্রণ ব্যবহার করে, আর নতুন প্রজন্ম সম্পূর্ণভাবে বাংলায় কথা বলে। ভাষা পরিবর্তন হলেও সামাজিক অবস্থান বদলায়নি। রাষ্ট্র তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও সমাজে তাদের ‘বহিরাগত’ হিসেবেই চিহ্নিত করে। এ যেন বাংলাদেশের মাটিতে এক অঘোষিত সম্প্রদায় যাদেরকে একটি কাঠামোগত জেলখানার ভেতর সারাজীবন কাটাতে হয়।
শিক্ষা ও চাকরি শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যম নয়; এটি নাগরিক মর্যাদার প্রতীক। কিন্তু খালিশপুরে আজও শিক্ষার সুযোগ সীমিত। খালিশপুরের একটি এনজিও স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ আছে, কিন্তু শিক্ষাজীবনের পরবর্তী ধাপের পথ প্রায় বন্ধ। অনেকেই খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়, তবে সরকারি চাকরিতে ‘বিহারি’ পরিচয়ই প্রধান বাধা। সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। যদিও দরিদ্রতা কিছুটা বাধা হিসেবে কাজ করে, তবে যেখানে শিক্ষা অবকাঠামো রয়েছে, সেখানে দরিদ্রতা ব্যাখ্যার একমাত্র কারণ নয়। ফলে অনেক বিহারি পরিবার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে, কারণ সম্ভাব্য সফলতা সত্ত্বেও পরিচয় তাদের জন্য শত্রু। এই বৈষম্যের মূল শিকড় রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় স্তরে। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক দায় বর্তমান প্রজন্মের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। যাদের জন্ম এই স্বাধীন রাষ্ট্রে, তারা কেন পরিচয়ের দণ্ডভোগ করবে? ইতিহাসে যেমন জার্মানির নাৎসি অতীতের দায় পরবর্তী প্রজন্ম বহন করেনি, তেমনি বাংলাদেশেরও উচিত মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রজন্মকে ন্যায্য নাগরিক মর্যাদা দেওয়া।
এই ভোগান্তি দূর করার মূল সমাধান হলো সমান শিক্ষা ও নাগরিক সুযোগের নিশ্চয়তা। যখন তারা বাঙালিদের সমানভাবে সরকারি অফিস, শিক্ষক, উকিল, জজ ও করপোরেট খাতে সুযোগ পাবে, তখন ভিন্ন পরিচয়বোধ আর বাধা থাকবে না। তাই বিহারিদের জন্য শিক্ষায় বিশেষ সুযোগ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষায় কোটার ব্যবস্থা এবং সরকারি চাকরিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এভাবে তারা নিজ যোগ্যতায় সমাজের মূলধারায় যুক্ত হতে পারবে এবং বাংলাদেশের নাগরিক মর্যাদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে।
খালিশপুরের গলিপথে এখন উর্দু ও বাংলার মিলন দেখা যায়। এই মিলনই বাংলাদেশি বহুত্ববাদী সমাজের সম্ভাব্য প্রতিচ্ছবি। কিন্তু যতদিন ‘বিহারি’ নামটি অপমান বা বৈষম্যের প্রতীক হিসেবে থাকবে, ততদিন স্বাধীনতার পূর্ণতা আসবে না। রাষ্ট্রের উচিত- এই মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুকে একটাই পরিচয়ে চিহ্নিত করা, সেটি হলো বাংলাদেশি। ভাষার পার্থক্য নয়, নাগরিক অধিকারের সাম্যই স্বাধীনতার সত্যিকারের মানে। এই উপলব্ধিই হোক রাষ্ট্র ও সমাজের নতুন প্রতিশ্রুতি। এই সংকটের সমাধান ভাষা নয়, সুযোগ ও স্বীকৃতি। রাষ্ট্র যদি নাগরিক সুযোগের আওতায় আনে, উচ্চশিক্ষায় কোটার ব্যবস্থা করে, উর্দুভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কলেজ স্থাপন করে, তাহলে এই সম্প্রদায় নিজ যোগ্যতায় সমাজের মূলধারায় যুক্ত হতে পারবে।
জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রক্রিয়া সহজ করা, সরকারি চাকরিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া- এসব কার্যকর পদক্ষেপ তাদের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু যতদিন ‘বিহারি’ নামটি অপমান বা বৈষম্যের প্রতীক হিসেবে থাকবে, ততদিন স্বাধীনতার পূর্ণতা আসবে না। রাষ্ট্রের উচিত- এই মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি শিশুকে একটাই পরিচয়ে চিহ্নিত করা সেটি হলো বাংলাদেশি। ভাষার পার্থক্য বৈষম্য নয়, সমমর্যাদার নাগরিক অধিকার প্রদানই হবে তাদের প্রতি ন্যায্যতা। রাষ্ট্র হবে সবার সেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণকে ঘিরে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না।
লেখক : শিক্ষার্থী, ইতিহাস ও সভ্যতা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
কেকে/এআর