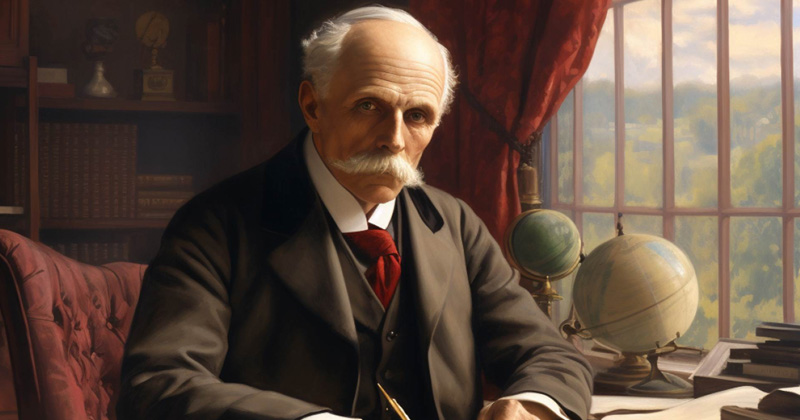আলফ্রেড মার্শাল ছিলেন একজন প্রভাবশালী ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, যাকে ‘বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির জনক’ বলা হয়। তার শ্রেষ্ঠ কাজ ‘প্রিন্সিপলস অফ ইকোনমিকস’ (১৮৯০) আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করে। এই বইয়ে তিনি চাহিদা ও সরবরাহ, প্রান্তিক উপযোগিতা এবং উৎপাদন খরচের মতো মৌলিক ধারণাগুলোকে সুসংহতভাবে উপস্থাপন করেন। গণিতে দক্ষ হলেও তিনি অর্থনীতিকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করতে চেয়েছিলেন।
ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি জন মেইনার্ড কেইনসের মতো অনেক অর্থনীতিবিদ তৈরি করেন। মার্শাল অর্থনীতিকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত, একাডেমিক পেশা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার কাজের মধ্যে ‘দি ইকোনমিকস অফ ইন্ডাস্ট্রি’ (মেরি পেলি মার্শালের সঙ্গে), ‘ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ট্রেড’ এবং ‘মানি, ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স’ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৪ সালে তার মৃত্যুর পর, ক্যামব্র্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগ ও লাইব্রেরির নামকরণসহ বিভিন্নভাবে তাকে স্মরণ করা হয়।
আলফ্রেড মার্শাল ছিলেন একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এবং তার সময়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একজন। তাকে প্রায়শই ‘বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির জনক’ বলা হয়। তার কাজ, বিশেষ করে তার সাড়া জাগানো বই ‘প্রিন্সিপলস অব ইকোনমিকস’, আধুনিক অর্থনীতিকে একটি নতুন দিশা দেখিয়েছিল।
মার্শালের জন্ম হয়েছিল লন্ডনের বারমন্ডসেতে। ছোটবেলা থেকেই তার গণিতে বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং ক্যামব্র্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গণিতে অসাধারণ ফল করেন। তবে, গণিতের কঠিন হিসাবের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি দর্শন এবং নীতিশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার মনে হয়েছিল, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ছাড়া মানুষের জীবনমানের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। এই ভাবনা থেকেই তিনি অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। মার্শাল বিশ্বাস করতেন, অর্থনীতির প্রধান কাজ হলো মানুষের বস্তুগত অবস্থার উন্নতি ঘটানো, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।
১৮৭৭ সালে তিনি মেরি পেলি মার্শালকে বিয়ে করেন। মেরিও একজন অর্থনীতিবিদ ছিলেন। এই দম্পতি একসঙ্গে ‘দি ইকোনমিকস অফ ইন্ডাস্ট্রি’ বইটি লেখেন, যা ইংল্যান্ডে অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই বইটি মার্শালের খ্যাতি এনে দেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের একজন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
মার্শালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ‘প্রিন্সিপলস অফ ইকোনমিকস’ (Principles of Economics), যা ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটি বহু বছর ধরে ইংল্যান্ডে অর্থনীতির প্রধান পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি অর্থনীতির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে একটি সুসংগত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
চাহিদা ও সরবরাহ : মার্শালই প্রথম এই দুটি ধারণাকে একত্রিত করে একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখান কীভাবে বাজারের ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। তার আঁকা এই লেখচিত্রগুলো আজও অর্থনীতির শিক্ষার্থীদের কাছে অপরিহার্য।
প্রান্তিক উপযোগিতা : এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করে যে, একটি পণ্যের অতিরিক্ত একক ব্যবহারের মাধ্যমে ভোক্তা যে অতিরিক্ত তৃপ্তি পান, তার মূল্য কতখানি।
উৎপাদন খরচ : তিনি উৎপাদন খরচকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসাবে ভাগ করেন এবং দেখান কীভাবে বিভিন্ন ধরনের খরচ পণ্যের মূল্যকে প্রভাবিত করে।
মার্শাল তার বইগুলোতে জটিল গাণিতিক তত্ত্বগুলো ফুটনোট এবং পরিশিষ্টে রাখতেন, যাতে সাধারণ পাঠক সহজেই মূল ধারণাগুলো বুঝতে পারেন। তার লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিকে কেবল পণ্ডিতদের জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষের জন্যও সহজবোধ্য করে তোলা।
ক্যামব্র্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে মার্শালের দীর্ঘ কর্মজীবন ছিল। তিনি অর্থনীতির জন্য একটি নতুন স্বতন্ত্র বিভাগ তৈরির চেষ্টা করেন, যা ১৯০৩ সালে সফল হয়। তার অনেক শিক্ষার্থী পরবর্তীতে বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠেন, যার মধ্যে নোবেল বিজয়ী জন মেইনার্ড কেইনস অন্যতম।
মার্শাল ১৯২৪ সালে ৮১ বছর বয়সে ক্যামব্র্রিজে তার নিজ বাড়িতে মারা যান। অর্থনীতিতে তার অবদান ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি অর্থনীতিকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত, একাডেমিক এবং বৈজ্ঞানিক পেশা হিসেবে গড়ে তোলেন, যা বিংশ শতাব্দীর বাকি অংশে এই ক্ষেত্রকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।
ক্যামব্র্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের লাইব্রেরি এবং সমিতি, এমনকি ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগও তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। তার বাড়িটিও তার সম্মানে ‘মার্শাল হাউস’ নামে পরিচিত।
আলফ্রেড মার্শাল শুধু একজন তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক। তার কাজ আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং আজও অর্থনীতির শিক্ষার্থীরা তার মৌলিক ধারণাগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে।
প্রারম্ভিক জীবন ও শিক্ষা
মার্শাল লন্ডনের বারমন্ডসেতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উইলিয়াম মার্শাল (১৮১২-১৯০১) এবং রেবেকা অলিভার (১৮১৭-১৮৭৮)-এর দ্বিতীয় পুত্র। তার বাবা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের একজন ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার ছিলেন এবং মা বাবার কাছ থেকে সম্পত্তি পেয়েছিলেন। মার্শালের দুই ভাই ও দুই বোন ছিল এবং অর্থনীতিবিদ রাল্ফ হাত্রি তার একজন আত্মীয় ছিলেন।
মার্শালের পরিবার ছিল ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত রক্ষণশীল। তার প্রপিতামহ, ‘রেভারেন্ড উইলিয়াম মার্শাল’, ডেভনশায়ারের এক কিংবদন্তী ধর্মযাজক ছিলেন। উইলিয়াম মার্শাল ছিলেন একজন কঠোর ধর্মপ্রাণ ইভাঞ্জেলিক্যাল। এই কঠোর পারিবারিক পরিবেশ মার্শালের কাজের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলে তিনি দার্শনিক আদর্শবাদের মতবাদকে সমর্থন করতেন বলে কিছু পণ্ডিত মনে করেন।
মার্শাল ক্ল্যাপহামে বেড়ে ওঠেন এবং মার্চেন্ট টেলরস’ স্কুল ও ক্যামব্র্রিজের সেন্ট জনস কলেজে পড়াশোনা করেন। গণিতে তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং ১৮৬৫ সালে ক্যামব্র্রিজ ম্যাথমেটিক্যাল ট্রাইপোস পরীক্ষায় তিনি সেকেন্ড রেংলার হন। তবে, মার্শাল একটি মানসিক সংকটের মুখোমুখি হন যা তাকে পদার্থবিদ্যা ছেড়ে দর্শনে মনোনিবেশ করতে পরিচালিত করে। তিনি অধিবিদ্যা দিয়ে তার অধ্যয়ন শুরু করেন, বিশেষ করে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে জ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে।
অধিবিদ্যা তাকে নীতিশাস্ত্রের দিকে নিয়ে যায়, বিশেষত সিডগউইকিয়ান উপযোগিতাবাদে। নীতিশাস্ত্র থেকে তিনি অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে শ্রমিক শ্রেণির উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি অপরিহার্য।
মার্শাল মনে করতেন, অর্থনীতির প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষের বস্তুগত অবস্থার উন্নতি ঘটানো, যা কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গেই সম্ভব। জর্জবাদ, উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী শিক্ষা, দারিদ্র্য এবং অগ্রগতির প্রতি তার আগ্রহ তার প্রাথমিক সামাজিক দর্শনের প্রভাবকে তার পরবর্তী কাজ ও লেখায় প্রতিফলিত করে।
কর্মজীবন ও শিক্ষকতা
১৮৬৫ সালে মার্শাল ক্যামব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৮৬৮ সালে নৈতিক বিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি মেরি পেলিকে পড়াতেন, যিনি পরে ক্যামব্রিজের নিউনহাম কলেজে প্রভাষক হন।
১৮৭৭ সালে তাদের বিবাহের কারণে মার্শালকে সেন্ট জনস কলেজের ফেলোশিপ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। এই সময়েই তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজ, ব্রিস্টল-এর প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন, যা পরে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। সেখানে তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও অর্থনীতি পড়াতেন এবং ১৮৮১ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।
১৮৮২ সালে তিনি রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে ফিরে আসেন এবং ১৮৮৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিয়ল কলেজে টিউটোরিয়াল ফেলো হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর ব্রিস্টল ছেড়ে চলে যান। ১৮৮৫ সালে তিনি ক্যামব্র্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৯০৮ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন।
এই সময়ে তিনি হেনরি সিডগউইক, ডব্লিউ. কে. ক্লিফোর্ড, বেঞ্জামিন জওয়াত, উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন্স, ফ্রান্সিস ইসিড্রো এজওয়ার্থ, জন নেভিল কেইনস এবং জন মেইনার্ড কেইনস সহ অনেক ব্রিটিশ চিন্তাবিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মার্শাল ক্যামব্র্রিজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা ক্রমবর্ধমান আয়, ফার্মের তত্ত্ব এবং কল্যাণ অর্থনীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিত। তার অবসরের পর ক্যামব্রিজ অর্থনীতিবিদদের একাডেমিক নেতৃত্ব আর্থার সিসিল পিগো এবং জন মেইনার্ড কেইনস গ্রহণ করেন।
অর্থনীতিতে অবদান
আলফ্রেড মার্শাল অর্থনীতিকে আরো গাণিতিকভাবে কঠোর করতে এবং এটিকে আরো বৈজ্ঞানিক পেশায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। ১৮৭০-এর দশকে তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সংরক্ষণবাদের সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৭৯ সালে, এ কাজগুলোর অনেকগুলো একত্রিত করে ‘The Theory of Foreign Trade: The Pure Theory of Domestic Values’ শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। একই বছর (১৮৭৯) তিনি তার স্ত্রী মেরি পেলি মার্শালের সঙ্গে ‘The Economics of Industry’ প্রকাশ করেন।
যদিও মার্শাল অর্থনীতিকে একটি আরো গাণিতিকভাবে কঠোর স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি চাননি যে গণিত অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাক এবং এভাবে সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠুক। সেই অনুযায়ী, মার্শাল তার বইগুলির পাঠ্য সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি করেছিলেন এবং পেশাদারদের জন্য গাণিতিক বিষয়বস্তু পাদটীকা ও পরিশিষ্টে রেখেছিলেন। এ. এল. বোলেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি বর্ণনা করেন—
১. ‘গণিতকে অনুসন্ধানের ইঞ্জিন হিসেবে নয়, সংক্ষেপিত ভাষা হিসেবে ব্যবহার করুন।’
২. ‘যতক্ষণ না আপনার কাজ শেষ হয় ততক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকুন।’
৩. ‘ইংরেজিতে অনুবাদ করুন।’
৪. ‘তারপর বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।’
৫. ‘গণিত পুড়িয়ে ফেলুন।’
৬. ‘যদি আপনি ৪ নম্বরে সফল না হন, তাহলে ৩ পুড়িয়ে ফেলুন। আমি প্রায়শই এটি করি।’
ব্রিস্টলে থাকাকালীন, তিনি এবং তার স্ত্রী ‘Economics of Industry’ বইটি সম্পন্ন করেন এবং প্রকাশের পর এটি ইংল্যান্ডে একটি অর্থনৈতিক পাঠ্যক্রম হিসাবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়; এর সহজ রূপটি অত্যাধুনিক তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল। এই কাজের মাধ্যমে মার্শাল খ্যাতি অর্জন করেন এবং ১৮৮২ সালে উইলিয়াম জেভনসের মৃত্যুর পর, মার্শাল তার সময়ের বৈজ্ঞানিক ধারার শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হন।
হেনরি ফসটের মৃত্যুর পর ১৮৮৪ সালে মার্শাল ক্যামব্রিজে রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে ফিরে আসেন। ক্যামব্র্রিজে তিনি অর্থনীতির জন্য একটি নতুন ট্রাইপস (বিশেষ ডিগ্রি) তৈরি করার চেষ্টা করেন, যা তিনি ১৯০৩ সালে অর্জন করতে পেরেছিলেন। সে সময় পর্যন্ত, অর্থনীতি ঐতিহাসিক এবং নৈতিক বিজ্ঞানের ট্রাইপসের অধীনে পড়ানো হতো, যা মার্শালকে তার কাঙ্ক্ষিত উদ্যমী ও বিশেষায়িত ছাত্র প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
পিগো এবং হাওট্রির সঙ্গে, মার্শাল মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব বা মুদ্রার আয়ের সংস্করণ তৈরি করেন। ১৯১৭ সালে, মার্শাল মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্বের ক্যামব্রিজ সংস্করণ প্রবর্তন করেন এবং এটি পিগো, হাওট্রি এবং রবার্টসন দ্বারা আরো পরিমার্জিত হয়। এটি ক্যামব্র্রিজ সমীকরণ নামে পরিচিতি লাভ করে।
প্রিন্সিপলস অফ ইকোনমিকস (১৮৯০)
মার্শাল তার অর্থনৈতিক কাজ ‘Principles of Economics’ ১৮৮১ সালে শুরু করেন এবং পরবর্তী দশকের বেশিরভাগ সময় এই গবেষণাপত্রটিতে কাজ করেন। তার কাজের পরিকল্পনা ধীরে ধীরে সমগ্র অর্থনৈতিক চিন্তার ওপর একটি দুই খণ্ডের সংকলনে প্রসারিত হয়। প্রথম খণ্ডটি ১৮৯০ সালে বিশ্বব্যাপী প্রশংসার সঙ্গে প্রকাশিত হয়, যা তাকে তার সময়ের অন্যতম প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় খণ্ডটি, যা বৈদেশিক বাণিজ্য, অর্থ, বাণিজ্য ওঠানামা, কর এবং সমষ্টিবাদ নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল, তা কখনো প্রকাশিত হয়নি।
‘Principles of Economics’ তার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করে। এটি আটটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, যা প্রথমে ৭৫০ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়ে ৮৭০ পৃষ্ঠায় বৃদ্ধি পায়। এটি ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে অর্থনীতির শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে রূপ দিয়েছে। এর প্রধান প্রযুক্তিগত অবদান ছিল স্থিতিস্থাপকতা, ভোক্তা উদ্বৃত্ত, ক্রমবর্ধমান ও হ্রাসমান আয়, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সময়, এবং প্রান্তিক উপযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর একটি নিপুণ বিশ্লেষণ। এই ধারণাগুলোর অনেকগুলোই মার্শালের নিজস্ব ছিল; অন্যগুলো ডব্লিউ. এস. জেভন্স এবং অন্যদের ধারণাগুলোর উন্নত সংস্করণ ছিল।
একটি বিস্তৃত অর্থে মার্শাল মূল্যবোধের ধ্রুপদী এবং আধুনিক তত্ত্বগুলোকে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল পণ্যের মূল্য এবং তাদের উৎপাদন খরচের মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করেছিলেন, এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে যে মূল্য নির্ভর করে উৎপাদনে ব্যয় করা প্রচেষ্টার ওপর। জেভন্স এবং প্রান্তিক উপযোগিতা তাত্ত্বিকরা উপযোগিতা সর্বাধিক করার ধারণার ওপর ভিত্তি করে মূল্যের একটি তত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই ধারণা রেখে যে মূল্য চাহিদার ওপর নির্ভর করে। মার্শালের কাজ এ দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করেছিল, তবে তিনি খরচের ওপর বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন।
সরবরাহ ও চাহিদা গ্রাফ এবং অন্যান্য তাত্ত্বিক অবদান
মার্শালের শিক্ষাদান এবং ‘Principles’ বইয়ের সাফল্যের বেশিরভাগই তার চিত্রের কার্যকর ব্যবহার থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যা শিগগিরই বিশ্বজুড়ে অন্যান্য শিক্ষকরা অনুকরণ করেন। আলফ্রেড মার্শালই প্রথম স্ট্যান্ডার্ড সরবরাহ ও চাহিদা গ্রাফ তৈরি করেন যা সরবরাহ ও চাহিদা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয় প্রদর্শন করে, যার মধ্যে রয়েছে সরবরাহ ও চাহিদা রেখা, বাজারের ভারসাম্য, সরবরাহ ও চাহিদার ক্ষেত্রে পরিমাণ ও মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক, প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্র, হ্রাসমান আয়ের সূত্র এবং ভোক্তা ও উৎপাদনকারী উদ্বৃত্তের ধারণা। এই মডেলটি এখন অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন চলক ব্যবহার করে বিভিন্ন আকারে অন্যান্য অর্থনৈতিক নীতিগুলো প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করেন।
মার্শালের মডেল জটিল অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়গুলোর একটি ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার অনুমতি দিয়েছে যেখানে আগে সমস্ত ধারণা এবং তত্ত্বগুলো কেবল শব্দ ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা যেত। এই মডেলগুলো এখন অর্থনীতির অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা মৌলিক বিষয় বা তত্ত্বগুলোর একটি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার অনুমতি দেয়।
তাত্ত্বিক অবদান
মার্শালকে তার সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে মূলধারার অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনাকে ব্যাপকভাবে রূপ দিয়েছে এবং নিওক্লাসিক্যাল অর্থনীতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যদিও তার অর্থনীতিকে অ্যাডাম স্মিথ, থমাস রবার্ট ম্যালথাস এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের কাজের সম্প্রসারণ ও পরিমার্জন হিসাবে বিজ্ঞাপন করা হয়েছিল, তিনি অর্থনীতিকে এর ধ্রুপদী বাজার অর্থনীতির ফোকাস থেকে সরিয়ে মানব আচরণের অধ্যয়ন হিসেবে জনপ্রিয় করেন। তিনি লিওন ওয়ালরাস, ভিলফ্রেডো পারেটো এবং জুলস ডুপুইটের মতো অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের তার কাজের প্রতি অবদানকে কম গুরুত্ব দেন এবং স্ট্যানলি জেভন্সের প্রভাবকেও অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বীকার করেন।
মার্শাল ছিলেন এমন একজন যিনি উপযোগিতা বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছিলেন, তবে মূল্য তত্ত্ব হিসেবে নয়। তিনি এটিকে চাহিদা রেখা এবং প্রতিস্থাপন নীতি ব্যাখ্যা করার জন্য তত্ত্বের একটি অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।
মার্শালের কাঁচি বিশ্লেষণ—যা চাহিদা এবং সরবরাহ, অর্থাৎ, উপযোগিতা এবং উৎপাদনের খরচকে একজোড়া কেঁচির দুটি ফলকের মতো একত্রিত করেছিল—কার্যকরভাবে মূল্য তত্ত্বকে বিশ্লেষণের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেয় এবং এটিকে মূল্য তত্ত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপন করে। যদিও ‘মূল্য’ শব্দটি ব্যবহার হতে থাকে, বেশিরভাগ মানুষের জন্য এটি ‘মূল্য’-এর প্রতিশব্দ ছিল। মূল্যগুলো আর দামের কিছু চূড়ান্ত এবং পরম ভিত্তির দিকে ঝুঁকে থাকে বলে মনে করা হয়নি; মূল্যগুলো অস্তিত্বশীল ছিল, চাহিদা এবং সরবরাহের সম্পর্কের মধ্যে।
অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনাকে সংহতি বদ্ধ করার ক্ষেত্রে মার্শালের প্রভাব অস্বীকার করা কঠিন। তিনি সরবরাহ ও চাহিদা ফাংশনগুলো মূল্যের নির্ধারণের সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহারকে জনপ্রিয় করেন (আগে কুরনট স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন); আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মূল্য পরিবর্তন এবং বক্ররেখা পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্রের জন্য মার্শালের কাছে ঋণী।
মার্শাল ‘প্রান্তিকতাবাদী বিপ্লবের’ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন; এই ধারণা যে ভোক্তারা প্রান্তিক উপযোগিতা মূল্যের সমান না হওয়া পর্যন্ত ভোগ সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করে, এটি তার আরেকটি অবদান ছিল। চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা মার্শাল এই ধারণাগুলোর একটি সম্প্রসারণ হিসেবে উপস্থাপন করেন।
অর্থনৈতিক কল্যাণ, যা উৎপাদনকারী উদ্বৃত্ত এবং ভোক্তা উদ্বৃত্তে বিভক্ত, মার্শালের অবদান ছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে, এই দুটিকে কখনো কখনো ‘মার্শালিয়ান উদ্বৃত্ত’ হিসাবে বর্ণনামূলকভাবে বর্ণনা করা হয়। তিনি উদ্বৃত্তের এই ধারণাটি কর এবং মূল্য পরিবর্তনের বাজারের কল্যাণের ওপর প্রভাব কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যবহার করেন। মার্শাল কোয়াসি-রেটও চিহ্নিত করেন।
ইংল্যান্ডের ‘শিল্প জেলাগুলির’ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্পর্কে মার্শালের সংক্ষিপ্ত উল্লেখগুলি বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থনৈতিক ভূগোল এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে ক্লাস্টারিং এবং লার্নিং সংস্থাগুলোর ওপর কাজের একটি সূচনা বিন্দু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
১৯৯২ সালে অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গ্যারি বেকার (১৯৩০-২০১৪) উল্লেখ করেছেন যে মিল্টন ফ্রিডম্যান এবং আলফ্রেড মার্শাল তার কাজের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন।
মার্শালের আরেকটি অবদান ছিল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অর্থনীতির ধারণার পার্থক্যকরণ। অর্থাৎ, যখন উৎপাদনের উপাদানগুলোর খরচ কমে যায়, তখন এটি বাজারের সমস্ত ফার্মের জন্য একটি ইতিবাচক বাহ্যিকতা হয়, যা কোনো ফার্মের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
শেষ জীবন ও কর্মজীবন
মার্শাল ১৮৮৯ সালের প্রথম দিনের সমবায় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরের দুই দশকে তিনি তার ‘প্রিন্সিপলস’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি শেষ করার জন্য কাজ করেন। তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে তার অটল মনোযোগ এবং সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা তাকে কাজটির বিশালতা আয়ত্ত করতে বাধা দেয়। কাজটি কখনোই শেষ হয়নি এবং তিনি আরো অনেক ছোট কাজ শুরু করেছিলেন—যেমন ১৮৯০-এর দশকে চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকারের জন্য বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি—একই কারণে সেগুলিও অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।
১৮৮০-এর দশক থেকে তার স্বাস্থ্যের সমস্যা ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে এবং ১৯০৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। তিনি তার ‘প্রিন্সিপলস’ নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আশা করেছিলেন, কিন্তু তার স্বাস্থ্যের অবনতি অব্যাহত থাকে এবং প্রতিটি নতুন অনুসন্ধানের সঙ্গে প্রকল্পটি আরো বড় হতে থাকে।
১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত তাকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংশোধন করতে উৎসাহিত করে এবং ১৯১৯ সালে ৭৭ বছর বয়সে তিনি ‘Industry and Trade’ প্রকাশ করেন। এই কাজটি মূলত তাত্ত্বিক ‘প্রিন্সিপলস’-এর চেয়ে একটি বেশি অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণাপত্র ছিল এবং এই কারণে এটি তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে ততটা প্রশংসা অর্জন করতে পারেনি। ১৯২৩ সালে, তিনি ‘Money, Credit, and Commerce’ প্রকাশ করেন, যা ছিল পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক ধারণাগুলোর একটি বিস্তৃত মিশ্রণ, যার মধ্যে অর্ধ শতাব্দী আগের প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত উভয় ধারণাই অন্তর্ভুক্ত ছিল।
শেষ বছর, মৃত্যু এবং উত্তরাধিকার
১৮৯০ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত মার্শাল অর্থনীতি পেশার শ্রদ্ধেয় জনক ছিলেন এবং তার মৃত্যুর পরের অর্ধশতাব্দী ধরে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের কাছে তিনি পূজনীয় পিতামহ হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি তার জীবদ্দশায় বিতর্ক থেকে দূরে থাকতেন, যা এই পেশার পূর্ববর্তী নেতারা করতেন না। তবে তার পক্ষপাতহীন মনোভাব সহকর্মী অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা এবং এমনকি ভক্তিও অর্জন করেছিল।
ক্যামব্র্রিজে তার বাসভবন, বলিওল ক্রফট, বিশিষ্ট অতিথিদের আনাগোনায় মুখরিত থাকত। ক্যামব্র্রিজে তার ছাত্ররা অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন, যার মধ্যে জন মেইনার্ড কেইনস এবং আর্থার সেসিল পিগো অন্যতম। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার ছিল অর্থনীতিবিদদের জন্য একটি শ্রদ্ধেয়, একাডেমিক, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পেশা তৈরি করা, যা বিংশ শতাব্দীর বাকি অংশের জন্য এই ক্ষেত্রের সুর বেঁধে দিয়েছিল।
মার্শাল ৮১ বছর বয়সে ক্যামব্র্রিজে তার নিজ বাড়িতে মারা যান এবং তাকে অ্যাসেনশন প্যারিশ বুরিয়াল গ্রাউন্ডে সমাহিত করা হয়। কেইনস তার সাবেক শিক্ষকের জন্য একটি শোকগাথা লেখেন, যাকে জোসেফ শুম্পেটার ‘একজন বিজ্ঞানীর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল বর্ণনা যা আমি কখনো পড়েছি’ বলে অভিহিত করেছেন।
ক্যামব্র্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের লাইব্রেরি (দ্য মার্শাল লাইব্রেরি অফ ইকোনমিকস), ক্যামব্র্রিজের অর্থনীতিবিষয়ক সমিতি (দ্য মার্শাল সোসাইটি), এবং ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টলের অর্থনীতি বিভাগ তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। তার আর্কাইভ মার্শাল লাইব্রেরি অব ইকোনমিকসে অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে পরামর্শের জন্য উপলব্ধ। তার বাড়ি, বলিওল ক্রফট, ১৯৯১ সালে লুসি ক্যাভেন্ডিশ কলেজ, ক্যামব্র্রিজ কর্তৃক কেনা হলে তার সম্মানে মার্শাল হাউস নামকরণ করা হয়।
আলফ্রেড মার্শালের স্ত্রী ছিলেন মেরি পেলি, একজন অর্থনীতিবিদ যিনি ক্যামব্র্রিজের প্রথম মহিলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন এবং নিউনহাম কলেজের প্রভাষক ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত বলিওল ক্রফটে বসবাস চালিয়ে যান; তার চিতাভস্ম বাগানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই দম্পতির কোনো সন্তান ছিল না।
প্রধান কাজসমূহ
এখানে আলফ্রেড মার্শালের প্রধান কাজগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো :
১৮৭৯ দি ইকোনমিকস অফ ইন্ডাস্ট্রি (মেরি পেলি মার্শালের সঙ্গে)
১৮৭৯ দি পিওর থিওরি অফ ফরেন ট্রেড : দি পিওর থিওরি অফ ডোমেস্টিক ভ্যালুস
১৮৯০ প্রিন্সিপলস অফ ইকোনমিকস
১৯১৯ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ট্রেড
১৯২৩ মানি, ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স
মার্শালের এই কাজগুলো অর্থনীতিতে তার গভীর অবদান এবং প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।
কেকে/এএম