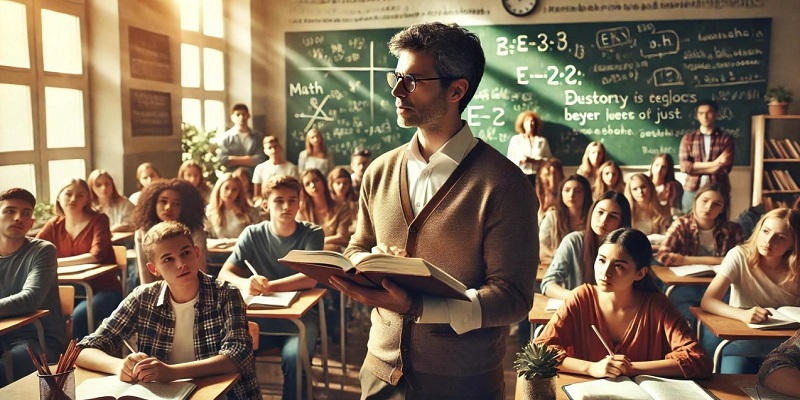বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক নির্মাণকেন্দ্র। এখানেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, গবেষক, নীতিনির্ধারক, এমনকি রাজনীতিকও। কিন্তু এই জায়গাতেই যখন সম্বোধনের ভাষায় বিভাজন তৈরি হয়—‘তুমি’, ‘তুই’ আর ‘আপনি’র ব্যবহারে, তখন বিষয়টি কেবল ভাষাগত নয়, তা হয়ে ওঠে একপ্রকার সাংস্কৃতিক শ্রেণিচিহ্ন ও ক্ষমতার প্রদর্শন।
আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের একাংশ শিক্ষার্থীদের ‘তুমি’ কিংবা ‘তুই’ বলে সম্বোধন করেন। প্রশ্ন—একজন উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থী, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নিজের মত গঠন করছেন, চিন্তা করছেন, বিতর্ক করছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাকে কেন ‘আপনি’ বলে সম্মান করা হবে না?
‘আপনি’ হলো একটি নিরপেক্ষ, সম্মানসূচক ও পেশাদার সম্বোধন। শিক্ষার্থীদের ‘আপনি’ বলায় মর্যাদাহানির কিছু নেই। শিক্ষার্থীদের প্রতি ভাষাগত সৌজন্য দেখানো উচিত। কেউ বয়সে ছোট বলেই তাকে ‘তুমি’ বলা যায়—এই যুক্তি যদি ধরি, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়স্ক শিক্ষার্থীও থাকেন, যারা হয়তো শিক্ষকের থেকেও অভিজ্ঞতায় বড়। তাদেরকেও কি আমরা তখন ‘তুমি’ বলব?
এই সমস্যা শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রেজিস্ট্রার, দপ্তর থেকে শুরু করে নিরাপত্তারক্ষীরাও প্রায়শই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন ‘তুমি’ সম্বোধন করে। এই ‘তুমি’ সংস্কৃতি আমাদের সমাজে প্রোথিত এক ধরনের বয়সবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। এটি আসলে একপ্রকার বৈষম্য।
শিক্ষার্থীরা যদি শ্রদ্ধা পায়, তারা তখন সম্মান ফেরত দিতেও শেখে। আজকের দিনে কোনো কোনো শিক্ষক যখন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ‘আপনি’ বলে ডাকেন, তখন শিক্ষার্থীদের চোখে-মুখে এক ধরনের বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে।
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে এই ‘আপনি’ সম্বোধন একমুখী। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ‘তুমি’ বা ‘তুই’ বলছেন অবলীলায়। বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি জায়গা যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকা উচিত। এই জায়গাতেই যদি সম্পর্ক হয় একমুখী এবং ভাষার মধ্যে অসম শ্রেণিবিন্যাস, তাহলে শিক্ষা কীভাবে মুক্তচিন্তার দিকে এগোবে?
শিক্ষকেরা দাবি করেন যে তারা শিক্ষার্থীদের সন্তানতুল্য মনে করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আপাতদৃষ্টিতে মানবিক মনে হলেও বাস্তবে সেটি একটি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই পড়ে যায়, যেখানে বড়রা ‘ভুল ধরতে পারেন’, ‘ধমক দিতে পারেন’, আবার ‘তুমি’ বলেও ‘ভালোবাসা’ দেখাতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার্থী যখন তার মত প্রকাশ করে, দ্বিমত বা সমালোচনা করে, তখনই সে ‘শিষ্টাচারহীন’ হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হবে সম্মাননির্ভর। সেখানে শিক্ষকের কাজ শুধু ‘শেখানো’ নয়, শেখারও।
‘আপনি’ বললে সম্মান কমে না। শিক্ষক যদি একজন শিক্ষার্থীকে ‘আপনি’ বলেন, তাতে কোনো ক্ষমতা হারায় না বরং এক ধরনের ভাষাগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ন্যায়বিচার থেকে তৈরি হয় আস্থার সম্পর্ক, যেখানে শিক্ষার্থী শুধু পরীক্ষায় পাসের জন্য নয়, বরং একজন সুন্দর মানুষ হওয়ার জন্যেও পড়াশোনা করে।
নৃতাত্ত্বিক গবেষক পিয়েরে বোর্দিউ তার ‘সিম্বলিক পাওয়ার’ তত্ত্বে দেখিয়েছেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি ক্ষমতার এক গোপন অস্ত্র। যে ভাষায় কেউ কাউকে সম্বোধন করে, সেটি তার সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণিকে চিহ্নিত করে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ‘তুমি’ ব্যবহার আসলে এক ধরনের প্রতীকী আধিপত্য। এটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে নির্ভর করে শ্রেণি ও ক্ষমতার ওপর, যেখানে শিক্ষার্থীর জায়গা নিচের সারিতে।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক অনেক বেশি সমমর্যাদাপূর্ণ এবং সম্বোধনের ভাষাও তেমনই।
উদাহরণস্বরূপ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে সরাসরি নাম ধরে ডাকা হয় ‘প্রফেসর লি’, ‘ড. জনসন’, আর শিক্ষকও শিক্ষার্থীদের সম্বোধন করেন ‘ইউ’ বলে, যা নিরপেক্ষ।
জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ‘সাই’ সম্বোধন ব্যবহৃত হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে। যা বাংলায় ‘আপনি’র সমতুল্য। জার্মানিতে ‘ডিউ’ মানে ‘তুমি’, সেটি কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ‘সান’ যোগ করে সম্বোধন করেন, যা সম্মানসূচক।
ইতিহাসবিদ ইউভাল নোয়া হারারি তার ‘একুশ শতকের ২১ শিক্ষা’ বইতে বলেন, শ্রেণিকক্ষের সম্মাননির্ভর হওয়া উচিত।
বাংলাদেশে অনেক শিক্ষক আছেন যারা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের ‘আপনি’ বলেন, এবং নামের আগে ‘জনাব’ বা ‘মিস’ ব্যবহার করেন। তবে সংখ্যায় তারা খুবই কম।
মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালায়া কিংবা ভারতের টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেসের (টিআইএসএস) শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সম্বোধনে সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করেন। শিক্ষার্থীরা সেখানে সমকক্ষ অ্যাকাডেমিক সহযোগী হিসেবে বিবেচিত।
আমেরিকান ভাষাবিদ নোয়াম চম্স্কি বলেন, আমাদের চিন্তার প্রতিফলন ঘটে ভাষায়, আর একইসঙ্গে ভাষাও আমাদের চিন্তার কাঠামো গড়ে তোলে।
এই পরিবর্তনের উদাহরণ আমরা দেখতে পাই কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করেন। এটি গড়ে তোলে এক নতুন অ্যাকাডেমিক সমতা।
‘তুমি’ নয়, ‘আপনি’ বলার এই সংস্কৃতি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই কেন থাকবে? আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও এই ভাষাগত সম্মানবোধের অভাব প্রকট। স্কুলে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ‘তুই’ বলে বকেন, আর ভুল করলেই বলে বসেন ‘তোর মতো শিক্ষার্থীদের দিয়ে কিছু হবে না!’
মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুর আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে তার প্রাথমিক শিক্ষা পরিবেশ থেকেই। একজন শিশু যদি প্রথম থেকেই ‘আপনি’ সম্বোধন শোনে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা দেখে, তাহলে সে নিজেও সম্মান করতে শিখবে।
মারিয়া মন্টেসরি শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তি হলো—শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিশুরা তাদের নিজস্ব গতিতে শিখতে পছন্দ করে এবং তাদের শেখার প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত পরিবেশ তৈরি করা হয়, যেখানে তারা নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী উপকরণ বাছাই করে, এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে শেখে।
কলেজ পর্যায়ে এসে শিক্ষার্থীরা প্রায়শই এক ধরনের সংকটে পড়ে। তারা শিশু নয়, প্রাপ্তবয়স্কও নয়। ফলে তাদের প্রতি আচরণে অনেক সময় স্পষ্টতা থাকে না।
অনেক শিক্ষক মনে করেন, শিক্ষার্থীদের ‘আপনি’ সম্বোধন করলে শ্রদ্ধা হারিয়ে যাবে। কিন্তু সত্যি হলো সম্মান দিলে সম্মান ফিরে আসে। শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীর সঙ্গে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলেন, তখন তার কথার মূল্য বেড়ে যায়। ‘আপনি’ বলার সাহস যে শিক্ষক দেখাতে পারেন, তিনিই হয়ে ওঠেন শিক্ষার প্রকৃত রোল মডেল।
একজন শিক্ষার্থীরও সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে। শুধু ভালো রেজাল্ট করলে নয়, কেবল আজ্ঞাবহ হলে নয়, বরং শুধু এই কারণেই যে, তিনি একজন মানুষ।
আমরা কি পারি না এমন একটি শিক্ষা-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে, যেখানে শ্রদ্ধা হবে পারস্পরিক? যেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন। সেই চোখে করুণা নয়, থাকবে সম্মান আর ভালোবাসা। ভাষা বদলালে মনোভাব বদলায়, আর মনোভাব বদলালেই গড়ে ওঠে এক নতুন সুন্দর সমাজ। আর তার সূচনা হোক ‘আপনি’ দিয়ে, ‘তুই’ বা ‘তুমি’ নয়।
লেখক : কলামিস্ট ও সাংবাদিক