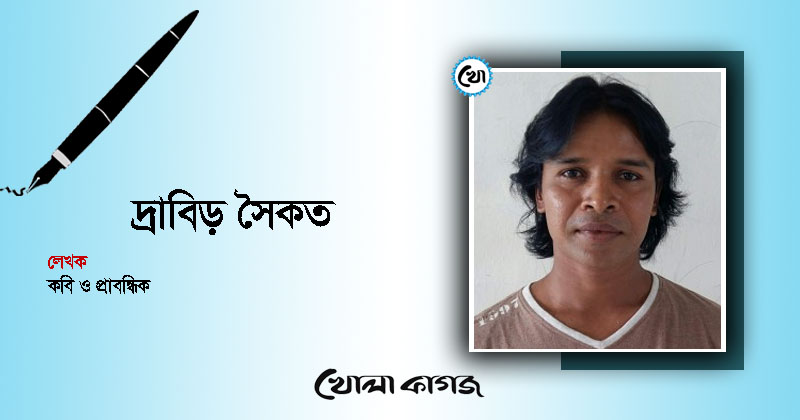প্রাকৃত সত্তার নিয়মানুযায়ী যার সংস্কার বা শোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে তাই সংস্কৃতি। প্রাকৃতিক কাঠামোর মৌল রীতিনীতিকে অনুসরণ করার মাধ্যমে প্রকৃতিকে সংস্কারের ভেতর দিয়ে সংস্কৃতি নির্মিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকও নয় আবার পুরোপুরি কৃত্রিমও নয় বরং মানুষের সহজাত প্রবণতা এবং সমাজের আরোপিত রীতিনীতির মাঝামাঝি একটি সেতুবন্ধ। সার্বিক অর্থে সংস্কৃতি একটি কৃত্রিম বিষয় তবে সে প্রকৃতির মূলনীতিকে অনুসরণ করছে। প্রাণের বা আত্মার মৌলিক প্রবণতা অনুযায়ী তার বিন্যাস। আত্মা হলো চৈতন্যময় সত্তা, নিজস্বতা, স্বভাব, জীবনশক্তি বা অভ্যন্তরীণ সত্তা। সাংখ্য ও যোগ দর্শনে পুরুষ বা চেতনা, তন্ত্রে আত্মা হলো অভিজ্ঞতালব্ধ শক্তি-চেতনার এক অভ্যন্তরীণ কেন্দ্র।
মনোবিজ্ঞানে আত্মা নয়, বরং ‘স্ব’ (self) বা ‘সচেতনতা’ (consciousness) কেন্দ্রীয় বিষয়, সাংখ্যদর্শনে যাকে বলা ‘জ্ঞ’; অবগত হবার আধার। আত্মার বিশেষত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘যিনি নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ অহংসীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ : ৩০৭)। অহং অতিক্রান্ত সত্তার সঙ্গে প্রকৃতির সামঞ্জস্যপূর্ণ চলনবিন্যাস হলো সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতির বিস্তার বহুবৈচিত্র্যের ভেতর। সংস্কৃতিকে (culture) অনেকেই কিছু মূল্যবোধের (Values, Norms) সমষ্টি মনে করেন, এর একটি (performative) আনুষ্ঠানিক দিক থাকে তাকে যাদের আমরা শিল্পকলা নামে চিনি, আরকিছু থাকে (Habitual) বা স্বভাবগত দিক, যা আমাদের নৈমত্তিক জীবনের আচার-আচরণ হিসেবে প্রকাশিত হয় কিন্তু সংস্কৃতিকে কেবল মূল্যবোধের সমষ্টি ভাবার কারণে পদ্ধতিগত কিছু ভুল তৈরি হয়, কারণ মূল্যবোধ কেবল চিন্তাগত বিষয়ের সাথে জড়িত, কেবল মানসিক বিষয় মূল্যবোধের বিষয়, ফলে এখানে দৈহিক বিষয়াদি বাদ পড়ে যায় কিংবা গৌণ হয়ে পড়ে। দুটি দিকের মূল পাটাতন স্বতন্ত্র হতে পারে, সেখানেই স্ববিরোধের খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেখান থেকে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি উৎসারিত হয়, সেই পাটাতন বসে থাকে জনগোষ্ঠীর প্রাকৃত সত্তায়।
ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র বিষয়। প্রশ্ন হলো সংস্কৃতির এ নির্মাণ কি কোনো স্বয়ম্ভু অভিব্যক্তি? সাধারণভাবে বলা হয় ব্যক্তি বা সমাজের বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতি হলো নির্দিষ্ট আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, ভাষা, শিল্প, ঐতিহ্য, সমাজকাঠামো, আইন-কানুন, অভ্যাস, কিছু প্রতীক, সংকেত এবং বিশ্বাসের সমন্বিত রূপ, যা একটি সমাজের মানুষ নিজেদের মাঝে ধারণ করে। যেসব বিষয়াদি তাদের একত্রিত রাখে এবং বাকি পৃথিবী ও জীবনযাপনের বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তকে একটি আকৃতি দেয়। সংস্কৃতির প্রচলিত অর্থকে নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্ককে আমরা পাশে সরিয়ে রাখতে চাই, কেননা সেটি এই মূল রচনার লক্ষ্য নয়। তবে বলে রাখা ভালো :
বঙ্গীয় শব্দকোষে সংস্কৃতি শব্দটি বলতে গেলে নেই। তার বদলে রয়েছে রস কথাটি এবং তিন পৃষ্ঠা ভরে তার মানে দেওয়া আছে। সেই রস কথাটিকে বাদ দিয়ে ঔপনিবেশিককালে, তৎকালীন কলকাতার বাঙালি পণ্ডিতগণ ইংরেজের culture শব্দটির প্রতিশব্দরূপে বাংলার ‘সংস্কৃতি’ শব্দটিকে নিয়মিত ব্যবহার করতে শুরু করেন। কেন করেন, সংস্কৃতি শব্দটির ভিতরে ঢুকলে, সেকথা আমরা জানতে পারি। [...] আদিতে ছিল ‘চর’ শব্দটি। যার দ্বারা বিচরণ সম্ভব তাকে বলা হত চরণ। চরণে চরণে যা বিধৃত থাকে, তাকে আচরণ বলে। সেই আচরণের পুনরাবৃত্তিকে বলে আচার এবং গোষ্ঠী ও কুলের আচারসমূহকে বলা হত ‘কুলাচার’। ভারতে প্রচলিত ‘কুলাচার’ ছিল কৃষি। ঐ ‘কুলাচার’ ও ‘অগ্রিকুলাচার’ বংশের NRI উত্তরসূরির নামই যথাক্রমে culture ও agriculture. সেই culture যখন ব্রিটিশের জিভে চেপে তার পিতৃভূ মিতে ফিরে এল, তখন তার গায়ে ছিল ক্যাপিটালিস্ট যজ্ঞস্বভাবের বর্ণ ও গন্ধ। (কলিম খান শ্রাবণ ১৪০৬ : ২০০)।
কুলাচার, কালচার, কৃষ্টি, সংস্কৃতি কিংবা রসের বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে তাবে এ রচনায় এসবের অর্থ মোটাদাগে সংস্কৃতি।
একটি জনগোষ্ঠীর ঐক্যতানের পেছনে যে সংস্কৃতির বর্ণিল সূত্র থাকে সেখান থেকেই মানুষ তাদের জীবনযাপনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু এমন সিদ্ধান্তের উৎপত্তি কোথায়? কীভাবে মানুষ সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংস্কৃতি নিজে নিজেই রূপায়িত হয় না, এটি ব্যক্তিগত কর্ম থেকেও উৎসারিত নয়। এর পেছনে সক্রিয় থাকে বিবিধ কাঠামো, সামষ্টিক চৈতন্যে যা একটি সমাজ ধারণ করে। বিশ্বব্যাপী তাত্ত্বিকদের মাঝে সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক চৈতন্য বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, তবে এর প্রত্যেকটি বিষয়ই যে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এ পরিবর্তন, সংযোজন বা সংস্কার তার ভূ -প্রকৃতি, জলবায়ু, দর্শন-ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদির অনুগামী এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়, অন্যথায় সেটি বিপর্যকর হিসেবে সংস্কৃতিতে আবির্ভূত হতে পারে। বঙ্গীয় অঞ্চলের তন্ত্র, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত দর্শনের অভ্যন্তরে প্রকৃতি বা প্রাকৃতসত্তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে যা আমাদের আলোচনায় ধীরে ধীরে স্পষ্টতা লাভ করবে। সাংখ্যদর্শনে জগতের কারণ প্রকৃতি।
প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম বলে প্রত্যক্ষযোগ্য নয় ‘সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্যতস্তদুপলব্ধেঃ’ কিন্তু কার্যের দ্বারা প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বারবারা ক্রুগারের (ইধৎনধৎধ কৎঁমবৎ, ১৯৪৫) একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম আছে (‘I shop therefore I am’, Barbara Kruger : 1990) ‘আই শপ দেয়ার ফর আই অ্যাম’, আমার ক্রয় ক্ষমতাই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ, যা মূলত দেকার্তের (René Descartes, 1596-1650) ‘আমি ভাবছি তাই আমি আছি’ এর শৈল্পিক প্রতিধ্বনি। প্রকৃতির প্রতি পাশ্চাত্যের এমন দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে গ্রিক-রোমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে এবং ইহুদি-খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসে। এই মতাদর্শের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত।
পাশ্চাত্যের জীবনযাপন এবং তাদের সমাজ কাঠামো তাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সূতিকাগার প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিকগণও প্রকৃতি বিষয়ে তাদের মালিকানাসুলভ মতামতকে তুলে ধরেছেন। প্লেটো তাঁর ‘লজ’ (The Laws of Plato) গ্রন্থে পরিবেশ-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বলেন, ‘[...] Suppose someone else, who had seen goats grazing without a goatherd and doing damage to cultivated fields, were to denounce the animal and blame, (Book 1, 639a)’ (Plato, 1980, p. 18)। প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় প্লেটোর মতাদর্শে।
প্রকৃতির ওপর মানুষের সর্বময় ক্ষমতার ধারণা তাকে প্রকৃতির প্রতি অবিচারে উৎসাহ প্রদান করে। প্রকৃতির সব রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তার ওপর সব ধরনের অত্যাচার, নিপীড়ন ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে হলেও আধিপত্য নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতির ওপর এভাবে আধিপত্য বিস্তারের বিভিন্ন পন্থায় প্রকৃতির কি দশা হলো সে বিষয়ে ভাবার দায় পাশ্চাত্য আধুনিকতার নেই। তবে আধুনিকতার প্রাণ-প্রকৃতি বা পুরুষ-প্রকৃতির ধারণাগুলোকে উত্তরাধুনিকতা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না। কেননা আধুনিকতার একপেশে মানবকেন্দ্রিকতা প্রকৃতির প্রতি যথেচ্ছাচার করবার একটি অধিকারবোধ তৈরি করে মানুষের মনে, যেটি প্রাচ্যের প্রাচীন উৎস থেকে অনুপ্রাণিত অথবা সাদৃশ্যপূর্ণ উত্তরাধুনিক মতাদর্শ এক ধরনের নিপীড়ন হিসেবে চিহ্নিত করে। বঙ্গীয় দর্শনেরও অবস্থান একই, অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের মতোই একটি সতন্ত্র সত্তা, তাকে অবলোকন বা অনুধাবনের পন্থা এখানে সংবেদশীল। উত্তরাধুনিকতা ও বঙ্গীয় অঞ্চলের প্রাচীন দর্শন ও তান্ত্রিক মতাদর্শ এখানে সাদৃশ্যপূর্ণ, প্রত্যেকেই প্রকৃতির ওপর এমন নিপীড়নকে অবৈধ মনে করে।
সংস্কৃতি তাই সংবেদনশীল বিষয়, এর একটি ক্ষুদ্র বিপর্যয় কোনো বড় ধরনের প্রলয়ের কারণ হতে পারে। সংস্কৃতি শব্দের অর্থের ভেতর থেকেই আমরা বিপর্যয়কর/মন্দ/নিকৃষ্ট বা অপসংস্কৃতি অথবা আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। প্রাকৃতসত্তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ই বিপর্যয়কর সংস্কৃতি, অনেক সময়ই আমরা যাকে অপসংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করতে চাই। অপ অর্থও মন্দ বা নিম্নমানের বিষয়, যা নির্দিষ্ট সমাজদেহে বা মানবদেহের সঙ্গে বিধিবদ্ধ নয়। মানবদেহকেও কেবলই দেহ হিসেবে দেখলে ভুল হবে, যেহেতু দেহ এবং মনের ধরনে ভিন্নতা রয়েছে। কাজেই প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের দেহ-মনের সঙ্গে যেটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাই বিপর্যকর, মন্দ বা অপসংস্কৃতি। তবে অপসংস্কৃতি শব্দটির যততত্র অপব্যবহারের আশংকা থাকে বিধায় শব্দটি বরং পরিহার করাই ভালো, যদিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা অবশ্যই ব্যবহার করবেন।
প্রকৃতি থেকে নিজেদের আলাদা করে তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ধারণাটি মূলত অজ্ঞতাপ্রসূত, কেননা মানুষ এই মহাপ্রকৃতির কাছে নিতান্তই ক্ষুদ্রতম এক সৃষ্টি। প্রকৃতি তার নির্দিষ্ট নিয়মে মানুষকে যেমন আবদ্ধ করেছে তেমনি নির্ধারিত একটি সীমার ভেতরে তার রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বাধীনতাকে যথার্থভাবে বুঝতে ব্যর্থ হলে আমরা তার ওপর বিবিধ বিষয় আরোপের প্রয়াস চালাই, তখনই সেটি প্রকৃতি সংস্কার করে সংস্কৃতি না হয়ে তা হয়ে ওঠে অপসংস্কৃতি। দেখা যাবে পৃথিবীর প্রায় সব বিদ্বান মানুষই প্রকৃতির নিয়মকে মান্যতা দেবার পক্ষেই তাদের রায় দিচ্ছেন। তবে পশ্চিমা সভ্যতার সমস্যা হলো অধিকাংশ সময়ই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের জীবনযাপন করতে হয়েছে, ফলে তাদের প্রধান প্রবণতা হলো প্রকৃতিকে প্রতিপক্ষ মনে করা। যা প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমের চিন্তা ও জীবনবোধের জায়গায় একটি মৌলিক পার্থক্য।
লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক
কেকে/এআর