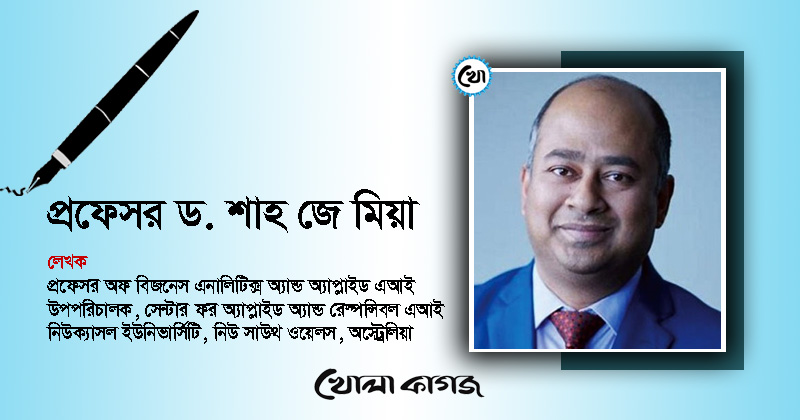আজকের আলোচনায় আমরা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই। ইদানীং এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক অপ্রীতিকর ছবি এবং ভিডিও ইন্টারনেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা কিনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সম্মানহানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এর আগেও আমার অনেক জাতীয় দৈনিকে লেখায় উল্লেখ করেছিলাম যে, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে একটি এমন ডিজিটাল মিডিয়া ফাইল (যেমন একটি ছবি, ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং) তৈরি করা সম্ভব, যা দেখতে আসল বলে মনে হলেও, বস্তুতই এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি এবং যার বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই।
এর আগেও আমি আলোচনা করেছিলাম যে, এসব এআই অ্যাপ্লিকেশনের এই নতুন ধারণাটি বিশ্বব্যাপী বেশিরভাগ সমাজেই অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এ ধরনের মিথ্যা কন্টেন্টগুলো তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা কিনা এক ধরনের গোষ্ঠীর বা মানুষের কাজ। যা হোক এই ধরনের মিথ্যা কনটেন্ট তৈরি করতে সক্ষম এআই সফটওয়্যারগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং ভাবে কাজ করে থাকে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে একজন ব্যবহারকারী যদি দুজন ভিন্ন ব্যক্তির ছবি সফটওয়্যারটিকে দিয়ে কমান্ডে বলে যে, আমাকে একটি ছবি তৈরি করে দাও যেখানে দেখা যাবে এই দুজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে হাত মেলাচ্ছে, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সফটওয়্যারটি এত নিখুঁত একটি ছবি তৈরি করবে যেটা থেকে বোঝার কোনো উপায়ই থাকবে না যে, এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি ঘটনা এবং এটি কখনোই সংঘটিত হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ডিপফেক প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে এবং সফটওয়্যারগুলোও অনেক শক্তিশালী হয়েছে। এখন সফটওয়্যারগুলো কৃত্তিম ছবি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে এমন ভিডিও তৈরি করতে পারে, যেখানে দেখা যাবে আমাদের এই উদাহরণের দুজন মানুষ একসঙ্গে বসে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে আলোচনা করছে, চা পান করছে বা একসঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে যদি সফটওয়্যারগুলোকে এই দুজন ব্যক্তির কোনো কথা বা বক্তব্য প্রদান করা যায়, তাহলে এগুলো তাদের কণ্ঠস্বর নকল করে যেকোনো বক্তব্য ভিডিওর সঙ্গে জুড়ে দিতে পারবে। ভিডিওতে তাদের প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সঠিকভাবে মুখের পেশি নড়বে এবং আবেগের পরিবর্তন প্রদর্শিত হতে পারে। এই মিথ্যা ভিডিও যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে খালি চোখে দেখে কেউই এই ছবি বা ভিডিওর কৃত্তিমতা যাচাই করতে পারবে না।
আমাদের দেশে মাত্র তিন মাসের মধ্যেই আমাদের মাঝে সংগঠিত হতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন ২০২৬। এই মুহূর্তে এই নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যক্তির জন্য তাদের সম্মান এবং ইমেজ ধরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এই মুহূর্তেই একটি শক্তি তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা এবং ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ইমেজ, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করার। তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অপ্রীতিকর মিডিয়া বা কনটেন্ট তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া। এই ক্রান্তিকালীন সময়ে তাই এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, এর কার্যপ্রণালি সম্পর্কে জানা এবং এর বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচারণা করা প্রতিটি সরকারি, বেসরকারি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অতীব জরুরি।
সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যেসব ছবি বা ভিডিও পোস্ট করে থাকি সেখান থেকে আমাদের চেহারা, আমাদের কণ্ঠস্বর, আমাদের গতিবিধি, এবং আমাদের কনটেন্টকে এসব এআই মডেলগুলোর জন্য প্রশিক্ষণ ডেটা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ডেটা থেকে শিক্ষা গ্রহণই পরবর্তীতে অনেক নতুন নতুন মিডিয়ার আবির্ভাব ঘটায়, যেখানে ভিডিওর মানুষটি দেখতে আমাদের কারো মতো, এমনকি কণ্ঠস্বর শুনতেও আমাদের মতো কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণ কৃত্তিম মিডিয়া, যেগুলোর সঙ্গে আসল ব্যক্তির কোনো সম্পর্কই নেই। এই কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলো মানুষের মুখের নড়াচড়া, অভিব্যক্তি এবং ভয়েস প্যাটার্ন বা সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে যার ফলে নির্দিষ্ট মানুষের আচার আচরণ, চলাফেরা, কথা বলার ধরন হুবহু নকল করতে সক্ষম হয়। ভয়েস সংশ্লেষণ বা কণ্ঠস্বরের ধরন বলতে একজন ব্যক্তির কথা বলার অনন্য ধরনকে বোঝায়। প্রতিটি ব্যক্তির কথা বলার ছন্দ, স্বর, গতি এবং বিরতির মতো বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যের থেকে আলাদা। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এই আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করা যায় এবং সেগুলো অনুকরণ করে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে কোনো বক্তব্য তৈরি করাও সম্ভব হয়।
দ্বিতীয় কার্যকলাপটি মানুষের চেহারার পরিবর্তন বা ফেস সোয়াপিং বা মুখ-অবয়ব বিকৃতিকরণ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এ কার্যকলাপটিও কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা মডেলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। এই প্রশিক্ষিত কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা মডেলটি একটি ভিডিও বা ছবিতে মানুষের মুখের বদলে অন্য একটি বা যেকোনো কিছুর সমন্বয় দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা মডেলটি মানুষের মুখের বৈশিষ্ট্য, ত্বকের রং, টোন এবং আলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রাখতে প্রশিক্ষিত হয়, যাতে মুখ অদলবদলের ঘটনাটি নির্বিঘ্ন এবং পরিচ্ছন্ন হয়। এরপর, এই কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাটি মুখের নড়াচড়া বা মুভমেন্ট সেটআপ এর জন্য কাজ শুরু করে, যাতে নকল মুখ স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করে, অভিব্যক্তি ও মাথার নড়াচড়া এবং এমনকি সূক্ষ্ম পেশির টান মূল ভিডিওর সঙ্গে গতির সমন্বয় করে থাকে।
আলোচনার এ পর্যায়ে চলুন জেনে আশা যাক ভুল তথ্য ‘মিস ইনফরমেশন’ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য ‘ডিস ইনফরমেশন’-এর মধ্যে পার্থক্য কী? যখন ব্যক্তি বা সংস্থা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো তথ্য ভুলভাবে উপস্থাপন করে, তখন তাকে ভুল তথ্য (misinformation) বলা যেতে পারে। প্রায়শই যখন কোনো ব্রেকিং নিউজ (তাৎক্ষণিক খবর) প্রকাশিত হয় এবং বিস্তারিত তথ্য তখনো নিশ্চিত করা হয়নি, তখন ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ভুল তথ্যের আরেকটি উদাহরণ হলো, যখন আমরা তথ্যের যথার্থতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই না করেই মিথ্যা তথ্যকে সত্য হিসাবে প্রচার করে ফেলি। ২০১৮ সালে Dictionary.com ‘misinformation’ শব্দটিকে ‘ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার’ (বর্ষসেরা শব্দ) হিসাবে ঘোষণা করে। এই শব্দটি প্রথম ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ব্যবহৃত হয়েছিল।
কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও ভুল তথ্য খুব সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (এম আইটি) গবেষকদের ২০১৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে টুইটার (বর্তমানে ‘এক্স’ নামে পরিচিত) ব্যবহারকারীদের মধ্যে সঠিক তথ্যের চেয়ে মিথ্যা তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়া মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে যে কেউ শুধু একটি ক্লিকের মাধ্যমেই সহজেই একটি মিথ্যা তথ্য শেয়ার করে দিতে পারে, যার ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই মিথ্যা খবরটি বা অসত্য দাবিটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি যদি মূল পোস্ট বা দাবিটি সংশোধন করাও হয়, তাহলেও খুব একটা বেশি লাভ হয় না, যদি মানুষরা ইতোমধ্যেই আলাদা পোস্টে সেই তথ্য শেয়ার করে ফেলে। এভাবে সেই ভুল তথ্যটি সক্রিয়ভাবে এবং বারবার ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং এই মিথ্যা গুজব ছড়ানোর জন্য শেয়ারকারীদের কোনো জবাবদিহিতা থাকে না। যদিও ভুল তথ্য ছড়ানোর পরিণামের বিভিন্ন মাত্রার প্রভাব থাকতে পারে, তবে ভুল তথ্যের কারণে ইন্টারনেটের সমস্ত তথ্যের প্রতি আস্থা কমে যেতে পারে। ফলস্বরূপ, এই অবিশ্বাস গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষয় করতে পারে এবং সংবাদ মাধ্যমের পরিবেশকে (news ecosystem) দুর্বল করে দিতে পারে।
ভুল তথ্য বা মিসইনফর্মেশনের বিপরীতে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য ডিসইনফরমেশন হলো সেই মিথ্যা তথ্য যা অন্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য তৈরি করা হয় এবং সত্য ঘটনাকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো হয়। Disinformation শব্দটি রাশিয়ান শব্দ ‘dezinformácija’ (দেজিনফরমাসিয়া) থেকে এসেছে। রুশ সরকার ১৯২৩ সালে মিথ্যা প্রচারণা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ‘disinformation’ প্রতিরোধের ব্যবস্থা শুরু করে। প্রত্যেকেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্যের (disinformation) দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে; অনেক সময় অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই এটি (অজানতে) ছড়িয়ে দেওয়া সহজ। তবে, ভুল তথ্যের (misinformation) বিপরীতে, ‘disinformation’-এর ভিত্তি হলো বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রতারণামূলক। এটি প্রাথমিকভাবে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হয়, এমনকি যারা পরবর্তীকালে এটি শেয়ার করে তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে এটি শেয়ার করলেও।
‘Disinformation’ সাধারণত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, বিকৃত ছবি, এবং ভিডিও বা অডিও ক্লিপ আকারে শেয়ার করা হয়। অপপ্রচার (Propaganda) এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্য প্রায়শই একসাথেই রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
আজকে মূলত আমাদের উদ্দেশ্য হলো, এআই দিয়ে তৈরি যে বিভিন্ন কন্টেন্ট যেগুলো অনলাইন বা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয় বিশেষ করে বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের আজকের এই আলোচনাটি করছি। আজকের লেখায় আমি তিনটি কেস নিয়ে আলোচনা করব।
(প্রথম যে কেসটি নিয়ে কথা বলতে চাই, তা হলো, ধরুন একজন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী যিনি অনেক ভালো কাজ করছেন, এআই দিয়ে তার সম্পর্কে গত পাঁচ-ছয় বছরের বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবে তিনি কার কার সঙ্গে চলাফেরা করছেন, কোথায় যাচ্ছেন, এগুলো ব্যবহার করে ‘disinformation’ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে একটি ফেক কনটেন্ট তৈরি করবে, যে এই ব্যক্তি একটি বিশেষ জায়গায় গিয়েছিল, এবং একটি খারাপ কাজ করেছে। কন্টেন্টটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে মানুষ বিশ্বাস করে যে, উল্লেখিত ব্যক্তি ওই বিশেষ বা নিষিদ্ধ স্থানে গমন করে খারাপ কাজটি সংগঠিত করেছে। এ খবর বা তথ্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তির ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং তার সমাজে যে সম্মান তা ক্ষুণ্ন হওয়া শুরু করে।
দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা ঘটতে পারে যেখানে, কোনো ব্যক্তি যখন দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা করে, যেখানে তিনি কোনো সংস্কারমূলক কাজ করবেন অথবা বড় বাজেটের কোনো কাজ করবেন। সেই সংস্কারমূলক কাজের সময় যে কোনো অসৎ ব্যক্তি তার সম্পর্কে এমন কোনো খবর বা কনটেন্ট তৈরি করতে পারে, যার মাধ্যমে প্রচার করা হবে যে, এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য হলো অসদুপায় অবলম্বন করা বা প্রকল্প থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা। এই তৈরিকৃত কন্টেন্টে তারা প্রচার করার চেষ্টা করবে, যেখানে দেখা যাবে বা কথোপকথন শোনা যাবে এমনভাবে যে, সংস্কারকারী ব্যক্তি এই জনস্বার্থমূলক প্রজেক্ট যেমন রাস্তা, হাসপাতাল বা স্কুলের প্রকল্প থেকে অর্থ আত্মসাতের পরিকল্পনা বা চেষ্টা করছেন।
এ ধরনের ফেক কন্টেন্টে দেখা যাবে বা শোনা যাবে যে, ওই ব্যক্তি বলছেন এই প্রকল্প থেকে তিনি কি পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা করছেন যার ফলে তিনি হয়তো বিদেশে একটি বাড়ি কিনতে পারবেন অথবা সম্পদ তৈরি করতে পারবেন। অথবা তাকে বলতে শোনা যাবে যে, তিনি অন্য কোনো ব্যক্তিকে মোটা অংকের কোনো টাকা এই প্রজেক্ট থেকে আত্মসাৎ করে পাঠিয়ে দেবেন। এ ধরনের একটি কনটেন্ট তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করা হবে যে ওই ব্যক্তি কত খারাপ একজন মানুষ।
তৃতীয় আরেকটি ঘটনা হতে পারে, যেটি মূলত কেলেঙ্কারি বা লজ্জাজনক কোনো ঘটনা সম্পর্কিত। এ রকম একটি সাজানো ঘটনায় দেখা যাবে, কোনো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে। তার হয়তো বিভিন্ন অপ্রীতিকর অবস্থার ছবি বা ভিডিও ইন্টারনেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে এবং প্রচার করা হবে যে তিনি চরিত্রগতভাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট একজন ব্যক্তি। এই কন্টেন্টগুলো যাচাই-বাছাই করার সুযোগের আগেই তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে যা কিনা ওই বিশিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা এবং ইমেজ মুহূর্তের মধ্যেই ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারে। তিনি যদি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি হন, এই অপপ্রচারের কারণে তার দলীয় অবস্থানের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, তার নোমিনেশন বাতিল হয়ে যেতে পারে, তার সমর্থন মুহূর্তের মধ্যেই অনেক কমে যেতে পারে এবং তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান ধ্বংস হয়ে যাবে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতিরোধ করার কি কোনো উপায়ই নেই? ভুল তথ্য (misinformation) এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্যের (disinformation) বিস্তার সমাজের জন্য, বিশেষ করে গণতন্ত্রের জন্য, নানা কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। যারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চায়, তাদের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ‘disinformation’ তৈরি করা এবং তা ছড়িয়ে দেওয়া একটি প্রধান কৌশলে পরিণত হয়েছে। অনির্বাচিত কর্মকর্তা, রাজনৈতিক প্রার্থী, কর্মী, এবং অন্যরা, যারা নিজেদের স্বার্থ ও লাভের জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে কাজ করে, তারা ভুল তথ্য বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ভুল তথ্য ব্যবহার করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঘটনাকে উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে। ২০২০ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, মেইল-ইন (mail-in) এবং অনুপস্থিত (absentee) ভোটিংয়ের অনুমোদনের ক্ষেত্রে একটি নতুন এবং ক্রমবর্ধমান পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবধান (partisan gap) তৈরি হয়েছিল, যার প্রধান কারণ ছিল ভোটার জালিয়াতির (voter fraud) ব্যাপকতা সম্পর্কিত মিথ্যা তথ্যের (disinformation) প্রচার। সেই সময়ে কিছু রাজনৈতিক প্রার্থী দাবি করেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তিদের নামে প্রচুর ভোট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠায় ২০২০ সালের নির্বাচনকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।
যাই হোক, পরবর্তীতে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক মার্কিন নির্বাচনগুলোতে মৃত ব্যক্তিদের ভোট দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল, যেখানে আট বছরের মেয়াদে একটি রাজ্যে ৪.৫ মিলিয়ন (৪৫ লাখ) ভোটারের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের ভোট দেওয়ার মাত্র ১৪টি সম্ভাব্য ঘটনা (বা ০.০০০৩ শতাংশ) পাওয়া গেছে, যা কোনো নির্বাচনের ফলাফলে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলার জন্য যথেষ্ট নয়। এ ধরনের ঘটনাসহ আরো অনেক ‘disinformation’ প্রচারের কারণে আমেরিকান ভোটারদের একটি বিশাল অংশ রয়েছে যারা বিশ্বাস করে না যে মার্কিন নির্বাচনগুলো মুক্ত, অবাধ এবং সুরক্ষিত। ২০২০ এবং ২০২১ সালজুড়ে, অসৎ ব্যক্তিরা অতীতের ‘disinformation’-এর ঘটনাগুলোকে নতুন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে তাদের নির্বাচনি প্রচারণার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে এই দাবিগুলোকে ব্যবহার করেছিল।
উপরে উল্লেখিত সবগুলো কনটেন্ট যেমন এআই দিয়ে তৈরি করা সম্ভব ঠিক তেমনি এই কন্টেন্টগুলোর শনাক্তকরণ এবং প্রচার রোধে এআই ব্যবহার করা সম্ভব। এআই দ্বারা তৈরি জাল কনটেন্ট (fake contents) মোকাবিলায় সাধারণত তিন ধরনের এআই ব্যবহার করা হয়। আমরা প্রধানত রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং ব্যবহার করে থাকি। রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং হলো এক ধরনের মেশিন লার্নিং, যেখানে একটি এজেন্ট বা সিস্টেম (যা শেখে এবং সিদ্ধান্ত নেয়) একটি এনভায়রনমেন্ট বা পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। এজেন্টটি বিভিন্ন অ্যাকশন বা কাজ (যা সে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় করতে পারে) সম্পাদন করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে শেখে এবং সেই কাজের প্রতিক্রিয়া বা ফিডব্যাক হিসাবে রিওয়ার্ড বা পুরস্কার (একটি ইতিবাচক সংকেত) অথবা পেনাল্টি বা শাস্তি (একটি নেতিবাচক সংকেত) পায়।
এজেন্টটি একটি ‘পলিসি’ (কাজ বেছে নেওয়ার কৌশল) শেখে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মোট বা সঞ্চিত পুরস্কারকে সর্বাধিক করে তোলে; এটি অনেকটা মানুষ বা প্রাণীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার মতোই। এই চেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়াটি এজেন্টকে বিভিন্ন স্টেট বা পরিস্থিতিতে (পরিবেশের বর্তমান অবস্থা) সেরা কাজটি বেছে নিতে শেখায়, এবং এর জন্য তাকে কোনো সঠিক উত্তর সরাসরি প্রোগ্রাম করে দিতে হয় না।
উদাহরণস্বরূপ, একটি রোবট একটি গোলকধাঁধায় (maye) প্রস্থান পথের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য ইতিবাচক পুরস্কার এবং দেয়ালে ধাক্কা খেলে শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে পথ চলতে শিখতে পারে, এবং শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকরী পথটি নিজেই আবিষ্কার করে ফেলে। এই এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা সাধারণত বিভিন্ন ধরনের টুলের মাধ্যমে মিথ্যা কন্টেন্টগুলো শনাক্ত করে থাকি। আজকের আলোচনায় আমরা শুধু রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়েই শেষ করলাম। পরবর্তীতে আমরা অন্যান্য প্রতিকারমূলক এআই প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা এবং তাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব বলে আশা রাখছি। এবং আমরা আরো আলোচনা করব কীভাবে এআই প্রযুক্তিকে ভিন্ন এআই প্রযুক্তি দিয়ে থামানো যায়, প্রতিরোধ করা যায়, এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আজকের জন্য এটুকুই, ধন্যবাদ সবাইকে।
লেখক : প্রফেসর অফ বিজনেস এনালিটিক্স এন্ড অ্যাপ্লায়েড এআই,উপপরিচালক, সেন্টার ফর অ্যাপ্লাইড এন্ড রেস্পন্সিবল এআই, নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটি, নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া।
কেকে/এআর