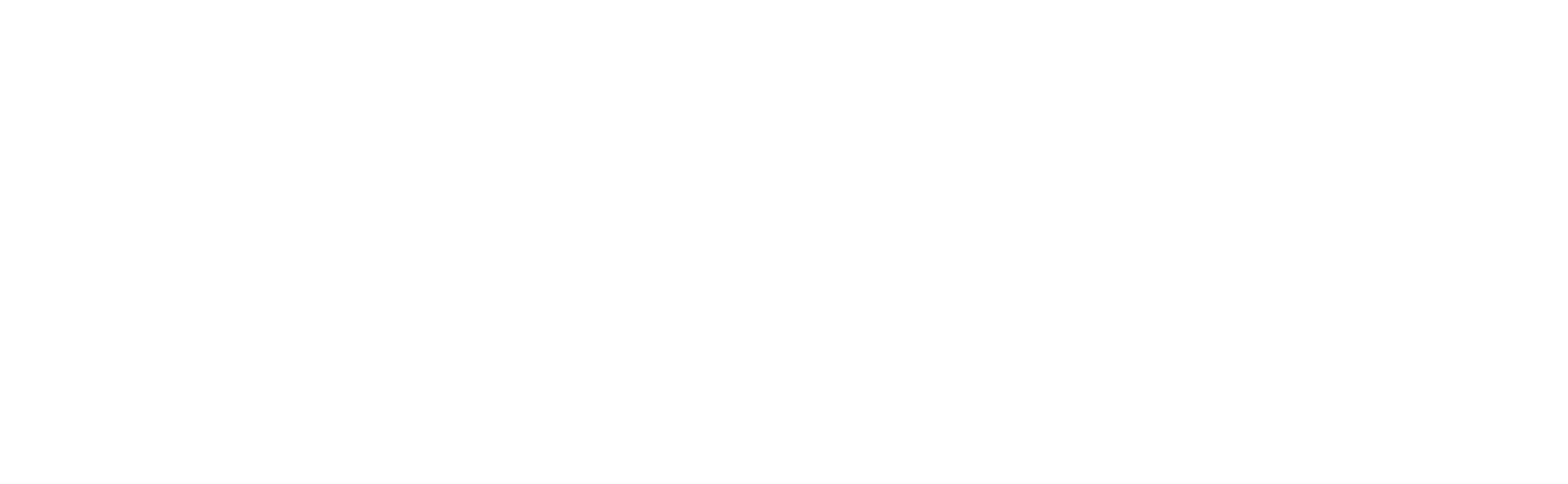দলিত মানুষের রূপকার
রোকেয়া ডেস্ক
🕐 ১:৫৭ অপরাহ্ণ, জুন ০২, ২০২১

প্রায় ছয় দশক ধরে নিপীড়িত মানুষের অলিখিত সংগ্রামী জীবনের ইতিহাসকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। সমগ্র জীবন মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি প্রবল দায়বোধে সাহিত্য রচনা করেছেন তিনি। জল-মাটি-শস্যের গন্ধবাহী মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে যে স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছে তা বহমান আছে এবং থাকবে আরও বহুকাল। দলিত মানুষের রূপকার মহাশ্বেতাকে নিয়ে লিখেছেন সাইফ-উদ-দৌলা রুমী
জন্ম ও শৈশব
১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকার আরমানিটোলার জিন্দাবাহার লেনের মামা বাড়িতে মহাশ্বেতা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মণীশ ঘটকের বয়স তখন পঁচিশ বছর এবং মা ধরিত্রী দেবীর আঠারো। বাবা ছিলেন একাধারে কবি এবং সাহিত্যিক; ‘যুবনাশ্ব’ ছদ্মনামে বাংলা ছোটগল্পে এক নতুন যুগের প্রণেতা। মাও কবি ছিলেন, যদিও লিখেছেন সামান্য কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্র তার ছিল বিস্তৃত। মহাশ্বেতা দেবীর প্রমাতামহ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন রামমোহন রায়ের প্রথম জীবনীকার; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার কন্যা কিরণময়ীর অর্থাৎ মহাশ্বেতার মাতামহীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, সাহিত্যপাঠ ও উদার মানসিকতা মহাশ্বেতার মানসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছিল। ইতিহাসের প্রতিকিরণময়ী দেবীর টান ছিল অসামান্য, তার গ্রন্থাগারে প্রায় প্রতিটি জেলার ইতিহাসের সংগ্রহ ছিল; পরবর্তীকালে সাহিত্যিক মহাশ্বেতার ইতিহাসপ্রিয়তার অন্যতম উৎস সম্ভবত তার মাতামহী। শৈশবে তিনি তার কাছ থেকে দেশি রূপকথা ছাড়াও শুনেছিলেন ডেভিড কপারফিল্ড ও অলিভার টুইস্টের গল্প। দিদিমা কিরণময়ী দেবীর ঔদার্যের একটি নিদর্শন মহাশ্বেতা দেবীর স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়। মণীশ ঘটক ও ধরিত্রী দেবীর নয় সন্তানের মধ্যে মহাশ্বেতা সবার বড়। এ সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে মহাশ্বেতা বলেছেন, ‘বাবারা সব ভাইবোন যেমন আমার ভাইবোনরাও জন্মসূত্রে আঁকার হাত, গানের গলা, অভিনয় ক্ষমতা পেয়েছিল। উত্তরাধিকারলব্ধ সম্পত্তিতে কিছু হয় না। নিরন্তর চেষ্টায় তাকে বাড়াতে হয়।’ নিজ সম্পর্কেও তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন; তিনি বলতেন যে, তিনি লিখতে-লিখতে লেখক হয়েছেন। মহাশ্বেতার বাবা মণীশ ঘটক প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাস করে আয়কর বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন ১৯২৯ সালে। বাবার বদলির চাকরি-সূত্রে তারা সপরিবারে ঢাকা, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, ফরিদপুর, মেদেনীপুর, বহরমপুর বিভিন্ন স্থানে থেকেছেন। তবে চাকরিতে উন্নতি করা তার ধাতে ছিল না; সকলের পদোন্নতি হতো, তার ঘটত পদাবনতি।
শিক্ষা জীবন
মহাশ্বেতা দেবীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঢাকার ইডেন মন্টেসরি স্কুলে মাত্র চার বছর বয়সে; কিন্তু স্কুলে তিনি নিয়মিত হননি। বাবার বদলির সূত্রে মাঝে বিদ্যালয়-জীবনে ছেদ পড়লেও বাড়িতে পড়াশোনার কোনো বিরাম ছিল না। ১৯৩৫ সালে বাবা মেদেনীপুরে বদলি হলে তিনি সেখানকার মিশন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরের বছর ১৯৩৬ সালে তাকে ভর্তি করা হয় শান্তিনিকেতনে। মাত্র দশ বছর বয়সে মা-বাবাকে ছেড়ে শান্তিনিকেতন যেতে মহাশ্বেতা কেঁদেছিলেন; কিন্তু তিন বছর পর শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় আসতে কেঁদেছিলেন অনেক বেশি। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি এই দুই বছর শান্তিনিকেতনে পড়ার অভিজ্ঞতা তাকে ঋদ্ধ করেছিল অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসা ও রবীন্দ্র-প্রভাবিত মামাবাড়ির বলয়ে বেড়ে ওঠা মহাশ্বেতার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সপ্তম শ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথকে তিনি পেয়েছিলেন বাংলার শিক্ষক হিসেবে। এ-সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথকে। শান্তিনিকেতনের এই দুই বছরের স্মৃতিচারণ রয়েছে তার দুটি বইয়ে- আমাদের শান্তিনিকেতন (২০০১) ও ছিন্ন পাতার ভেলায় (২০০৬)। তাকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরতে হয় অসুস্থ মা ও ছোট পাঁচ ভাইবোনের দেখাশোনা করার জন্য। মাত্র তেরো বছর বয়সে গৃহকর্ত্রীর কঠোর দায়িত্ব তিনি পালন করা শুরু করেন সুচারুভাবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও সাহিত্য পাঠ থাকে অব্যাহত। ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পর তিনি বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস এইটে ভর্তি হন। এ সময়ে বন্ধুসম কাকা ঋত্বিক ঘটকের সান্নিধ্যে তিনি ইংরেজি সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন। দেশ-কালের অস্থিরতা ও বিশ্ব সাহিত্যের সংযোগে তার লেখক জীবনের প্রস্তুতিপর্ব ধরে নেওয়া যায় সে সময়কে। এ-সময়ই তার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৪০-এ রংমশাল পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেবেলা’ সম্পর্কে লিখেছিলেন তিনি এবং এটি ছিল তার প্রথম প্রকাশিত লেখা।
১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাস করে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন মহাশ্বেতা। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও তিনি পার্টির কর্মকা-ের সঙ্গে যুক্ত হন। কমিউনিজমের প্রতি আস্থা গড়ে উঠেছিল সম্ভবত মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণেই। দলীয় রাজনীতিতে তার আস্থা ছিল না, রাজনীতির ছকে বাঁধা জীবন তার অভিপ্রেত নয়, মানবতাবাদে বিশ্বাসী হলেও তত্ত্বনির্ভর হয়ে ওঠেননি তিনি।
কর্মজীবন
ছাত্রীজীবনেই অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার অভীপ্সায় ১৯৪২ সালে সহপাঠিনীদের সহযোগিতায় ‘চিত্ররেখা’ নামে কাপড় ছাপানোর দোকান খুলেছিলেন। দোকানের মূলধন হিসেবে প্রদত্ত ৩০ টাকাও তার নিজের উপার্জনের। হ্যান্ডবিল দেখে ভাই অবলোকিতেশের বুদ্ধি ও মায়ের সক্রিয় সমর্থনে ঢাকা থেকে কাপড় রং করার সাবান ভিপি করে আনিয়ে কলেজে বিক্রি করতেন। সেই ব্যবসা থেকে জমেছিল ওই ৩০ টাকা। এ ব্যবসা অবশ্য তিনি স্বল্প সময়ই চালিয়েছেন এবং তারপর আবারো ব্যস্ত হয়েছেন পড়াশোনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকা-ে। বাবার বদলিসূত্রে ১৯৪৪ সালে মহাশ্বেতা চলে আসেন রংপুরে। সেখানে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী বিনয় রায় ও রেবা রায় চৌধুরীর সান্নিধ্যে এসে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তার এ অভিজ্ঞতা সম্ভবত পরবর্তী জীবনে তাকে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। পুনর্বার তিনি শান্তিনিকেতনে বিএ পড়তে যান ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে, সাংসারিক দায়িত্ব থেকে কিছুটা অব্যাহতি পেয়ে, ছোট বোন মিতুল সে দায়িত্ব নেওয়ায়। দ্বিতীয়বারে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতায় প্রতিবাদ-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। গান্ধী দিবসে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের, কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী করেছেন। এসবই তার সংগ্রামী চেতনাকে আরো উজ্জীবিত করেছে এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহের কাহিনি রচনার পূর্বসূত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। শান্তিনিকেতনে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কথায় তিনি ছোটগল্প লেখা শুরু করেন। সে সময়ে তার তিনটি ছোটগল্প দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়। প্রতিটি গল্পের জন্য তিনি পারিশ্রমিক হিসেবে ১০ টাকা করে পান; লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার প্রেরণা তৈরি হয় এ সময়টাতে।
১৯৪৬ সালে ইংরেজি অনার্সসহ বিএ পাস করে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরে আসেন মহাশ্বেতা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ (ইংরেজি) ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণামে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে তার লেখাপড়া স্থগিত হয়ে যায়। তাই বলে তিনি থেমে থাকেননি, নানা কাজে যুক্ত থেকেও প্রায় ১৭ বছর পর ১৯৬৩ সালে তিনি এমএ পাস করেন। প্রখ্যাত নাট্যকার ও সাহিত্যিক বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে পারিবারিকভাবে তার বিয়ে হয় ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে। সে-সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে বিজন ভট্টাচার্য কোনো অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সংসার চালানোর পুরো দায়িত্ব কাধে নিয়ে মহাশ্বেতা ১৯৪৮ সালে পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। জীবিকার তাগিদে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন; যথেষ্ট সংগ্রামসংকুল ছিল তার কর্মজীবন। ১৯৪৯ সালে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে চাকরি পেলেও তা করা হয়নি, বড় অফিসার বাবা মণীশ ঘটকের কন্যার কেরানি পদে যোগ দেওয়া সামাজিকভাবে নিন্দনীয় বলে। ওই বছরই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পোস্টাল অডিটে আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে চাকরি পান; কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় রাজনৈতিক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বা স্বামী কমিউনিস্ট হওয়ার অপরাধে। প্রখ্যাত আইনবিদ অতুল গুপ্তের চেষ্টায় অস্থায়ীভাবে পুনর্বহাল হলেও ১৯৫০ সালে তার ড্রয়ারে মার্কস ও লেনিনের বই পাওয়ার অপরাধে তাকে দ্বিতীয়বার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর আর সরকারি চাকরিতে ফেরার চেষ্টা করেননি তিনি।
চাকরি যাওয়ার পর তিনি সংসার চালাতে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কাপড় কাচার সাবান বিক্রি এবং সকাল-বিকেল টিউশনি শুরু করেন। একমাত্র সন্তান নবারুণের আগমন তার জীবনযুদ্ধকে আরো কঠিন করে তোলে। ১৯৫৭ সালে রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পাওয়ার পর কিছুটা স্থিতি আসে জীবনে। ১৯৬৩ সালে এমএ পাস করার পর ১৯৬৪ সালে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন তিনি। লেখাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার পর ১৯৮৪ সালে তিনি সেখান থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। দেশ পত্রিকায় তার প্রথম জীবনীগ্রন্থ ঝাঁসীর রাণী ৬ আগস্ট ১৯৫৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে পুস্তকাকারে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় নিউএজ প্রকাশনা সংস্থা থেকে। দেশ পত্রিকাতেই ‘যশবমত্মী’ নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এর আগে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী ও সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে তিনি অনেক গল্প লেখেন সচিত্র ভারত পত্রিকায়।
ব্যক্তিগত জীবন
১৯৬১-৬২ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। ১২-১৩ বছরের নবারুণকে ফেলে চলে আসতে হয় তাকে। এ-যন্ত্রণা তাকে দীর্ণ করে তীব্রভাবে। অতিমাত্রায় ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান তিনি, কিন্তু ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় বেচে যান। বেদনা ভোলার জন্যই যেন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ১৯৬৩-৬৪ সালে অসিত গুপ্তকে। কিন্তু সে বিয়েও সুখের হয়নি; ১৯৭৫-৭৬ সালে আবার বিবাহ বিচ্ছেদ। এরপর থেকে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন। কাজকে সঙ্গী করে এগিয়ে যাওয়া জীবনের পথে এবং সে পথে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া নিপীড়িত অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে।
১৯৭৯ সালে পিতার মৃত্যুর পর মণীশ ঘটক সম্পাদিত বর্তিকা পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহাশ্বেতা এবং এ পত্রিকাকে পরিণত করেন ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষিমজুর, আদিবাসী, শিল্প-শ্রমিক তথা সমাজের মুখপত্রে।
বর্তিকার স্বতন্ত্র চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন বৈপ্লবিক দিগন্ত উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস মহাশ্বেতাকে বাংলা লিটল-ম্যাগাজিন আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। সাংবাদিকতা তার সাহিত্য-রচনার অন্তরায় হয়নি বরং সহায়ক হয়েছে। ১৯৮২-৮৪ সালে তিনি যুগান্তরে ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন কলেজ থেকে দুই বছরের ছুটি নিয়ে; আদিবাসী এবং ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালোবাসায় সাহিত্যের আসরে উপস্থাপিত করেন সে জীবনকে।
সাহিত্যচর্চা
ঝাঁসীর রাণী তাকে লেখক হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। ভূগোল, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি তার লেখার অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে এ সময় থেকেই। ইতিহাস-আশ্রিত এ কাহিনি লেখার ইতিহাসও বেশ উপভোগ্য। হিন্দি ফিল্মের চিত্রনাট্য লেখার জন্য বিজন ভট্টাচার্য মুম্বাই যান ১৯৫২ সালে, মহাশ্বেতা তার সহযাত্রী হন। মুম্বাইয়ে বড় মামা, শচীন চৌধুরীর কাছে থাকতেন। মামার কাছ থেকে তিনি ইতিহাসের, বিশেষত সিপাহি বিদ্রোহের কাহিনি পড়েন।
এ বিষয়কে গ্রহণ করে তিনি ঝাঁসীর রাণীর জীবনীগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন এবং অল্প সময়ে ৪০০ পাতা লিখে ফেলেন; কিন্তু তাতে তৃপ্ত হতে না পেরে রচনার কাজ স্থগিত রেখে বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে ১৯৫৪ সালে বুন্দেলখের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। কয়েক মাস একা-একা বুন্দেলখের আনাচে-কানাচে ঘুরে সংগ্রহ করেন রানী সম্পর্কিত আঞ্চলিক লোকগীতি এবং লোককাহিনি। রানীর জীবনীকার বৃন্দাবনলাল ভার্মা ও রানীর ভাইপো গোবিন্দ চিন্তামণির সঙ্গে যোগাযোগ করে ঝাঁসির সঙ্গে সম্পর্কিত আরো কিছু স্থান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কলকাতায় ফিরে এসে নতুন করে লেখেন ঝাঁসীর রাণী। এ-সময় থেকেই তার পেশাদারি লেখকের পথ সুগম হয়।
লেখক জীবনে সর্বদাই তিনি তথ্য, উপাত্ত, লোকজ উপাদান সংগ্রহ করে এবং বিষয়টিকে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন; সাহিত্য সৃষ্টি তার কাছে সৌখিন মজদুরি নয়, বরং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রকাশ। ইতিহাস আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ ঝাঁসীর রাণী সাহিত্যিক হিসেবে মহাশ্বেতার অবস্থানকে একটি শক্ত ভিত্তি দেয়। সেই ভিত্তিতেই তার পরবর্তী জীবনের সুউচ্চ সাহিত্য-পিরামিড স্থাপিত।
১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাস নটীর পটভূমি ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ; এ বিদ্রোহের ঝঞ্ঝাসংকুল পটে খোদাবক্স ও মোতির প্রণয়ের আখ্যানে নটী ঐতিহাসিক উপন্যাসের শর্তপূরণ করেছে। মহাবিদ্রোহের পটভূমিতে এ সময় তিনি আরো লিখেছেন উপন্যাস অমৃত সঞ্চয়ন (১৯৬২) ও গল্প ‘চম্পা’ (১৯৫৯); আঠারো শতকের বর্গি আক্রমণকে উপজীব্য করেছেন আঁধার মানিক (১৯৬৬) উপন্যাসে। এ কাহিনিগুলোতে তিনি আঠারো ও উনিশ শতকের বিদ্রোহ ও সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনকে একবিন্দুতে মিলিয়েছেন। তার ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য রাজবৃত্ত নয়, লোকবৃত্তকে প্রাধান্য দিয়েই রচিত। ইতিহাসকে ভিন্নভাবে দেখার তার যে প্রবণতা তা আঁধার মানিক গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্ট করেছেন তিনি, ‘ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে একই সঙ্গে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংস্তূপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। আর তখনি, এই ভিতরপানে চোখ মেলার দরুনই অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে সমাজনীতি ও অর্থনীতি; বেরিয়ে আসতে বাধ্য।
কেননা, সমাজনীতি ও অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত রাজনীতির পটভূমি তৈরি করে, তার সিদ্ধি ও সাফল্য এনে দেয়। এ সমাজনীতি ও অর্থনীতির মানে হলো লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবনব্যবস্থা।’
নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হাজার চুরাশির মা উপন্যাসটি মহাশ্বেতার কথাসাহিত্যের এক মাইলফলক বলে বিবেচিত হয়, যদিও এর আগে ‘রং নাম্বার’, ‘শরীর’, ‘প্রাত্যহিক’ গল্পেও একই বিষয় অবলম্বিত হয়েছিল। ‘রং নাম্বার’ গল্পে নকশাল আন্দোলনে নিহত দীপঙ্করের বাবা তীর্থবাবুর মানস জগতের উন্মোচনের মতো হাজার চুরাশির মা উপন্যাসে নকশালপন্থী নিহত তরুণ ব্রতীর মা সুজাতার অন্তর্দহনকে বিস্মৃতি দিয়ে সত্তরের উত্তাল সময়কে ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের রক্তাক্ত এক অধ্যায়কে সাহিত্যের দলিলীকরণের মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে লেখক মধ্যবিত্তের আত্মতৃপ্তি ও মুগ্ধ সংকীর্ণতার প্রাকারে তীব্র আঘাত হানেন। গোর্কির মায়ের মতোই ব্রতীর মা সুজাতার অরাজনৈতিক সত্তা রূপান্তরিত হয় বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ সত্তায়। উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও মহাশ্বেতা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-সংগ্রামকে উপজীব্য করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। ‘দ্রৌপদী’, ‘জাতুধান’, ‘শিকার’, ‘শিশু’, ‘সাগোয়ানা’, ‘লাইফার’, ‘মাছ’, ‘বিছন’ প্রভৃতি গল্পে সমাজের নানা অবিচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনতার প্রতিবাদের শিল্পভাষ্য নির্মিত হয়েছে। ইতিহাসভিত্তিক গল্প, যেমন ‘দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনি’, ‘রোমথা’ প্রভৃতিতেও মানুষের অসহায়ত্ব ও নিপীড়িত হওয়ার ইতিবৃত্তকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
আদিবাসীদের মধ্যেও অবহেলিত লোধা-শবরদের নিয়ে মহাশ্বেতা একাধিক গল্প লিখেছেন। ‘কুড়োনির বেটা’, ‘চোর’, ‘অর্জুন’, ‘উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু’, ‘তারপর’ প্রভৃতি গল্পে শবরজীবনের নানাপ্রান্ত শিল্পরূপ পেয়েছে। ‘ডাইনি’ ও ‘প্রেতোৎসব’ গল্পে আদিবাসী জীবনে ডাইন-ডাইনি বিশ্বাসের স্বরূপ এবং তার সূত্র ধরে উচ্চশ্রেণির সুবিধাবাদী মানুষের স্বার্থসিদ্ধির কৌশল বিশেস্নষণ করা হয়েছে।
শেষ জীবন
মহাশ্বেতা দেবী অর্ধশতক ধরে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্যসহ নানাবিধ ধারায় সক্রিয় থেকে বাংলা সাহিত্যকে দান করেন অফুরন্ত। কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, তার সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন প্রাদেশিক ও বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে তাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দিয়েছে প্রভূত পরিচিতি। পেশাগত কারণে বেশকিছু বাণিজ্যিক রচনা করতে হয়েছে; কিন্তু তিনি কালজয়ী হয়েছেন ভারতবর্ষীয় ব্রাত্য মানুষ, বিশেষত আদিবাসী জীবনের কথাকার হিসেবে। সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন, ইতিহাসপ্রিয়তা ও প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী চেতনা তাকে আদিবাসী জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত তার আদিবাসী-সম্পর্কিত রচনাগুলো বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের আস্বাদ এনেছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধে সাহিত্য-রচনার পাশাপাশি তিনি জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কাজের সঙ্গে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের সাহচর্যে তাদের জীবনকেই তার পরবর্তী জীবনের সাহিত্য-উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ব্রাত্যজন ও আদিবাসী জীবনকে কেবল কথার মালা গেঁথে মহিমান্বিত করেছেন মহাশ্বেতা, তা নয়; বরং সক্রিয় থেকেছেন তাদের নানা অধিকার-দাবি আদায়ে। অসংখ্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি এবং সক্রিয়ভাবে আমৃত্যু মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামে শামিল হয়েছেন; প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ’, পশ্চিমবঙ্গের আটত্রিশ গোষ্ঠীসহ সকল আদিবাসীর মিলনমঞ্চ।
সাহিত্যে স্বীকৃতিস্বরূপ মহাশ্বেতা বহু পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চৈতন্য লাইব্রেরি পুরস্কার (১৯৫৮), শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার (১৯৬৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মৃতিপদক (১৯৭৮), সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯), নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক শেফালিকা স্বর্ণপদক (১৯৮১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ভূবনমোহিনী দেবী পদক (১৯৮৩), ভারত সরকারের ‘পদ্মশ্রী’ (১৯৮৬), জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৮৯), বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার (১৯৯০), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৯৬), ম্যাগসাইসাই পুরস্কার (১৯৯৭), সাম্মানিক ডক্টরেট রবীন্দ্রভারতী (১৯৯৮), ফেলোশিপ : বোম্বে, এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৯৮), ইয়াসমিন স্মৃতি পুরস্কার, দিল্লি (১৯৯৮), সাম্মানিক ডি.লিট ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ ইউনিভার্সিটি, কানপুর (২০০০), সাম্মানিক ডি.লিট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (২০০১), ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মাননা (২০০১), ইতালির ‘প্রিমিও নোনিনো রিসিট ডি আউর’ (২০০৫) এবং সমগ্র সাহিত্য রচনার জন্য ফরাসি সরকার কর্তৃক ‘অফিসার অব দি অর্ডার অব আর্টস অ্যান্ড লেটারস’ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। নিজ সংকল্পে স্থির থাকতে পারেননি তিনি। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় তিনি সংকল্প ব্যক্ত করেছিলেন যে, তিনি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাঁচবেন এবং পরবর্তীকালের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হবেন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মানুবর্তী হয়ে নয় বছর আগেই তাকে চলে যেতে হলো ২০১৬ সালের ২৮ জুলাই। ৯১ বছরের দীর্ঘ জীবনে অফুরন্ত দিয়েছেন তিনি বাংলা সাহিত্যকে। একজন দায়িত্ববান সাহিত্যিক হিসেবে অন্যায়-অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে ‘সূর্য-সম ক্রোধ’ নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী সমগ্র জীবন ‘মানুষের কথা’ লিখেছেন। শিল্পের চেয়ে মানবিকতার দাবিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি সর্বদা; তবে তাতে শিল্প নিষ্প্রাণ হয়নি বরং মানবতার রসে জারিত হয়ে সপ্রাণ হয়েছে। বহুপ্রজ এই লেখক সংখ্যায় নয়, বিষয়বিন্যাস এবং নির্মাণ-কৌশলের অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন এবং নিজেকে পরিণত করেছেন এ অঙ্গনের এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্বে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি মানুষের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছেন এবং যতদিন আদিবাসীরা বেঁচে থাকবে ততদিনই তিনি তাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মহাশ্বেতা বেঁচে থাকবেন তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে; ভবিষ্যৎকাল হয়তো নতুন মূল্যায়নে নতুন দৃষ্টিকোণে তার সাহিত্যপাঠ করবে, কালের গর্ভে তা হারিয়ে যাবে না।
এ বিভাগের অন্যান্য সংবাদ