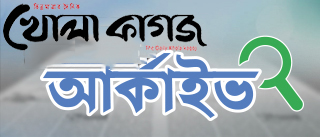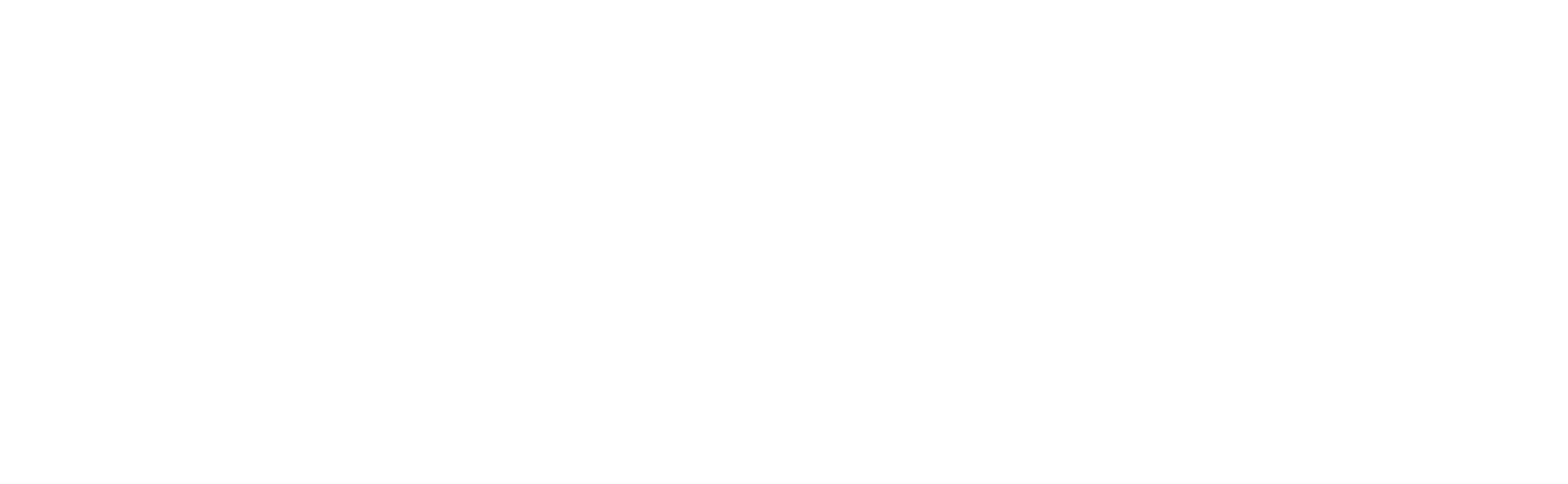শৃঙ্খলবন্দি নারীমুক্তির সংগ্রাম
সাইফ-উদ-দৌলা রুমী
🕐 ৩:২৩ অপরাহ্ণ, মার্চ ১০, ২০২১

১৯৫৯ সালে সিমোন দ্য বোভোয়া বলেছিলেন, ‘নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে।’ শিশু তার লিঙ্গ সম্পর্কে সচেতন থাকে না। চুলে ফিতে বেঁধে, ফ্রক পরিয়ে, হাতে পুতুল তুলে দিয়ে তাকে ‘নারী’ হিসেবে নির্মাণ করে সমাজ। ‘নির্মাণ’ কিন্তু এখানেই থেমে থাকে না। আসলে লিঙ্গ বৈষম্য সভ্যতার আমদানি করা। সেই সভ্যতা, ‘জোর যার মুলুক তার’ এই তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে মেয়েদের মস্তিষ্কে তালা দিয়ে রেখেছিল। সে তালা ভাঙতে দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে নারীকে। অন্তঃপুরের তালা ভেঙে নারীমুক্তির সেই ইতিহাস তুলে ধরেছেন সাইফ-উদ-দৌলা রুমী।
সাংবিধানিক অবস্থান
বাংলাদেশে নারীরা রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনগ্রসর থাকায় বাংলাদেশের সংবিধানে তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ সুবিধা ও অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত প্রথম ও মূল সংবিধান এবং পরবর্তীতে কয়েকটি সংশোধনীতে তাদের বাড়তি সুযোগ সুবিধা ও সংরক্ষিত অধিকার দেওয়ার কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযোজন করা হয়েছে।
জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসন রাখা হয়েছে। তবে সাধারণ আসনের নির্বাচনে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কোনো বাধা নেই। সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ৬৫ নম্বর ধারার মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছে। ১৯৭৩-এ সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি এবং এ আসনগুলি দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৭৯ সালে নারী দশকের প্রভাবে এ আসন সংখ্যা ৩০-এ বাড়ানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী ১৯৮৮ সালের সংসদে সংরক্ষিত আসন ছিল না। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সালে পুনরায় ১০ বছরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৪ সালে এ সংখ্যা ৪৫-এ উন্নীত করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১১ সালের ৩ জুলাই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা কতটা সমতা ভোগ করছে আইন কাঠামো এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। নারী অধিকার রক্ষাকারী আইনসমূহ নারীর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক সমতার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সুরক্ষায় আইন ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপ করতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ঘোষণা করে এবং তাতে রাষ্ট্রকে এ লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে নিদের্শনা দেয়। সংবিধান নারীর অধিকার ও মর্যাদার যে নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং সামাজিক নিয়মাচার ও রীতি হিসেবে ব্যক্তি আইনে যা প্রতিফলিত হয়েছে এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করে সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-আইন বস্তুত পারিবারিক আইনসমূহের ভিত্তি। সুতরাং বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, শিশুরক্ষা ও উত্তরাধিকার বিষয়ে দেওয়ানি আইন ও ব্যক্তি আইন নারী-পুরুষের ব্যবধান অব্যাহত রেখে চলেছে।
মুসলিম আইন অনুসারে মৃত স্বামীর সগোত্রীয় উত্তরাধিকারী থাকলে স্ত্রী সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে এক-অষ্টমাংশ পায়, আর সেরকম উত্তরাধিকারী না থাকলে পায় মৃত স্বামীর সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। একমাত্র কন্যা মৃত পিতা বা মাতার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। পুত্র ছাড়া একাধিক কন্যা থাকলে কন্যাগণ যৌথভাবে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়। যদি সেখানে কোনো পুত্র থাকে তাহলে কন্যা অথবা প্রত্যেক কন্যার অংশ হবে পুত্র বা পুত্রদের অংশের অর্ধেকের সমান। মুসলিম আইন অনুসারে মা কখনও সন্তানদের অভিভাবকত্বের অধিকারী নন। মা সাত বছর বয়স পর্যন্ত পুত্র সন্তানদের ও কন্যা সন্তান সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত তাদের যতœ করার ও অভিভাবকত্বের অধিকারী।
মহলবন্দি
পাল রাজা ধর্মপালের স্ত্রী রানী বল্লভদেবীকে বনবাসে পাঠানো হয়। কারণ তিনি কোনো পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারেননি। একটি রূপকথা অনুযায়ী বনবাসে থাকাকালীন তিনি সমুদ্র কর্তৃক নিষিক্ত হয়ে দেবপাল নামক একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রসারিত করেন।
বারো শতকে সেনগণ ক্ষমতায় আসার পর ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ছিলেন রাজ দরবারের অপরিহার্য অঙ্গ। তাদের শাসনামলে ব্রাহ্মণদের নির্দেশাবলী কতটকুু পালন করা হতো তা জানা যায় না, তবে বলা যায় এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনগুণ বয়সী বরের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্ক কনের বিবাহ। কতিপয় নারী নিঃসন্দেহে উচ্চশ্রেণীর, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হলেও তাদের স্বেচ্ছায় চলাফেরার ক্ষমতা ছিল সীমিত। পরিবারে তাদের অবস্থান থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছাড়া নারীদের অন্য কোনো আইনগত অথবা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। এর ব্যতিক্রম ছিল বিধবাদের ক্ষেত্রে, অবশ্য কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে তাদের স্বামীদের সম্পত্তি ‘ভোগ’ করার অনুমতি দেওয়া হতো। এছাড়া তাদের নিজ ভরণপোষণের জন্য অতি অল্পসংখ্যক উপায় ছিল। রাজ অন্তঃপুরে নারীরা দৃষ্টির বাইরে নিভৃতে অবস্থান করলেও সাধারণভাবে নারীদের বেলায় এটা সত্যি ছিল না। কারণ তারা ঘোমটা দিয়ে চলত না। এটা বিশ্বাস করা হতো যে, বিধবারা অমঙ্গলসূচক এবং তাদের জন্য অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ ছিল। পতিদের চিতায় তাদের আত্মাহুতি দিতে উৎসাহিত করা হতো।
ব্রিটিশ শাসন জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে ‘নারী’ প্রশ্নটি ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে এবং প্রভাবশালী ব্রিটিশ লেখকগণ ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজকে নিকৃষ্ট বলে নিন্দা করে নারীদের প্রতি যে আচরণ করা হয় সে বিষয়টি উল্লেখ করেন।
সংস্কারকদের মধ্যে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল নারী শিক্ষা। বাংলায় মেয়েদের স্কুল প্রথম চালু করেন মিশনারিগণ। ১৮১৯ সালে ব্যাপ্টিস্ট মিশন ‘ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি’ গঠন করে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ‘সম্ভ্রান্ত’ হিন্দু বালিকাদের জন্য চার্চ মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক যে ৩০-টিরও অধিক স্কুল খোলা হয় তার দায়িত্ব নিতে ১৮২১ সালে মিস মেরী অ্যান কুক কলকাতায় আগমন করেন। ১৮২৪ সাল নাগাদ ঢাকায় একটি খ্রিস্টান মহিলা স্কুল শুরু করা হয়, কিন্তু ১৮২৬ সালে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫৪ সালে ব্রিটিশ সরকার অনুদানের মাধ্যমে নারীশিক্ষাকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করে।
১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজ থেকে বি.এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা স্নাতক হন। নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
মুসলিম মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। ১৯১১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ছিল বাংলায় মুসলিম নারীদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়।
সাহিত্য-সংস্কৃতি
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে নারীর ধারাবাহিক অবদান লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং স্বকীয়তার দিক দিয়ে তাদের রচনাবলি বিশিষ্ট। নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য এবং পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা নারীকে তার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছে। প্রথমদিকে সাহিত্যে বিদ্রোহের চেয়ে করুণ রসের আধিক্য লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীতে তা আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে পর্যবসিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, সরলাবালা সরকার, উমা দেবী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সুফিয়া কামাল স্বৈরাচার, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সমাজ, ভাষা ও সংস্কৃতির মূূূূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে লেখা সুফিয়া কামালের কবিতাগুলি পরবর্তীতে মোর যাদুদের সমাধি পরে নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের সময় তিনি মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য নারী সমাজকে আহ্বান করেন তার বেণীবিন্যাস সময় তো আর নেই কবিতায়। এছাড়া মৈত্রেয়ী দেবীর কবিতায় রয়েছে প্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে ভাবনার সুগভীর অনুসন্ধান। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যকর্মে রয়েছে ধর্মীয় বিধানের অপব্যবহারের কথা, সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গ, সে যুগের নারীদের মানসিক, শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক অবরুদ্ধতার কথা, সমাজের কুসংস্কার ও অবরোধ-প্রথার কুফল, নারীদের প্রতি সামাজিক অবমাননা, নারী অধিকার ও নারী জাগরণ সম্পর্কে এবং নারী শিক্ষার পক্ষে প্রাগ্রসর নিজস্ব অভিমত। সরসীবালা বসুর উপন্যাস ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও সারল্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।
সংগীতেও রয়েছে নারীর অবদান। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন এবং বাদ্রিদাস মুকুলের নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীতে তালিম নেন। সতী দেবী রবীন্দ্র সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গানের খ্যাতনামা শিল্পী। আলমোড়ায় উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান কালচার সেন্টারে তিনি গান শেখাতেন। তিনি বোম্বের পৃত্থী থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফিরোজা বেগম নজরুল সংগীত শিল্পী ও স্বরলিপিকার হিসেবে পরিচিত।
এছাড়াও চলচ্চিত্রে রয়েছে নারীর ব্যাপক পদচারণা। আনোয়ারার অর্ধশতাধিক ছবির মধ্যে নয়ন মনি, গোলাপী এখন ট্রেনে, নবাব সিরাজউদ-দৌলা উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। কবরী সারোয়ারের অভিনীত শতাধিক ছবির মধ্যে লালন ফকির, সুজন সখি, সারেং বউ উল্লেখযোগ্য।
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও বাচসাস পুরস্কার লাভ করেন। গেীতম ঘোষ পরিচালিত পদ্মা নদীর মাঝি ছবির উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রী চম্পা। ডলি ইব্রাহিম সূর্য দীঘল বাড়ি ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। অভিনেত্রী নূতন ১৯৮৩ সালে প্রাণ সজনী ছবিতে অভিনয়ের জন্য বাচসাস পুরস্কার এবং ১৯৮৭ সালে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত ছবিতে অভিনয়ের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ববিতা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে ১৯৭৭ সালে বসুন্ধরা পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে রামের সুমতি ছবিতে অভিনয়ের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। রওশন জামিল, রোজিনা, শাবানাও পুরস্কার লাভ করেন।
আন্তর্জাতিক নারী দিবস
আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয়। সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ হিসেবে এ দিবস উদযাপন করে থাকেন। তবে দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়ের্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকরা।
সেই মিছিলে চলে সরকারি বাহিনীর দমন-পীড়ন। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বছর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সমঅধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল। বাংলাদেশেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার লাভের পূর্ব থেকেই দিবসটি পালিত হতে শুরু করে।
১৯৭৫ সালের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় জাতিসংঘ। এরপর থেকে বিশ্বজুড়েই পালিত হচ্ছে দিনটি নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করার অভীপ্সা নিয়ে।
রাজপথ
বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থানের অগ্রগতি হয়েছে চারটি পৃথক স্তরে- নেতৃত্বের পর্যায়, কোটা পদ্ধতি, নির্বাচনী রাজনীতি এবং নারী আন্দোলন। দেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ধরন ও সুযোগ সম্পর্কে ১৯৭২ সালের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থসামজিক অবস্থার আলোকে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবিধানে জাতীয় সংসদকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে সংসদে মহিলা সদস্য নির্বাচিত করার বিধান রাখা হয়। আইনসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে বিতর্কও নতুন কিছু নয়। পাকিস্তানের গণপরিষদে এ সম্পর্কিত আলোচনা থেকেই এর সূত্রপাত, যেখানে মাত্র দুজন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। এ দুই মহিলা সদস্য ১৯৩৫ সালের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের ফ্র্যাঞ্চাইজ কমিটির কাছে আইনসভায় ১০ ভাগ মহিলা কোটা সংরক্ষণের দাবি জানান। কিন্তু সেখানে মাত্র তিন ভাগ কোটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ও পরিধি অনেকটা বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের দ্বৈত ভোটের অধিকার তথা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ নির্বাচনী এলাকায় ভোট প্রদান এবং সাধারণ নির্বাচনী এলাকায় ভোটাধিকারের সুযোগ দেওয়া হয়। আইন প্রণয়নের রাজনীতিতে মহিলাদের আগ্রহের সাক্ষ্য মেলে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে তিনজন মহিলার নির্বাচনের মধ্যে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমাবনতি এবং সামরিক আইন জারির প্রেক্ষিতে আইনসভায় গণতান্ত্রিকভাবে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ হ্রাস পায়।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র আইয়ুব শাসনামলে আইন প্রণয়নের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করে রাখা হয়। আইয়ুব খানের ১৯৬২ সালের সংবিধানে মহিলাদের পৃথক নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রদত্ত সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। মহিলাদের জন্য মাত্র সাতটি সংরক্ষিত আসন রাখা হয় এবং আইনসভার পুরুষ সদস্যদের ভোটে তাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। সংরক্ষিত মহিলা আসনে এভাবে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নারীদের তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষের মুখাপেক্ষী করা হয়। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের কয়েকদিন আগে সংরক্ষিত মহিলা আসন ১৫ থেকে বাড়িয়ে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ৩০-এ উন্নীত করা হয়। সংসদে মহিলা কোটা বিলুপ্ত করার বিষয়ে সংসদের ভেতর ও বাইরে মহিলা আসনসংখ্যা ও এর নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে তীব্র বিতর্ক এখনও অব্যাহত রয়েছে। নারী সংগঠনগুলি, বিশেষ করে ১৭টি সংগঠনের মিলিত সংস্থা ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ তাদের ১৭-দফা দাবিতে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণের দাবি পেশ করে। কিন্তু ১৯৯০ সালে এক সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচনযোগ্য ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ আরও ১০ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালের ৩ জুলাই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরই এদেশের ইতিহাসে প্রথম স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করার মর্যাদা লাভ করে।
মুক্তিযুদ্ধেও নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাতে মহিলাদের, বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মুক্তিযুদ্ধ সময়ে তাদের ভূমিকা আরও বিস্তারিত হয়। অনেক মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের অস্ত্রচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ ঘটে নানাভাবে। একদিকে যেমন তারামন (বীর প্রতীক), কাঁকন বিবি, রহিমা বেগমদের মত অনেকে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অপরদিকে সহযোদ্ধা হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করে ও মুক্তিযোদ্ধাদের আতিথ্য প্রদান ও তথ্য সরবরাহ করেও যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অগণিত মহিলা। অনেক মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ, বস্ত্র ও ওষুধপত্র সংগ্রহ করে তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছে।
সাংবাদিকতা
বাঙালি নারীদের সাংবাদিকতায় আগমন ঘটে সাময়িকী সম্পাদনার মাধ্যমে। প্রথম সাময়িকী পাক্ষিক বঙ্গমহিলা সম্পাদনা করেছিলেন একজন মহিলা। মোক্ষমদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালের ১৪ এপ্রিল। প্রথম মাসিক জেন্ডার ভিত্তিক ম্যাগাজিন অনাথিনী মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে। মহিলা কর্তৃক সম্পদিত প্রথম সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন বঙ্গবাসিনী প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। মুসলিম নারী বেগম সুফিয়া খাতুন কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম মাসিক ম্যাগাজিন অন্বেষা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সনের বৈশাখ মাসে। একজন মহিলা কর্তৃক সম্পাদিত পাপিয়া নামক ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। ম্যাগাজিনটি সম্পাদনা করেন বিভাবতী সেন। এ সচিত্র সাময়িকীটি শিশুদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়। বেগম শামসুন্নাহার এবং মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত বুলবুল প্রকাশিত হয় বছরে তিন সংখ্যা। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৬ সাল থেকে এটি মাসিক ম্যাগাজিনে রূপান্তরিত হয়। একজন মুসলমান মহিলা কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন বেগম প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই। নূরজাহান বেগম এবং সুফিয়া বেগম যৌথভাবে তা সম্পাদনা করেন। কিন্তু এর প্রকাশনার দ্বাদশ সংখ্যা থেকে নূরজাহান বেগম এককভাবে এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

নারীরা শুরুতে সংবাদপত্র সম্পাদনার কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করলেও ধীরে ধীরে সাংবাদিকতার অন্যান্য শাখায় তাদের পদচারণা ঘটে। পাকিস্তান আমলে বাংলার এ অঞ্চলে সাংবাদিকতায় নারীদের আগমন ঘটে খুব ধীরগতিতে। এ আমলে খুব বেশি নারী সাংবাদিকের নাম পাওয়া যায় না। সাংবাদিকতায় খ্যাতিমানদের মধ্যে লায়লা সামাদ, নূরজাহান বেগম, জাহানারা আরজু, মাফরুহা চৌধুরী, মাহফুজা খাতুন, হাসিনা আশরাফ, সেলিনা হোসেন, বেবী মওদুদ এবং তাহমিনা সাঈদের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর এই দৃশ্যপটে বেশ পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত নারী পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নিচ্ছেন এবং এদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
উন্নয়ন
এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় নারীর ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে। এক্ষেত্রে ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। নারীর ক্ষমতায়ন একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও সব ধরনের পেশায় যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হলেও তাদের স্থায়ী সামাজিক অনগ্রসরতা সরকারি প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে প্রবেশের সমান সুযোগ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ শতকের সত্তরের দশকের গোড়া থেকেই নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আইনের বিধান, নির্বাহী আদেশ, নীতি সংশোধন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীর সামাজিক পদমর্যাদা উন্নয়ন ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য গত তিন দশকে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসব পদক্ষেপ ও উপযুক্ত কর্মপন্থা জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত অনুরূপ পদক্ষেপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বাধীনতার পর সরকারি চাকরিতে নারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৪১৭ জন নারীকে ১৫টি ক্যাডারে নিয়োগ করা হয়েছে এবং অধিকাংশ নারীকে এ ক্যাডারগুলির মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডার এবং অধস্তন পর্যায়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারি চাকরির বিভিন্ন ক্যাডারে চাকরিজীবীর মাত্র ৪.৮৯ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে এসব নারী।
উদ্যোক্তা হিসেবে নারীদের অবদান অপরের জন্য বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উদ্যোক্তা হিসেবে নারীরা হস্তশিল্প ব্যবসাকে প্রাধান্য দেন বেশি। শহর ও গ্রামাঞ্চলে তাদের উপার্জনমূলক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে রয়েছে কাপড় সেলাই, নকশা, বাটিক, বুটিক, এমব্রয়ডারি ও খাদ্য বিক্রয়। শহরে কর্মজীবী হিসেবে নারীরা যুক্ত আছেন বিপণীকেন্দ্রে, অভ্যর্থনা ডেস্কে, বিজ্ঞাপনী সংস্থায়, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, আইন ব্যবসায়, স্বাস্থ্য বিভাগে, করপোরেটেড সেক্টরে, শিল্পকলা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওতে। তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নারীরা কৃষি বা অন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিম্ন মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। মজুরি বৈষম্য ছাড়াও নারীদের সাধারণত শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার সমস্যা রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে প্রবেশের সুযোগ থাকলেও নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের বিবেচনা করা হয় না।
এ বিভাগের অন্যান্য সংবাদ