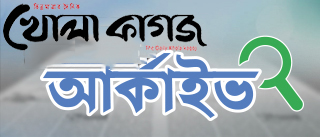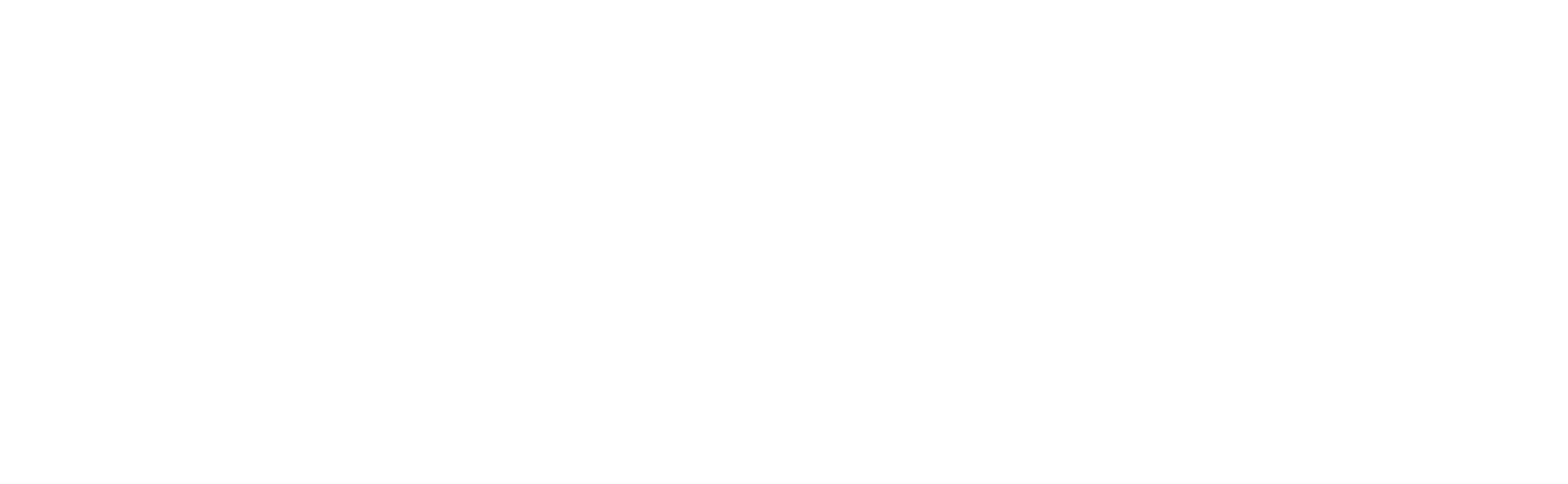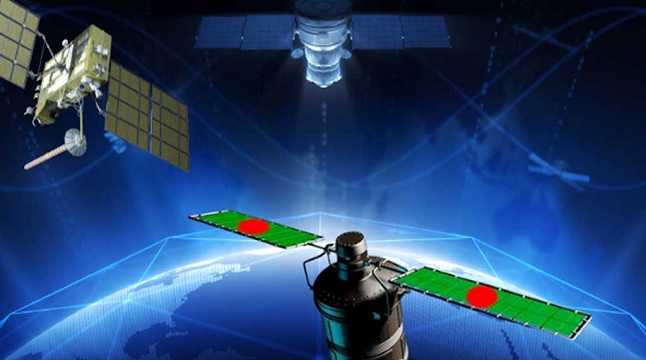বিলুপ্তপ্রায় হস্তশিল্প
সাইফ-উদ-দৌলা রুমী
🕐 ২:৪৯ অপরাহ্ণ, মার্চ ০৬, ২০২১

বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল পটভূমি গ্রাম। তবে প্রাত্যহিক যান্ত্রিকতা আর ব্যস্ততায় ভুলতে বসেছি আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য। বিদেশি পণ্যের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশীয় পণ্য। মসলিন, জামদানি, শীতল পাটি, নকশিকাঁথার দেশের মানুষ হয়েও হারাতে বসেছি সেসব ঐতিহ্য। বিলুপ্তপ্রায় বাঙালির হস্তশিল্প নিয়ে লিখেছেন সাইফ-উদ-দৌলা রুমী।
ঢাকাই মসলিন
বাংলা মসলিন শব্দটি এসেছে ‘মসুল’ থেকে। ইরাকের এক বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র হলো মসুল। এই মসুলেও অতি সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হতো। এই মসুল ও সূক্ষ্ম কাপড়-এ দুইয়ের যোগসূত্র মিলিয়ে ইংরেজরা অতিসূক্ষ্ম কাপড়ের নাম দেয় ‘মসলিন’। অবশ্য বাংলার ইতিহাসে ‘মসলিন’ বলতে বোঝানো হয় তৎকালীন ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের কাপড়কে। ফুটি কার্পাস নামক গাছের তুলা থেকে তৈরি করা হতো সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়।
মসলিনের তুলা ছিল অন্যান্য জাতের চেয়ে ভিন্ন। আর মসলিন কাপড় বোনার ক্ষেত্রে তুলা থেকে সুতা তৈরি ও সুতা দিয়ে কাপড় বোনা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক ছিল। ঠাণ্ডা ও শীতল আবহাওয়ার আর্দ্রতা মসলিনের সুতা কাাঁর জন্য বেশ উপযোগী। ফলে নাতিশীতোষ্ণ বাংলার এ আবহাওয়া মসলিন কাপড় বোনার জন্য বেশ উপযোগী ছিল।
মসলিনের পথ চলা শুরু হয়েছিল আজ থেকে ৪০০ বছর আগে থেকে। বঙ্গদেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশসহ ভারতের পশ্চিম বাংলার উৎপাদিত মসলিন সুদূর চীন, আমেরিকা, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, মিশর, ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ‘পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সি’ শীর্ষক গ্রন্থে মসলিন সম্পর্কে বিশেষ ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। রোমানরা মসলিনের খুব কদর করত। ইতিহাসে আছে, মোগল আমলে তৈরি করা ঢাকাই মসলিন ঘাসের ওপর রাখলে এবং তার ওপর শিশির পড়লে কাপড় দেখাই যেত না। কয়েক গজ মসলিন কাপড় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যেত বলে জনসাধারণ একে ‘হাওয়ার কাপড়’ বলত। এমনকি একটি আংটির ভেতর দিয়ে এক থান কাপড় অনায়াসে টেনে বের করা যেত। দেশলাইয়ের বাক্সেও এ সূক্ষ্ম মসলিন রাখা যেত।
বাংলার মসলিনশিল্প তার সোনালি সময়ে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি শিল্প গড়ে ওঠা, টিকে থাকা কিংবা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পেছনে কাজ করে অনেক ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক নিয়ামক। বাংলায় গড়ে ওঠা মসলিন শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। মোগলদের পরাজিত করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা বাংলা দখলের আগেই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের বিলেতি শাড়ির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হলো ঢাকার মসলিন। তাই তারা মসলিনকে চিরতরে দূর করে দিতে চাইল। প্রথমেই তারা মসলিন কাপড়ের ওপর অত্যধিক শুল্ক বা ট্যাক্স চাপিয়ে দিল। বিলেত থেকে আমদানি করা কাপড়ের ওপর শুল্ক ছিল দুই থেকে চার শতাংশ। কিন্তু মসলিনসহ দেশি কাপড়ের ওপর তারা ট্যাক্স বসাল ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ। তাই দেশে যেমন বিলিতি কাপড় সুলভ হলো, একই সঙ্গে ব্যয়বহুল হয়ে উঠল মসলিনসহ দেশি কাপড়। প্রতিযোগিতায় তাই মসলিন টিকতে পারছিল না। কিন্তু তারপরও টিকে ছিল মসলিন।
এবার ইংরেজ শাসকগণ নিষেধাজ্ঞা জারি করল মসলিন তৈরির ওপর। তাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেও চলল মসলিনের উৎপাদন। তখন ব্রিটিশরাজ চড়াও হলো মসলিনের কারিগরদের ওপর। তারা মসলিন কারিগরদের ধরে ধরে তাদের হাতের আঙ্গুল কেটে দেওয়া শুরু করল, যাতে গোপনে গোপনে তারা মসলিন তৈরি করতে কিংবা এর নির্মাণকৌশল অন্যদের শিক্ষা দিতে না পারে। আর এভাবেই একদিন বাঙালিরা হারিয়ে ফেলল তাদের গর্বের মসলিন তৈরির প্রযুক্তি জ্ঞান।
কুমিল্লার খাদি
কুমিল্লা খাদি কাপড় দেশ-বিদেশে বেশ জনপ্রিয়। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় এ কাপড়ের জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠে। ‘স্বদেশী পণ্য গ্রহণ কর আর বিদেশি পণ্য বর্জন কর’ স্লোগানের ওপর ভিত্তি করেই তৎকালীন সময়ে খাদিশিল্পের উৎপত্তি হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এ উপমহাদেশে হস্তচালিত তাঁতশিল্প ছিল জগদ্বিখ্যাত। দেশের চাহিদা মিটিয়ে সব সময় তাঁতের কাপড় বিদেশেও রপ্তানি হত। হাতে বোনা কাপড়কে উপমহাদেশের মানুষ জানে খাদি হিসেবে। খদ্দর শব্দটি গুজরাটি, খদ্দর থেকে খাদি। শব্দটির আভিধানিক অর্থ কার্পাস তুলা থেকে হাতে কাটা সুতা দিয়ে হাতে বোনা কাপড়। খাদে বা গর্তে বসে তৈরি, তাই এ কাপড়ের নাম দেওয়া হয় ‘খাদি’। জনপ্রিয় খাদি কাপড়ের সঙ্গে কয়েকটি দিক জড়িত রয়েছে। তা হচ্ছে তাঁতী, সুতা, কাটুনি, ব্লক কাটার ও রঙের কারিগর। সবাই মিলে তৈরি করেন নান্দনিক খাদি কাপড়।
প্রাচীনকাল থেকেই এ উপমহাদেশে কুমিল্লার তৈরি খাদি বা খদ্দর কাপড়ের চাহিদা ছিল প্রচুর। এ চাহিদাকে ধরে রাখার জন্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর তৎকালীন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা ড. আখতার হামিদ খান ও তৎকালীন গর্ভনর ফিরোজ খান নুনের সহযোগিতায় ‘দ্যা খাদি অ্যান্ড কটেজ ইন্ড্রাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। চান্দিনাতে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত একটি তাঁতশিল্প রয়েছে আজও।
কুমিল্লার খাদি শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও এটি মূলত কুটিরশিল্প। গ্রাম্য বধূরা গৃহস্থালির কাজের ফাঁকে ফাঁকে চরকায় সুতা কেটে তাঁতীদের কাছে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সুযোগ পেত। খাদির পোশাক যেমন দৃষ্টিনন্দন তেমনি পরতেও আরামদায়ক। কুমিল্লা জেলায় দেড় হাজার পরিবার এ পেশায় জড়িত। চান্দিনা, মুরাদনগর ও দেবিদ্বারে সহস্রাধিক তাঁতশিল্প রয়েছে। এসব অঞ্চলের তাঁতশিল্পীরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এ শিল্পটিকে ধরে রাখার জন্য। কিন্তু কারখানায় তৈরি করা কাপড়ের সঙ্গে টিকে থাকাটা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাছাড়া রয়েছে কাপড় তৈরিকরণ কাঁচামালের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।
ঢাকাই জামদানি
জামদানি হল কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র, যার বয়ন পদ্ধতি অনন্য। জামদানি বুননকালে তৃতীয় একটি সুতা দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। মসলিন বয়নে যেমন ন্যূনপক্ষে ৩০০ কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হয়, জামদানি বয়নে সাধারণত ৭০-৮০ কাউন্টের সূতা ব্যবহৃত হয়। জামদানি বিভিন্ন নানা স্থানে তৈরি করা হয় বটে কিন্তু ঢাকাকেই জামদানির আদি জন্মস্থান বলে গণ্য করা হয়। জামদানি বয়নের অতুলনীয় পদ্ধতি ইউনেস্কো কর্তৃক একটি অনন্যসাধারণ নির্বস্তুক সংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।
প্রাচীনকালের মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে জামদানি শাড়ি বাঙালী নারীদের অতি পরিচিত। মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হয়। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়িকেই বোঝানো হয়। তবে জামদানি দিয়ে নকশী ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা প্রভৃতিও তৈরি করা হত। ১৭০০ শতাব্দীতে জামদানি দিয়ে নকশাওয়ালা শেরওয়ানির প্রচলন ছিল। এছাড়া, মুঘল ও নেপালের আঞ্চলিক পোশাক রাঙ্গার জন্যও জামদানি কাপড় ব্যবহৃত হত।
জামদানির নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ রয়েছে। একটি মত অনুসারে ‘জামদানি’ শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে এসেছে। ফার্সি জামা অর্থ কাপড় এবং দানা অর্থ বুটি, সে অর্থে জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়। এ কারণে মনে করা হয় মুসলমানেরাই ভারত উপমহাদেশে জামদানির প্রচলন ও বিস্তার করেন। আরেকটি মতে, ফারসিতে জাম অর্থ এক ধরনের উৎকৃষ্ট মদ এবং দানি অর্থ পেয়ালা। জাম পরিবেশনকারী ইরানি সাকীর পরনের মসলিন থেকে জামদানি নামের উৎপত্তি ঘটেছে। নকশা অনুযায়ী জামদানির নানা নাম হয়ে থাকে। যেমন তেরছা, জলপাড়, পান্না হাজার, করোলা, দুবলাজাল, সাবুরগা, বলিহার, শাপলা ফুল, আঙ্গুরলতা, ময়ূরপ্যাচপাড়, বাঘনলি, কলমিলতা, চন্দ্রপাড়, ঝুমকা, বুটিদার, ঝালর, ময়ূরপাখা, পুইলতা, কল্কাপাড়, কচুপাতা, প্রজাপতি, জুঁইবুটি, হংসবলাকা, শবনম, ঝুমকা, জবাফুল ইত্যাদি।
জামদানির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়, আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টাব্দে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে, পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান গ্রন্থে এবং বিভিন্ন আরব, চীন ও ইতালির পর্যটক ও ব্যবসায়ীর বর্ণনাতে। কৌটিল্যের বইতে বঙ্গ ও পু-্র এলাকায় সূক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ আছে, যার মধ্যে ছিল ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসি।
১৭৪৭ সালের হিসাব অনুযায়ী দিল্লীর বাদশাহ, বাংলার নবাব ও জগৎ শেঠের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার জামদানি কেনা হয়। এছাড়া ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ প্রায় নয় লাখ টাকার মসলিন কেনে। তবে আঠারো শতাব্দীর শেষের দিকে মসলিন রপ্তানি অনেকাংশে হ্রাস পায়। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। এদের নিযুক্ত গোমস্তারা নিজেদের স্বার্থে তাঁতীদের উপর নির্যাতন শুরু করে। তাঁতীরা কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করতে রাজি না হলে তাদের মারধর করা হতো। অবশ্য তাঁতীদের উপর অত্যাচার ঠেকাতে কোম্পানি আইন প্রণয়ন করেছিল।
১৭৮৭ সালে জেমস ওয়াইজের মতে ৫০ লাখ এবং জেমস টেইলরের মতে ৩০ লাখ টাকার মসলিন ইংল্যান্ডে রপ্তানি করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮০৭ সালে এ পরিমাণ ৮.৫ লাখ টাকায় নেমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮১৭ সালে রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমেই কেবল ইউরোপে মসলিন পাওয়া যেত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জামদানি ও মসলিনের এক হিসাব থেকে দেখা যায়, সাদা জমিনে ফুল করা ৫০ হাজার টাকার জামদানি দিল্লী, লক্ষ্মৌ, নেপাল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এলাকার নবাবরা ব্যবহার করতেন। এ শিল্প সংকুচিত এবং পরে বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে কিছু কারণ ছিল, যার মধ্যে প্রধান কারণ ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব। এর ফলে বস্ত্রশিল্পে যন্ত্রের আগমন ঘটে এবং কম মূল্যে ছাপার কাপড় উৎপাদন শুরু হয়। এছাড়া দেশি সুতার চেয়ে তখন বিলেতি সুতার দাম কম ছিল। তৎকালীন মোঘল সম্রাট ও তাদের রাজ কর্মচারীরা এ শিল্পের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন। ফলে ধীরে ধীরে জামদানি শিল্প কালের গহ্বরে হারিয়ে যায়।
অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঢাকার ডেমরায় জামদানি পল্লীর তাঁতীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। তবে মেধা ও পারিশ্রমিকের অভাবের কারণে তাঁতীরা আর এ পেশায় আসতে চাইছেন না।
নকশিকাঁথা
নকশিকাঁথার নকশায় জড়িয়ে থাকে অনেক গল্প। এটি একান্তই নারীদের শিল্প। সাধারণত বর্ষাকালে ঘরবন্দি থাকার দীর্ঘ সময়ে নারীরা দল বেঁধে নকশিকাঁথা সেলাইয়ের কাজ করে থাকতেন। হাজারো গল্প তখন ধরা দিত কাঁথার জমিনে রংবেরঙের সুতার কারুকাজে।
‘নক্সী-কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।’
কবি জসীমউদ্?দীন এক অদ্ভুত মায়াময় আখ্যান রচনা করেছিলেন তার পাঠকদের জন্য। সাজু আর রূপাইয়ের বিচ্ছেদি প্রেমের গল্প হলেও সে কাহিনীর প্রধান চরিত্র ছিল নকশা তোলা নকশিকাঁথা। কাঁথা বুনতে বুনতে কত কথাই না সাজুর মনে হয়েছে, মনে পড়েছে কত স্মৃতি। লাল-নীল সুতায় সেসব কথাই কাঁথার জমিনে ফুটে উঠেছিল প্রেম আর বিরহ-বেদনার গল্প হয়ে। রঙিন সুতায় বোনা এ গল্পের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্বকালে বাংলায় কাঁথার উদ্ভব বলে ধারণা করেন গবেষকেরা। পাণিনির ব্যাকরণ কিংবা অন্যান্য পালি ও সংস্কৃত বইপত্রে, নাথসাহিত্যে, মৈমনসিংহ গীতিকায় কাঁথার উল্লেখ পাওয়া যায়। নকশিকাঁথা দুই রকম।
নকশিকাঁথা আর নকশা ছাড়া সাধারণ কাঁথা। যেসব কাঁথায় নকশা থাকে, সেগুলোই নকশিকাঁথা। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীরা সেলাই করে চলেছেন এ কাঁথা উষ্ণতা ও উপহারের জন্য। তবে যশোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল কাঁথার নকশা, সেলাইয়ের ফোঁড়ের কলাকৌশলের জন্য একেবারে স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে নিয়েছে নকশিকাঁথার ভুবনে। এসব অঞ্চলে নকশিকাঁথার রয়েছে নিজস্ব ঘরানা। তবে কালেরগর্ভে হারিয়ে যাওয়ার পথে গ্রামীণ এ লোকশিল্পটি।
মৃৎশিল্প
মাটির সোঁদা ঘ্রাণ টেনে নেয় মাটির মানুষকে। সেই কবে গত শতকের ষাট দশকে গেয়েছিলেন শিল্পী, ‘মাটিতে জন্ম নিলাম, মাটি তাই রক্তে মিশেছে, এ মাটির গান গেয়ে ভাই জীবন কেটেছে।’ মাটিকে শিল্পিত করে তোলার কাজে নিবেদিত যারা, তাদের রক্ত মাংস মজ্জায় সুন্দরের সুঘ্রাণে সৌন্দর্যের আবরণে নতুন সৃষ্টির ভুবন তৈরি হয়। মাটি হয়ে যায় তখন মৃৎশিল্প। সহস্র বছর ধরেই এ শিল্প চর্চিত হয়ে আসছে এ ভূ-ভারতে তথা উপমহাদেশে। বাংলাদেশের প্রায় সব প্রান্তে কুমারেরা বসবাস করে। মাটির পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল, সরা, বাসন, ঘরা, কলসি, বদনা, ঠিলা, ঘটির কদর ছিল সর্বত্র। প্রতিটি ঘরে ও সংসারে এসব নিত্য ব্যবহার্য হয়ে আসছিল হাজার বছর ধরে। মাটি খনন করে যে প্রতœতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার করা হচ্ছে, সেখানে মৃৎশিল্পের নানা পণ্যের দেখা মিলছে। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশের মানুষ মৃৎশিল্প নির্ভর জীবনযাপন করে আসছে। কুমার সম্প্রদায় এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। হাতের সুনিপুণ হাতের কারুকাজ ফুটে ওঠে মৃৎশিল্পে। শৈল্পিক হাতে তৈরি পণ্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করা হতো। হাট-বাজারে সারা বছরই বিক্রি চলত। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন ও চৈত্র- এই চার মাস মৃৎশিল্পের তৈরি পণ্যের চাহিদা একটু বেশি থাকে। বাকি আট মাস বেচা-বিক্রি তেমন হয় না। পহেলা বৈশাখসহ গ্রামীণ মেলায় কিছু বিক্রি-বাট্টা হয়। শখের বশে অনেকে ঘর সাজানোর জন্য কিনে থাকেন। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ শিল্পের বিশাল বাজার আবারও তৈরি হতে পারে।
আদিবাসী তাঁতশিল্প
আমাদের দেশের আদিবাসী সমাজ অনেক বেশি আত্মনির্ভরশীল। তারা নিজেদের বস্ত্র নিজেরা বুনে পরিধান করে শুধু তাই নয়, সেটা বিক্রিও করে। এতে আর্থিক সচ্ছলতা যেমন আসে তেমনই পরনির্ভরশীলতা কমে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরী মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে। তবে বর্তমানে পৃষ্ঠপোষকতা, রক্ষণাবেক্ষণ, দিকনির্দেশনা এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে আদিবাসীদের তাঁতশিল্প। পাহাড়ে বসবাস করা আদিবসীরা শিল্পটি কিছুটা ধরে রাখলেও সংকটে রয়েছে মণিপুরী তাঁতষিল্প। বুননশিল্পে দক্ষ অধিকাংশ মণিপুরী তাঁতী নিজেদের পেশা বদল করছেন। মণিপুরীদের হাতে তৈরি তাঁত শিল্পের সুনাম থাকলেও এখন অনেকেই সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং তাঁতশিল্পীদের কম পারিশ্রমিক দিয়ে ব্যবসায়ীরা লাভবান হওয়ায় শিল্পীরা এ পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তরুণরাও এ পেশায় না আসা অন্য একটি কারণ। কিন্তু মণিপুরী নারীদের প্রায় ৯০ শতাংশ জন্মসূত্রেই তাঁতশিল্পের সঙ্গে পরিচিত।
সিলেট বিভাগে বাস করে মণিপুরী সম্প্রদায়। ১৮০০ শতক থেকে এ এলাকায় মণিপুরীদের বাস। এ দেশে প্রায় দেড় লাখ মণিপুরী বসবাস করে। মণিপুরী নারীদের সুখ্যাতি রয়েছে হাতে বোনা তাঁতের কাপড়ের জন্য। মৌলভীবাজারে শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জের প্রায় ৬০টি গ্রাম বিখ্যাত মণিপুরী তাঁতশিল্পের জন্য। বাংলাদেশের প্রাচীন হস্তশিল্পগুলোর মধ্যে মণিপুরী হস্তশিল্প সুপ্রসিদ্ধ। মণিপুরী হস্তশিল্প অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তাঁতশিল্পের সঙ্গে মণিপুরীদের রয়েছে যুগযুগান্তরের সম্পর্ক। মণিপুরী সমাজে মেয়েদের তাঁতশিল্পের অভিজ্ঞতাকে বিয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব যোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়।
মণিপুরীদের বস্ত্র তৈরির তাঁতকল তিন প্রকার। যেমন কোমরে বাঁধা তাঁত, হ্যান্ডলুম তাঁত ও থোয়াং। এ তাঁতগুলো দিয়ে সাধারণত টেবিল ক্লথ, স্কার্ফ, লেডিস চাদর, শাড়ি, তোয়ালে, মাফলার, গামছা, মশারি, ইত্যাদি ছোট কাপড় তৈরি হয়। প্রধানত নিজেদের তৈরি পোশাক দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেই মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে তাঁতশিল্পে নির্মিত সামগ্রী বাঙালি সমাজে নন্দিত ও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে নকশা করা ১২ হাত মণিপুরী শাড়ি, নকশি ওড়না, মনোহারী ডিজাইনের শীতের চাদর বাঙালি মহিলাদের সৌখিন পরিধেয়।
তামা-কাঁসা শিল্প
পালবংশের রাজত্বকাল থেকে বাংলার যেসব শিল্প উৎকর্ষতায় পৌঁছেছে তাদের মধ্যে তামা-পিতল শিল্প অন্যতম। রাজা গৌড় গোবিন্দের শাসনামলে ভারতের কংশ বণিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে কাঁসা শিল্পের আবির্ভাব ঘটে। কংশ বণিকরাই এ শিল্পের স্রষ্টা। হিন্দুদের বিয়েশাদি এবং পূজা-পার্বণে কাঁসার ব্যবহারকে পূত-পবিত্র বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। একটা সময় ছিল যখন গ্রাম জুড়ে শোনা যেতো কামারের হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ। কামারের সৃষ্ট আওয়াজের ছন্দে সৃষ্টি হতো তামা-কাঁসা-পিতলে এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস।
একটা সময় তামা-পিতল থেকে গৃহস্থলীতে ব্যবহৃত তৈজস্ব উৎপাদন থেকে শুরু করে তৈরি হতো নিখুঁত নকশার সব ভাস্কর্য। চকচকে ধাতবে মোড়ানো নিখুঁত এসব শিল্প আমাদের দেশের অনেকের কাছে অপরিচিত থাকলেও এ শিল্পের দৌরাত্ম্য এখন বিশ্বজুড়ে। আমাদের দেশে এ শিল্পের চর্চা এখন খুব কম হলেও ধামরাই, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, নরসিংদি এসব জায়গাতে এখনও চলে তামা-কাঁসা-পিতলে শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এ শিল্পের সুনাম ছিল।
কাঁসা ও পিতলের অপূর্ব শিল্পকর্মের জন্য ব্রিটিশ সরকার কাঁসা শিল্পীদের মধ্য নামকরা অনেককেই প্রশংসা ও পদকে ভূষিত করেছিলেন। অথচ আজ উপযুক্ত সহায়তা এবং সমাদরের অভাবে এ শিল্প অন্ধকারে ধুকছে। এখন বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও সুন্নতে খাতনা কিংবা সে ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে কেউ পিতলের কলসী, কাঁসার জগ, গ্লাস ও চামচ উপহার দেয় না। এক সময় কাঁসা ও পিতলের তৈরি জিনিসপত্র বিয়েসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সেরা উপহার হিসেবে বিবেচিত হতো। এককালে কাঁসা শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও রমরমা অবস্থা থাকলেও বর্তমানে চলছে চরম দুর্দিন। নানা প্রতিকূলতার কারণে এ শিল্পে নিয়োজিত হাজার হাজার শ্রমিকের ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই অনিশ্চিত। এরই মধ্যে বহু শ্রমিক পেটের দায়ে অন্য পেশায় চলে গেছে। আবার অনেকে জীবিকার অন্বেষণে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে গেছে।
বর্তমানে ঢাকার জিনজিরা, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং বিক্রমপুরে কাঁসা শিল্প কোনোমতে টিকে আছে। এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা এখনও প্রাণ দিয়ে এ শিল্পকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। আধুনিকতার চরম উৎকর্ষে মনোরম চোখ ধাঁধানো আকর্ষণীয় স্টিলের সামগ্রী, মেলামাইন ও দেশ-বিদেশের নজর কাড়া কাচের রকমারি সামগ্রীর কারণে মান্ধাতার আমলের কাঁসা শিল্প চরমভাবে মার খাচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য সামগ্রীর তুলনায় কাঁসার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। এ কারণেও ক্রেতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।
এ বিভাগের অন্যান্য সংবাদ