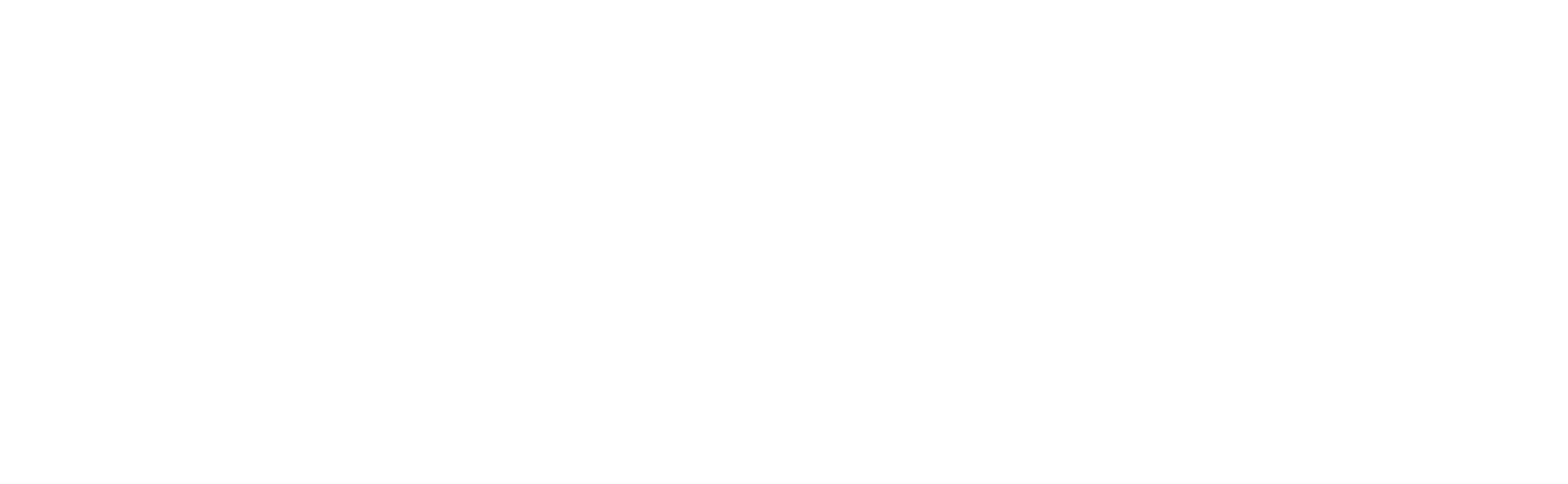শিক্ষাব্যবস্থার নিষ্ঠুর বলি শিশুরা
অরিত্র দাস
🕐 ৮:৫৫ অপরাহ্ণ, জানুয়ারি ১৪, ২০২০
ঠিকমতো হাঁটতে পারার আগে আমাদের শিশুদের স্কুলের আঙিনায় পাঠানো হয়। কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয় মস্তবড় ভারী ব্যাগ। অ আ ক খ লিখতে না পারলে দেখানো হয় ভয়-ভীতি। ‘ম’ যে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ সেটি না শিখিয়ে বলা হয়- মুখস্থ করো। অতঃপর মুখস্থ করার ক্ষমতা দিয়ে একজন শিশুর মেধা মূল্যায়ন করা হয়। বুদ্ধি-বিচক্ষণতা-সৃজনশীলতা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয় না।
যে যত বেশি মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী সে তত বেশি মেধাবী! আর এজন্য আমাদের শিশুরা বড় হয়ে আমলা হয়, কেরানি হয়। বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, লেখক, দার্শনিক, উদ্ভাবক হয় না।
মা-বাবারা গর্ব করে বলেন- ‘আমার সন্তান হাঁটতে শেখেনি কিন্তু দেখ, এটুকু বয়সে কত সুন্দর ছড়া মুখস্থ বলতে পারে’। এখানেই যেন অভিভাবকের সব কৃতিত্ব। আর তখনই শিশুর মেধা অর্ধেক পচে যায়। মুখস্থবিদ্যা মেধার বাহক নয়, ধারকও নয়। ‘আত্মস্থ’ শব্দটার সঙ্গে একজন শিক্ষার্থী পরিচিত হয় প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক স্তর পার করে যাওয়ার পর। আমি শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম কলেজে পড়ার সময়।
এক শিক্ষক পড়ানোর ফাঁকে এই দুর্লভ শব্দটা বলে ফেলেছিলেন। তখন জানতে পারলাম আত্মস্থের স্থায়িত্ব বেশি, মুখস্থের স্থায়িত্ব নেই। শব্দটার প্রতি সেই থেকে একটা দুর্বলতা। একটা আফসোস এখনও কাজ করে- শব্দটার সঙ্গে আগে পরিচিত হলাম না কেন। শব্দটার এত মহিমা, এত গুণ অথচ শব্দটা এতকাল অবদি অজ্ঞতার নিচে চাপা পড়েছিল। কেউ ঘুণাক্ষরেও শব্দটার কথা বলেনি। তাই একপ্রকার আক্ষেপের বশবর্তী হয়ে সেই থেকে শব্দটা সঙ্গে করে চলেছি। সুযোগ পেলে কাউকে না কাউকে সহসা বলে দেই, মুখস্থ নয় আত্মস্থ করো।
‘মুখস্থ নয় আত্মস্থ করো’ -এটা মূলনীতি হওয়া উচিত এদেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীর, শিক্ষাব্যবস্থার। যেমন সিঙ্গাপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মৌলিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ‘থিংকিং স্কুলস, লার্নিং নেশন’ নামে একটি নীতি অনুসরণ করছে। যাতে বাচ্চারা চিন্তার মাধ্যমে মেধার চর্চা করতে পারে।
অন্যদিকে এদেশে বাচ্চাদের বলা হয়, সারাদিন বই নিয়ে পড়ে থাকো, না পারলে মুখস্থ করো, না বুঝলেও মুখস্থ করো। ফলশ্রুতিতে এখানকার শিশুরা গণিতের মতো বিষয়ও মুখস্থ করে। কারণ, সামনে পরীক্ষা আসন্ন। পরীক্ষায় তো পাস করতে হবে। পেতে হবে জিপিএ-৫। অনেক চাপ মাথার ভেতর। আর তাই মুখস্থ ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই।
প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থীকে এতবেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় যে, সময় নিয়ে কোনো কিছু অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ আর অবশিষ্ট থাকে না। ফলে জানার আগ্রহ, শেখার আগ্রহ, বোঝার আগ্রহ, সৃষ্টির আগ্রহ মরে যায়। তখন তার মধ্যে একটাই আতঙ্ক কাজ করে- পরীক্ষা।
ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে দেখেছি- বাংলাদেশে তৃতীয় শ্রেণির অর্ধেকের বেশি শিশু বাংলা রিডিং পড়তে পারে না। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫ জন শিক্ষার্থী অঙ্ক করতে পারে না। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলার এবং ৬৮ শতাংশ গণিতের নির্ধারিত ধারণাগুলো অর্জন না করেই প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করে।
শিশুদের কথা ছেড়ে দিলাম, কিশোরদের কথা বলা যাক। কলেজ পড়ুয়া বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ক্রিয়া (টেনস) বুঝে না, বাক্য গঠন করতে পারে না, ইংরেজিতে দু’লাইন লিখতে পারে না। তারা ভালোভাবে না পারে বাংলা, না পারে ইংরেজি। না পারার কারণ- তারা পরীক্ষার উদ্দেশে পড়ে। জানার উদ্দেশ্যে পড়ে না। জানার উদ্দেশ্যে পড়লে পারত। যেমন গল্প উপন্যাস আমরা জানার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে পড়ি বলে, গল্পের কোথায় কী আছে, কে কোন সংলাপ দিয়েছে- তা সাধারণত ভুলি না।
পরীক্ষা এবং মুখস্থ একে অপরের পরিপূরক। ধ্বংসাত্মক, তথাপি মুখস্থ এবং তথাকথিত ঘন ঘন পরীক্ষা থেকে বের হতে পারেনি শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা। মুখস্থ নয় আত্মস্থ করো- এ কথাটি যেমন কোনো বিদ্যালয়ের দেয়ালে লেখা আমার চোখে পড়েনি। তেমনি পরীক্ষার উদ্দেশে নয়, জানার উদ্দেশ্যে পড়- এই কথাটিও কোনো বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেখিনি। দেখব কী করে? আমাদের বিদ্যালয়গুলো মানেই তো পরীক্ষালয়।
‘শাস’ নামক সংস্কৃত ধাতু থেকে বাংলা ‘শিক্ষা’ শব্দটি এসেছে। যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়- ‘শিক্ষা হলো তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না, বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।’ সেই বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক সিঁড়ি বা প্রথম ধাপ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। হাতেখড়িও বলা চলে। যার অপর নাম মৌলিক শিক্ষা।
মৌলিক শিক্ষা বলতে বোঝায় সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সবার জন্য সমান আবশ্যিক। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষার কথা বলেছে ইউনেস্কো। সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় জড়তা থাকবে কেন? জিপিএ-৫ পাওয়ার অন্যায় চাপ থাকবে কেন? অসুস্থ প্রতিযোগিতা, আতঙ্ক, ভয় ও আত্মহননের প্রবণতা থাকবে কেন? বৈষম্য থাকবে কেন? বৈষম্য তৈরি করে পরীক্ষা। ভালো শিক্ষার্থী এবং খারাপ শিক্ষার্থীর ট্যাগ লাগিয়ে দেয় ঘন ঘন পরীক্ষা পদ্ধতি। এই হতাশা একজন শিক্ষার্থীকে ভেতরে ভেতরে শেষ করে। আর এটি যদি হয় প্রাথমিক শিক্ষা জীবন থেকে তবে তো এখানেই সে পঙ্গু। বাকি পথ হাঁটবে কীভাবে? কোনো কোনো শিক্ষার্থীর এই হতাশা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যায়। অধিকাংশ শিক্ষার্থী কাটিয়ে উঠতে পারে না।
মৌলিক শিক্ষার কড়াঘাতে শিশুরা আত্মহত্যা করছে। এ বছর প্রাথমিক সমাপনী এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেটের বিষাক্ত ফলাফলের ছোবলে অনেক শিশু আত্মহত্যা করেছে। শিশুরা আত্মহত্যা করেছে- এই কথাটাই আমি বিশ্বাসের সহিত মেনে নিতে পারি না। তারপরও স্বীকার করতে হয়, হ্যাঁ শিশুরা আত্মহত্যা করেছে এবং তা করেছে কেবল মৌলিক শিক্ষাগ্রহণ করতে গিয়ে। পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী বুঝে উঠতে পারে না জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। কিন্তু সে বুঝে ফেলেছে আত্মহত্যার পথ। এর চেয়ে দুঃখজনক ও অবিশ্বাস্য ঘটনা আর কী হতে পারে এ জগতে?
অ্যারিস্টটল বলেছেন, ‘সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হলো শিক্ষা।’ কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুদের মন অসুস্থ করে তুলছে। কোমলমতি শিশুগুলোকে পরীক্ষা নামক বর্বরতার চাকায় পিষ্টে শিশু শিক্ষা পদ্ধতির ধ্বজা উড়িয়ে বেড়ায় যারা, তারা রীতিমতো সন্ত্রাসী। শিক্ষার্থী আত্মহত্যার প্ররোচনায় তাদের প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে। শিশুদের তো এ বয়সে আত্মহত্যা করার কথা ছিল না, তারা জানে না আত্মহত্যার ইতিবৃত্ত। তবে আত্মহত্যা করল কেন? এই প্রশ্নটি শিক্ষা সংস্কারক তথা সরকারের প্রতি আমি রাখতে চাই। আমি চাই আমার এ প্রশ্নের উত্তর কোনো শিক্ষা সংস্কারক বা সরকারপন্থি শিক্ষাবিদেরা পত্রিকার পাতায় লেখার মাধ্যমে দেবেন।
শিক্ষা অর্জনের পথগুলো হবে জলের মতো স্বচ্ছ এবং মসৃণ। জীবনের প্রথম জ্ঞান অর্জনে ভয় নয়, উৎসাহের সঙ্গে জানা অনিবার্য। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা। প্রতিযোগিতা জয়ী হতে সহায়তা করে বটে কিন্তু জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে না। কেননা প্রতিযোগিতা পরীক্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরদিকে জ্ঞানের শাখা-প্রশাখাকে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে সামীবদ্ধ করে রাখা যায় না।
গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, সৃষ্টিশীলতার পথ রুদ্ধ করা এবং প্রতীভা ক্ষয়ের অন্যতম কারণ এ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিহিংসাপরায়ণতা তৈরি করে, প্রকৃতপক্ষে যথার্থ সদাশয় মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক শিক্ষা থেকে সরিয়ে নিয়ে করে ফেলেছে জিপিএ-৫ পাওয়ার একটা অন্তসারশূন্য প্রতিযোগিতা। জিপিএ-৫-এর উন্মাদনা আমাদের শিশুদের শিক্ষাজীবনকে নিরানন্দময় তো করছেই, সঙ্গে বিষিয়ে দিচ্ছে। জিপিএ-৫ ও ঘন ঘন পরীক্ষার উদ্বেগে শিশুরা খেলাধুলা করতে পারছে না। বন্ধুদের সঙ্গে মিশে দুষ্টুমি করতে পারছে না।
পড়াশোনার বাইরের পৃথিবীটাকে তারা অবলোকন করতে পারছে না। ফলে তাদের শৈশব বলতে কিছু থাকছে না। কিন্তু হওয়ার কথা ছিল উল্টো। আতঙ্ক নয়, আনন্দ থাকা বাঞ্ছনীয় ক্লাস রুমে। জোর জবরদস্তি নয়, খেলা করো ছড়া ও কবিতা নিয়ে। ক্লাস রুমে স্তব্ধ হয়ে বসে না থেকে বরং স্কুলের মাঠে ছুটে বেড়াও। দাবা খেলো, ফুটবল খেলো, গোল্লাছুট খেলো, সাঁতার কাটো, তবলা বাজাও, নাচও, গাও- যা মন চায় চিৎকার করে সবাইকে জানাও। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ বলতে এসবই বোঝায়। যা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় না। নেদারল্যান্ডসের শিশুদের শিক্ষার জগত খেলাধুলার মতো আনন্দময়, সাবলীল।
এখানে মাধ্যমিক পর্যায়ের আগে কোনো শিশুকে বাড়ির কাজ এবং পড়াশোনার চাপ দেওয়া হয় না। ফিনল্যান্ডের প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিও একই, কোনো শিশুকে বাড়ির কাজ দেওয়া হয় না। এ ছাড়া সাত বছরের পূর্বে কোনো শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে পাঠানো যায় না এবং কিশোর বয়সের আগে তাদের কোনো ধরনের পরীক্ষা নেই। অন্যদিকে জাপানের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বলতে আগে নীতি-নৈতিকতা, পরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।
প্রাথমিক শিক্ষার ছয় বছর জাপানিরা শিশুদের শেখায় নম্রতা, ভদ্রতা ও নীতি-নৈতিকতা। এছাড়া দেশটির শিক্ষাব্যবস্থায় ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের কোনো পরীক্ষা নেই। বৃটেনের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা দিতে হয় না। এমনকি ‘মুখস্থবিদ্যা’ নামক শব্দটির সম্পর্কে বৃটেনের বাচ্চাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় সে চিত্র আলাদা।
শিক্ষা-দীক্ষায় সবচেয়ে উন্নত নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়াসহ ৮৭টির অধিক দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ছয় বছর। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। অর্থাৎ পাঁচ বছর। তার মানে দাঁড়াল, উন্নত দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এদেশের শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক ফারাক।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শিক্ষা’র সংজ্ঞার সঙ্গে এদেশের শিক্ষার কোনো মিল নেই। সরকারের যারা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবেন বা নীতিমালা প্রণয়ন করেন, তারা বাংলাদেশের শিশু, শিক্ষার্থী, পরিবেশ এবং শিক্ষা নিয়ে দো-টানার মধ্যে আছেন বলে একটা সংশয় সাধারণ মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। কেননা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে পুনঃপুনঃ পরিবর্তনশীলতা ভিত্তিহীন। বস্তুত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম দেখে মনে হয়, কর্তা-ব্যক্তিরা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। তারা আসলে কী সিদ্ধান্ত নিলে বা কোন উপায় অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীদের ভালো হবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।
আবার এমনও হতে পারে, তারা যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে। তাই সেই দায়বদ্ধতা থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা না রাখলে, শিক্ষাব্যবস্থা বারংবার সংস্কার না করলে তাদের অস্তিত্ব এবং পেশা দুটোই হয়তো সংকটে পড়ে যাবে। এই ‘ভয়ে’ হয়তো তারা শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙেচুরে একের পর অর্থহীন শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করে যাচ্ছেন।
সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ‘পাবলিক পরীক্ষা ছাড়া সমাপনী পরীক্ষাগুলোতে পুরো গ্রেডিং সিস্টেম তুলে দিয়ে কীভাবে মূল্যায়ন করতে পারি, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি।’ এ থেকে স্পষ্ট যে, হয়তো আগামীতে সমাপনী থাকবে না, তবে পরীক্ষা থাকবে। পরীক্ষা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি নেই।
তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়, যে শিক্ষা পদ্ধতির স্থায়িত্ব নেই, ভিত্তি নেই। এক সময় বাধ্য হয়ে তুলে দিতেই হয়। দুর্বল সৃজনশীল পদ্ধতিও একসময় তুলে দিতে হবে। তাহলে এমন শিক্ষানীতির প্রয়োগ করার দরকার ছিল কী? মোট কথা, আমাদের সরকারের শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান ও দূরদর্শিতা দুটোই অত্যন্ত কম। তারা তাদের প্রণীত শিক্ষা পদ্ধতির ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে অবগত নয়।
যার কারণে উপেক্ষিত হচ্ছে ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে গৃহীত সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০’। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা হবে এবং এসএসসি পরীক্ষা তুলে নেওয়া হবে। সেখানে সমাপনী (পিইসি) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেটের (জেডিসি) কথা উল্লেখ নেই।
এর আগে স্বাধীন বাংলাদেশে আরও ছয়টি কমিশন বা কমিটি রিপোর্ট ঘোষিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন (১৯৭২) প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বাড়িয়ে আট বছর করার সুপারিশ (১৯৭৪) করে। পরবর্তীতে প্রায় সব শিক্ষা কমিশনই প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ আট বছরে উন্নীত করার সুপারিশ বহাল রাখে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন হয়নি কখনও।
সরকার যতগুলো শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করেছে তার সব যে খারাপ তা বলব না। অনেক কিছু অবশ্যই ভালো। ধীরে ধীরে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকার জাতীয়করণ করছে। যেমন বার্বাডোজ নামক দেশটির বেশিরভাগ স্কুলই সরকারি। সরকারের বিপুল বিনিয়োগের কারণে সেদেশে সাক্ষরতার হার প্রায় ৯৮ শতাংশ। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের কাজটি শুরু করেন।
পরবর্তীতে তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাকি বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করার কাজ শুরু করেন। সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি, শ্রেণিকক্ষে লৈঙ্গিক সমতা প্রতিষ্ঠা, বিনামূল্যে বই বিতরণ, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচির মতো সরকারি-বেসরকারি নানা দীপ্তময় উদ্যোগ। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্কুলের ছাত্রীদের সাইকেল সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এডুকেশন-৯ ফোরামভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।
এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ বিশে^র অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে এগুলো সংবিধানের মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি। যে সফলতাগুলো নিয়ে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল সেসব প্রাথমিক শিক্ষার শরীরি উন্নয়ন অর্থাৎ বাহ্যিক উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার ভেতরকার গুণগত উন্নয়ন নয়। নয় শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন। প্রাথমিক শিক্ষার শরীরি উন্নয়ন হয়েছে, এখন প্রাথমিক শিক্ষার মনের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আর তা ঘটাতে হলে ঘন ঘন পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দিতে হবে। কারণ, শিশুশিক্ষা উন্নয়ন ও মেধা বিকাশে প্রধান অন্তরায় প্রত্যেক শ্রেণিতে একাধিক পরীক্ষাসহ পঞ্চম শ্রেণি এবং অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা। সার্টিফিকেট ব্যতীত এ পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে না। বরং একজন শিশু শিক্ষার্থীকে জীবনের সরল রেখাপথে হাঁটতে শুরুতেই বাধা সৃষ্টি করে। তার কোমল স্বপ্নালু জীবনকে আঘাত করে। অতএব, আমরা সার্টিফিকেট চাই, না-কি শিশুর মেধার উৎকর্ষ চাই- এটা একটা প্রশ্ন। আরও একটি প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা পাসের হার চাই, নাকি গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা চাই?
এত এত পরীক্ষা, এত ভীষণ প্রতিযোগিতা ও মুখস্থবিদ্যা দিয়ে যখন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এদেশে একজন বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার, বিজ্ঞানী, দার্শনিক তৈরি করা গেল না তখন শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা বিপ্লব দরকার। পরীক্ষার চেয়ে জানার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, উদ্ভাবনের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। বাড়ির কাজের চেয়ে শিশুর মানসিক বিকাশে ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনে জোর দিতে হবে। পরীক্ষা মেধা মূল্যায়নের চেয়ে হতাশা তৈরি করে বেশি। প্রতিটি স্তরে মানুষের চিন্তায়, ফলাফলে, যোগ্যতা ও দক্ষতায়, চলা-ফেরার, কথা-বার্তায়, আকাক্সক্ষায় পরিবর্তন আসে।
সেই পরিবর্তনকে মসৃণ করতে পারে ঘন ঘন পরীক্ষা পদ্ধতির বাতিলকরণ এবং প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা। নয়তো সমাপনী পরীক্ষায় ব্যর্থ একজন শিক্ষার্থী জুনিয়ার সার্টিফিকেট পরীক্ষার সময় পূর্বের কৃত ফলাফলের কারণের হতাশায় ভুগবে। ফলে তার ভালো করার ইচ্ছাশক্তিটা হারিয়ে যাবে। আবার জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার আশানুরূপ ফলাফল করতে না পারা একজন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় ভালো করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলবে। তাই হতাশা সৃষ্টিকারী ঘন ঘন পাবলিক পরীক্ষা রদ করতেই হবে। কেননা ঘুণে পোকা যেমন কাঠের শরীরে বাসা বেঁধে কাঠটিকে আস্তে আস্তে শেষ করে দেয়।
তেমনি হতাশা একজন শিক্ষার্থীকে তিলে তিলে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয় অভিভাবকদের। শিক্ষা মানে শেখা। সে শেখায় যখন জোরজবরদস্তি, পাস-ফেল, ভয়-আতঙ্ক, আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে তখন শিক্ষায় আর শেখার প্রবণতা থাকে না। বস্তুত মুখস্থবিদ্যা, প্রতিযোগিতা, পরীক্ষা- নিছক কোনো শব্দ নয়, মেধা ধ্বংসের তিন আগ্নেয় অস্ত্র।
অরিত্র দাস : শিক্ষার্থী, আইন ও বিচার বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
[email protected]
এ বিভাগের অন্যান্য সংবাদ