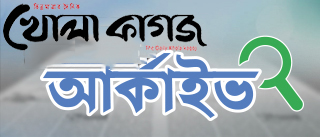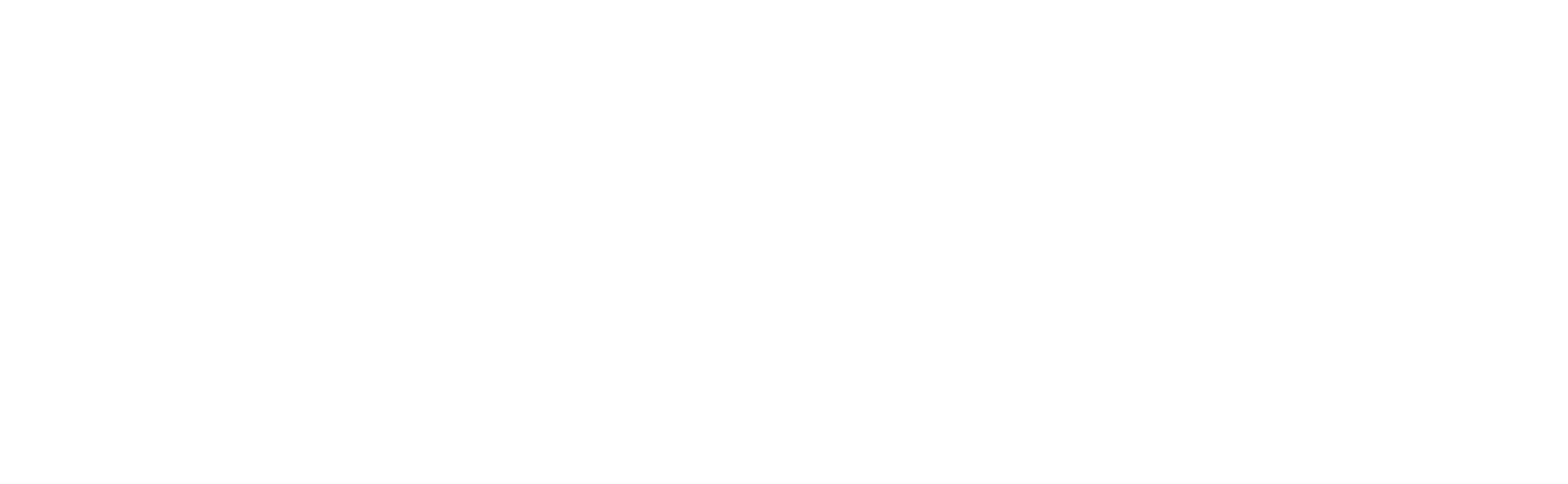ওয়েবের ছবি বিশ্লেষণ
শায়েখ আরেফিন
🕐 ৭:১৬ অপরাহ্ণ, জুলাই ১৫, ২০২২

জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিনিয়তই এগিয়ে চলে ও নতুন তথ্য আমাদের জানায়; তন্মধ্যে কিছু ঘটনা হয়ে ওঠে যুগান্তকারী। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই চাঁদে পদার্পণের দিনটি যেমন, তেমনি ৫৩ বছর পর এই জুলাইয়ের ১২ তারিখে জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন ভোরের সূচনা হলো।
জেমস ওয়েবের ছবি প্রকাশের দিনক্ষণ নাসা বেশ আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল। আগ্রহ-উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষায় ছিল মানুষ। ক্ষণগণনা শেষে নাসার বিজ্ঞানী মিশেল থ্যালের এলেন উপস্থাপনায়। তিনি স্বাগত জানালেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে ভিড়-করা মানুষদেরÑ আমেরিকার বিভিন্ন শহর, কানাডা, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, ইসরায়েল ইত্যাদি দেশের একাধিক শহর, ভারতেরও ভোপাল, বেঙ্গালুরুর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের মিলনায়তনে অপেক্ষারত মানুষদের স্বাগত জানালেন। তারপর শুরু হলো ছবি প্রকাশ ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে স্বল্প বিশ্লেষণ।
চারটি রঙিন ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। একটি ছবি অবশ্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কয়েকঘন্টা আগে উন্মুক্ত করার পরই সামনে চলে এসেছিল। ছবিগুলো সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তা থেকে সংক্ষেপে কিছু তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো।
এসএমএসিএস ০৭২৩ : এটি একটি বিশাল গ্যালাক্সিপুঞ্জের ছবি। এই গ্যালাক্সিপুঞ্জের ভর এতটাই বেশি যে আলো এখানে সরল পথে চলতে পারে না, চলে বাঁকা পথে এবং আলোর দীপ্তিও বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের ভাষায় এটি হচ্ছে gravitational lens. এ বিষয়ে আইনস্টাইনের কথা আলোচক উল্লেখ করেন (আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত সবাই জানতো এবং মানতো যে আলো চলে সোজা পথে। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন ভারি বস্তুর পাশ দিয়ে যাবার সময় আলো বেঁকে যায়। অর্থাৎ ভারি বস্তুর মহাকর্ষ বল আলোকে বাঁকিয়ে দেয়)। এই আলো পৃথিবীতে আসতে পেরিয়ে গেছে ১৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষেরও বেশি সময়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাপ্ত এটিই গভীরতম মহাবিশ্বের ছবি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন আরও গভীরের ছবি তোলা সম্ভব যেটি হবে বিগব্যাঙের কাছাকাছি সময়ের।
সাউদার্ন রিং নেবুলা : এটি আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ভেতরেই অবস্থিত, পৃথিবী থেকে ২০০০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। এর ব্যাস অর্ধ-আলোকবর্ষবিস্তৃত। এটি একটি গ্যাস ও ধূলার পিণ্ড যা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। এর কেন্দ্রে রয়েছে মৃতপ্রায় একটা নক্ষত্র। হাবল টেলিস্কোপও এই নেবুলার ছবি তুলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু জেমস ওয়েবের ছবি অনেক বেশি উজ্জ্বল ও গবেষণা-উপযোগী। এ ছবি বিশ্লেষণ ক'রে জানা যাবে কীভাবে নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটে।
স্টেফানস কুইন্টেট : পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্হিত এই স্টেফানস কুইন্টেট। এটি পাঁচটি গ্যালাক্সির সমন্বয়ে গঠিত একটি ক্লাস্টার বা গ্যালাক্সিপুঞ্জ। হাবল টেলিস্কোপও এর ছবি পাঠিয়েছে। ছবিটি নিতে হাবলের লেগেছিল কয়েক সপ্তাহ এবং তাতে অনেক তারকার অস্তিত্ব ছিল না। আর ওয়েবের লেগেছে ১২ ঘন্টার কিছু বেশি সময়। দুটো টেলিস্কোপের তোলা ছবির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য গবেষণা করলে তা নতুন দিগন্ত খুলে দিবে ব'লে ধারণা বিজ্ঞানীদের।
ক্যারিনা নেবুলা : মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে পৃথিবী থেকে ৭৬০০ আলোকবর্ষ দূরে আকাশের অন্যতম বৃহৎ ও উজ্জ্বল নীহারিকা এটি। মনে রাখা দরকার নীহারিকা হচ্ছে নক্ষত্রের সূতিকাগার। নীহারিকা মূলত বিশাল গ্যাস ও ধূলার পিণ্ড যেখান থেকে জন্ম হয় নক্ষত্রের। হাবল টেলিস্কোপও ক্যারিনা নেবুলার ছবি পাঠিয়েছে। নক্ষত্রের জন্ম প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করা জেমস ওয়েবের প্রধান চারটি কাজের একটি। ক্যারিনা নেবুলার ছবিটি এ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য চমৎকার হবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।
বৈজ্ঞানিক কল্পকথার অন্যতম আকর্ষণ টাইম ট্র্যাভেল বা সময় যাত্রা। তত্ত্ব অনুযায়ী সময় যাত্রা করে সময়কে স্তব্ধ/ধীর করে দেওয়া সম্ভব, অতীত দেখা সম্ভব। পৃথিবীর সাপেক্ষে সময় যাত্রা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি এখনো। কিন্তু কোটি কোটি বছর আগের যেসব ছবি নিয়ে আলোচনা হলো সেগুলোর সাপেক্ষে মানুষের এ একপ্রকার সময় যাত্রাই!
যে-ছবি আজ আমরা পাচ্ছি তা কোটি বছর আগের রূপ। ১৩০০ কোটি বছর আগের ছবির নক্ষত্রটি আজ হয়তো সেভাবে নেই, ইতোমধ্যে মৃত্যু ঘটে গেছে। আরও রোমাঞ্চকর যে আমরা এমন এক অতীত দেখছি যখন পৃথিবীরও জন্ম হয়নি (পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বছর)। তাই বলা যায়, ওই নক্ষত্রের সাপেক্ষে আমরা সময় যাত্রা করছি। তেমনি আজ যদি সাড়েছয় কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে থেকে কেউ পৃথিবী দেখে, দেখবে পৃথিবীতে ডাইনোসরের চলাফেরা। কাজেই জেমস ওয়েব এক ধরনের সময় যাত্রাও কিন্তু উপহার দিচ্ছে আমাদের!
মনে রাখা দরকার, আলোচিত ছবিগুলো ওয়েবের উদ্বোধনী ছবি, বিস্ময়ের শুরু কেবল! জেমস ওয়েব নিজেও একটি বিস্ময়। এটিকে বলা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে জটিল যন্ত্র। যন্ত্রটি আরও কতই না বিস্ময় উপহার দেবে মানবজাতিকে!
লেখক : শায়েখ আরেফিন, বিশ্লেষক ও সমালোচক
এ বিভাগের অন্যান্য সংবাদ