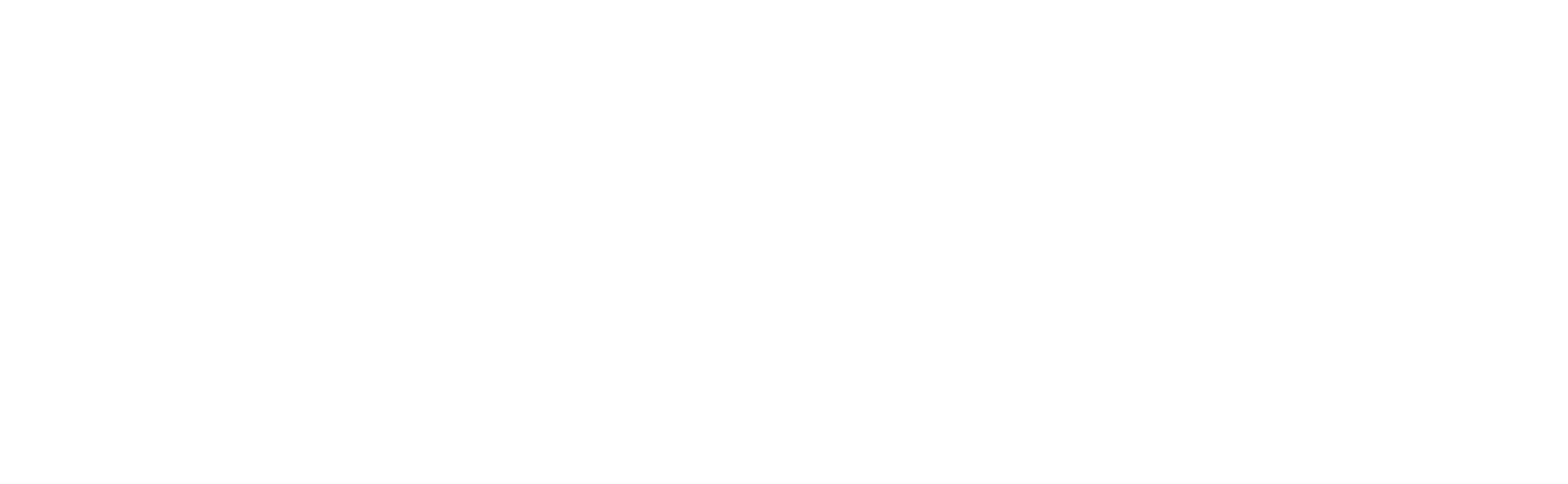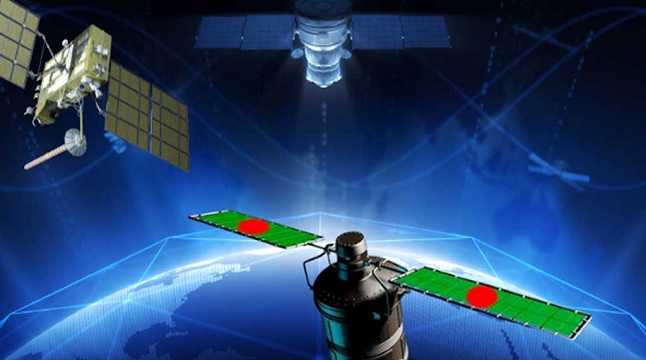ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস ঐতিহ্য
সাইফ-উদ-দৌলা রুমী
🕐 ১০:৪৮ পূর্বাহ্ণ, আগস্ট ১০, ২০২০
বাংলার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যে রয়েছে জাতিগত আচারের মিশেল। বাঙালির পাশাপাশি সমাবেশ ঘটেছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর। বাংলাদেশে বসবাস করা উপজাতিদের নিয়ে আজকের আয়োজন। সম্পাদনা করেছেন সাইফ-উদ-দৌলা রুমী
বিশ্ব আদিবাসী দিবস
আদিবাসীদের অধিকার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সুরক্ষা প্রদানের স্বার্থে প্রতি বছর ৯ আগস্ট পালিত হয় আন্তর্জাতিক দিবস। ১৯৯৪ সাল থেকে দিবসটি পালন করে আসছে বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি আদিবাসী। মানবাধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য।
১৯৯২ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ উপ-কমিশনের কর্মকর্তারা তাদের প্রথম সভায় আদিবাসী দিবস পালনের জন্য ৯ আগস্টকে বেছে নেন।
জাতিসংঘের তথ্যমতে, বিশ্বের ৭০টি দেশে ৩০ কোটি আদিবাসী বাস করে, যাদের অধিকাংশই অধিকার বঞ্চিত। অনেক দেশে আদিবাসীরা স্বীকৃতিই পায়নি। কোনো দেশে উপজাতি, কোনো দেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা হয় তাদের। ১৯৯৩ সালকে জাতিসংঘ প্রথম বার দআদিবাসী বর্ষদ ঘোষণা করে। পরের বছর ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতি বছর ৯ আগস্টকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া জাতিসংঘ ১৯৯৫-২০০৪ এবং ২০০৫-২০১৪ সালকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আদিবাসী দশক ঘোষণা করে।
সাঁওতালদের বাহা উৎসব
সাঁওতালদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব হলো বাহা উৎসব বা বাহা পরব। বাহা অর্থ ফুল। তাই বাংলায় বাহা পরবকে ফুল উৎসবও বলা হয়। মূলত নববর্ষ হিসেবে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এ উৎসব পালন করে সমতলে বসবাসকারী আদিবাসী সাঁওতালরা। উত্তরাঞ্চলে সমতলে বসবাসকারী আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে উড়াও, মুন্ডা, মালো, মাহাতো, মালপাহাড়ী, রাজওয়ারসীসহ ৩৮টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এ বাহা উৎসব পালন করে থাকে। বাহা পরবের মূল কথা হচ্ছে এই পরব না করা পর্যন্ত সাঁওতাল মেয়েরা সারজম বাহা (শাল ফুল), ইচাক বাহা, মুরুপ বাহা এগুলো খোঁপায় দিতে পারে না। এই পরবের মধ্য দিয়েই নতুন বছরের ফুল, ফল, পাতাকে সাঁওতাল আদিবাসীরা ব্যবহার করতে শুরু করে। গ্রামের মানঝি (গ্রাম প্রধান) পরবের দিন ঠিক করে। দুই-তিন দিনব্যাপী চলতে থাকে পরব। বাহা পরবের জন্য নির্দিষ্ট একটি পূজার স্থান থাকে। একে সাঁওতালরা জাহের থান বলে। বাহা পরবের প্রথম দিনকে বলা হয় উম আর দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় বাহা সারদী। প্রকৃতিকে ভালোবেসে সাঁওতাল আদিবাসীরা বাহা উৎসব পালন করে।
তাদের ধারণা বাহা উৎসবের পুজা পার্বন করলে তাদের সমাজ ও পরিবারের উন্নয়ন হবে। বাহা পুজা না করা পর্যন্ত সাঁওতাল নারীরা বাহা ফুল অর্থাৎ শাল ফুল ছিড়েও না মাথায় পরেও না। বছরের শুরুতে নতুন ফুল ফুটে বা যেই এলাকায় যেই ফুল পাওয়া যায় সেই ফুল দিয়েই এ বাহা উৎসব পালন করা হয়।
সাঁওতাল বিদ্রোহ
১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ১০ হাজার সাঁওতাল কৃষকের জমায়েত হয়েছিল ভারতের দামিন-ই-কোহ এলাকায়। তাদের দাবি ছিল, ‘জমি চাই, মুক্তি চাই’। যা থেকে শুরু হয় বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ এক সময় হয়ে উঠেছিল সব সম্প্রদায়ের মানুষের মুক্তিযুদ্ধ। ইতিহাসে যেটাকে বলে সাঁওতাল বিদ্রোহ।
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের এ দেশীয় দালাল সামন্ত-জমিদার, সুদখোর ও তাদের লাঠিয়াল বাহিনী, দারোগা-পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতাল নেতা সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব- এ চার ভাইয়ের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়ায় সাঁওতালরা।
ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত আইন ও বিধিবিধান, খাজনা প্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথম দিকে সাঁওতালরা তাদের আদি বাসভূমি কটক, ধলভূম, মানভূম, বড়ভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ও বীরভূমের পার্বত্য এলাকা ছেড়ে রাজমহল পাহাড়ের সমতলভূমিতে বসতি স্থাপন করে। বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গল কেটে স্থানটিকে তারা চাষাবাদের উপযোগী করে তোলে। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সেখানেও তাদের মালিকানার দাবি নিয়ে হাজির হয়। সাঁওতালরা ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং নিজেদের প্রাকৃতিক অধিকার বজায় রাখার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়।
সাঁওতালরা বিশ্বাস করত, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম জঙ্গল কেটে জমি চাষের উপযোগী করে, জমির মালিকানা তারই। মোগল সম্রাটরা এ ঐতিহ্যকে সম্মান করায় তখন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাস্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে জমিদাররা জমির উপর তাদের মালিকানার দাবি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।
এই স্বাভাবিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ১৮১১, ১৮২০ ও ১৮৩১ সালে সাঁওতালদের মধ্যে বৃটিশ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ, সুসংগঠিত ও ব্যাপক বিদ্রোহটি সংঘটিত হয় ১৮৫৫-৫৬ সালে এবং তা দমন করতে সরকারকে কয়েক দফা সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে হয়।
সাঁওতালরা বাঙালিদের ‘মইরা’ ও ‘দিকু’ নামে ডাকত এবং তাদের শত্রু মনে করত। কেননা এ বাঙালিরাই ছিল জমিদার, মহাজন, দোকানদার ও রেলওয়ে শ্রমিক-ঠিকাদার, যারা কমবেশি সবাই ছিল শোষক ও নির্যাতনকারী।
এসব মইরা ও দিকুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাঁওতালরা ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে সংগঠিত হতে শুরু করে। যখন সাঁওতাল নেতা বীর সিংহকে পাকুড় রাজের কাচারিতে তলব করে তার অনুসারীদের সামনে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করে শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়, তখনই শুরু হয় মূল বিদ্রোহ। একতা ও শক্তির প্রতীক হিসেবে গৃহীত শাল বৃক্ষ স্পর্শ করে সাঁওতালরা শপথ গ্রহণ করে।
১৮৫৫ সালের জুন মাস থেকে বিদ্রোহ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ গণঅভ্যুত্থানের মতো সাঁওতালরাও গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে। ডাক ও রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তাদের এলাকা থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং রেলওয়ে শ্রমিক নিয়োগকারী ঠিকাদার, যারা সাঁওতাল মেয়েদের ফুসলিয়ে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করত, তাদেরকে পাওয়ামাত্র হত্যা করা হয়। জমিদারকে খাজনা প্রদান পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মহাজনের তমসুক বা বন্ধকীপত্র এক ঘোষণার দ্বারা বাতিল করা হয়।
পিপলিতে সাঁওতালরা মেজর বারোজের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভিযানকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে। এ বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে সাঁওতালরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালের ১৯ জুলাই সামরিক আইন জারি করা হয়। সাঁওতালদের দমনের জন্য তিনটি সৈন্যদল পাঠানো হয়। সাঁওতালদের রক্তে সিক্ত হয় রাজমহল পার্বত্য এলাকা। তাদের সবকটি গ্রাম ধ্বংস করা হয়। বন্দি সাঁওতালদের শিকলবদ্ধ অবস্থায় রেলপথ নির্মাণের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।
১৮৫৬ সালের ফেব্রয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সাঁওতালদের অধিকাংশই ধরা পড়ে এবং লোক দেখানো বিচার করে তাদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। অবশেষে ১৮৫৬ সালের মার্চে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে সাঁওতালদের পক্ষ থেকে অনুরূপ কোনো বিদ্রোহ যাতে না হয়, সেজন্য জমির মালিকানা স্বত্ত্ব দিয়ে রাজমহল পাহাড়ে বিপুল সংখ্যক মইরা ও দিকুদের বসতির ব্যবস্থা করা হয়।
সাঁওতাল ও মালো
আদিবাসী মালোরা বাংলাদেশে এসেছে ভারতের রাঁচি থেকে। এদের গানেও মিলে তার সত্যতা। ‘রাঁচি থেকে আসলো ঘাসী, তারপর হলো আদিবাসী।’ ব্রিটিশ শাসনামলে রেললাইনের কাজের সূত্র ধরেই এ অঞ্চলে এদের আগমন ঘটে। দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার শীতল গ্রামে মালো পরিবার রয়েছে প্রায় দেড়শটি। এক সময় এদের পূর্ব পুরুষরা বাস করত রংপুরের তাজহাট এলাকায়। কলেরা ও ডায়রিয়া থেকে মুক্তি পেতে বহু বছর পূর্বে এরা এসে বসতি গড়ে শীতল গ্রামে। দিনাজপুর ছাড়াও রংপুর, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি, উচায়, পলি চাঁদপুর, চাঁদপুর, পাথরঘাটা, বীরনগর, বদলগাছী, পাহাড়পুর, নওগাঁ, মহাদেবপুর, মানমাছি, সোনাপুর, চিরিরবন্দর, হিলি, নবাবগঞ্জ, শাহজাদপুর, ধারজুরি, দাউদপুর এবং দিনাজপুর সদরসহ কয়েকটি উপজেলার কিছু অংশে বিভিন্ন এলাকায় মালো অধিবাসীদের বসবাস।
এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার মৃতিঙ্গা চা বাগান, চাটলাপাড়া চা বাগান, দেওয়ানদি চা বাগান, দেওরাছড়া চা বাগান, চম্পাহাড়ি চা বাগান, আলীনগর চা বাগান ও সনচড়া চা বাগানেও মালোরা বাস করেন।
ইংরেজ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা প্রজাদের উপর করের বোঝা বাড়িয়ে দেয়। এতে প্রজারা অসস্তোষ প্রকাশ করে। ফলে বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ আন্দোলনে মালোরাও অংশ নেয় এবং এক সময় জমিদারদের কাছে পরাজিত হয়। ফলে জমিদারদের অধীনে তাদের বন্দি জীবন কাটাতে হতো। এছাড়াও জমিদাররা মালোদের দিয়ে ঘোড়া, মহিষ ও গবাদি পশুর ঘাস কাটার কাজ করাতো। সে কারণে মালোদের ঘাসী বলেও ডাকা হতো। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারদের লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ হিসেবেও কাজ করতো। স্থানীয়রা এদের চিনে নেয় বুনা বা বুনো হিসেবে। আবার অনেকেরই ধারণা, বিহারের মালভূমি ও মালই টিলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিল আছে বলেই এদের মালো নামে ডাকা হয়।
মালোদের গোত্র বিভক্তি তাদের বংশ পরিচয়কেই তুলে ধরে। এদের ১৩টি গোত্র রয়েছে। গোত্রগুলো হচ্ছে পরনদীয়া, নায়েক, খাসোয়ার, খাটোয়ার সিং, দুয়ারসিনী, হেটঘেটিয়া, কার্টাহা, ভূঞা, রাজ, অহীর, ম-লগোত্র, সিমের লেকোয়া প্রভৃতি। এদের সমাজে একই গোত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ। মালো সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। এদের পরিবারে মেয়েরা বাবার কোনো সম্পত্তি পায় না। তবে কোনো পরিবারে বাবা মারা গেলে মা ও বোনদের দেখার দায়িত্ব অবশ্যই বড় ভাইকে পালন করতে হয়।
সাঁওতাল : দিনাজপুর জেলার কাহারোল, বীরগঞ্জ, চিরিরিরবন্দর, ফুলবাড়ী, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাটসহ ১৩টি উপজেলার বেশকিছু এলাকা এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও গাইবান্ধায় অধিক সংখ্যক সাঁওতালদের বসবাস। সাঁওতালি ভাষা অস্ট্রিক ভাষার পরিবারভুক্ত। কোল ও মুন্ডারি ভাষার সঙ্গে সাঁওতালি ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। সাঁওতালদের সংস্কৃতি চর্চায় লিখিত সাহিত্যের বিকাশ না ঘটলেও লোকগীতি ও লোককাহিনী সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। সাঁওতালদের যেমন ভাষা আছে কিন্তু লিখিত বর্ণমালা নেই, তেমনি তাদের ধর্ম আছে কিন্তু কোনো আনুশাসনিক ধর্মগ্রন্থ নেই। বর্তমান খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা তাদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হচ্ছে। দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ সাঁওতাল ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের নিজস্ব একটি ধর্ম রয়েছে। তবে তার নির্দিষ্ট কোনো নাম পাওয়া যায়নি। এ ধর্ম কিছুটা হিন্দু ও কিছুটা বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্রন বলে মনে হয়। সাঁওতালরা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আদি বাসিন্দা। এরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষি সংস্কৃতির জনক ও ধারক হিসেবে স্বীকৃত। সাঁওতাল সমাজ প্রধানত কৃষিজীবী। কিন্তু আর্থ-সামাজিক কারণে দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। জীবিকা অর্জনে বা কর্মজীবনে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতালদের ঘর ছোট, কিন্তু গৃহাঙ্গন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। মাটির দেয়ালে নানারকম কারুকার্য চিত্র। সাঁওতাল নারীর সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও শিল্পমনের পরিচয় তুলে ধরে। ঘরের আসবারপত্র খুবই সাদামাটা যা তাদের সরল জীবনরীতির পরিচায়ক। সাঁওতাল সমাজ বর্তমান সময়ও ঐতিহ্যবাহী পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় পরিচালিত এবং গ্রাম প্রধানরা বিশেষ মর্যাদা ভোগ করে থাকে।
সাঁওতালদের মধ্যে ১২টি গোত্র বিভাগ রয়েছে। কিস্কু, হাঁসদা, মুর্মু, হেমব্রম, মার্ডি, সরেন, টুডু, বাস্কে, বেশরা, চঁড়ে, পাঁউরিয়া ও বেদেয়া। সাধারণ নিয়মে একই গোত্রের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু এসব অনুশাসন এখন ততটা সচল নয়।
পাহাড়ি উপজাতি
পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে ১১টি ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী। এরা হচ্ছে মারমা, চাকমা, মুরং, ত্রিপুরা, লুসাই, খুমি, বম, খেয়াং, চাক, পাংখোয়া ও তংচংগ্যা। এ ১১টি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে একমাত্র বান্দরবান জেলাতে।
বান্দরবান জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হলো মারমা। তারা মূলত ম্রাইমা নামে বার্মা থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে বান্দরবানে। বান্দরবানের দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুরং (ম্রো) সম্প্রদায়। তারা বার্মার আরাকান রাজ্য থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খুমীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে এসে বসতি গড়ে তোলে।
এ জেলায় আরেক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হল ত্রিপুরা, যদিও খাগড়াছড়িতে তাদের সংখ্যা বেশি। ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মানুষ মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। তাদের আদি নিবাস ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। এ জেলায় তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীও কম নয়। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজ চাকমাদের একটি উপশাখা হলেও তারা তা অস্বীকার করে নিজেদের পৃথক জাতিসত্ত্বারুপে মনে করে।
খিয়াংরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ এলাকায় আসে। তারা আরাকানের উমাতাং অঞ্চলে বসবাস করত। চাকরা আরাকান থেকে এ অঞ্চলে আসে। এদের আদীবাস চীনের যুনান প্রদেশে। পাংখোরা জনগোষ্ঠী ভারতের লুসাই পাহাড় ও মিজোরাম হতে এ অঞ্চলে আসে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এসেছে পাশ্ববর্তী দেশ বার্মা, চীন, ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে। সে কারণে এ এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আদিবাসীদেরও মিল পাওয়া যায়।
খুমি বান্দরবানের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। খুমি নামটির অর্থ হলো সর্বোত্তম জাতি। আরাকানীরা এদের খেমি জাতি বলে অভিহিত করে থাকে। ১৭০০ শতকের শেষভাগে খুমি উপজাতি আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করে।
এ জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে আলাদা আলাদা ভাষা ও সংস্কৃতি। এদের অনেক রীতিনীতি, কৃষ্টি, সামাজিক জীবনাচার ও গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মহামান্বিত ও বৈচিত্র্যময় করেছে। এক সময়ের প্রচলিত রাজ প্রথা ও রাজ পূণ্যাহ অনুষ্ঠান আছে।
বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায়ের বড় উৎসব হলো বর্ষবরণ যা তাদের ভাষায় সাংগ্রাই উৎসব নামে পরিচিত। এছাড়া অন্যান্য উৎসবের মধ্যে রয়েছে ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে। তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব বিঝু। এছাড়া অন্যান্য ধর্মালম্বীরা ও বছরে বিভিন্ন সময়ে নিজ সংস্কৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উৎসব পালন করে আসছে।
পোশাক-পরিচ্ছদও অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিল্প মননশীলতার পরিচয় মেলে। চাকমাদের পিনন-খাদি, মারমাদের লুঙ্গি-থামি শিল্পকলার পরিচয় বহন করে।
সাঁওতাল বিদ্রোহ
১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ১০ হাজার সাঁওতাল কৃষকের জমায়েত হয়েছিল ভারতের দামিন-ই-কোহ এলাকায়। তাদের দাবি ছিল, ‘জমি চাই, মুক্তি চাই’। যা থেকে শুরু হয় বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ এক সময় হয়ে উঠেছিল সব সম্প্রদায়ের মানুষের মুক্তিযুদ্ধ। ইতিহাসে যেটাকে বলে সাঁওতাল বিদ্রোহ।
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের এ দেশীয় দালাল সামন্ত-জমিদার, সুদখোর ও তাদের লাঠিয়াল বাহিনী, দারোগা-পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতাল নেতা সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব- এ চার ভাইয়ের নেতৃত্বে রুখে দাঁড়ায় সাঁওতালরা।
ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত আইন ও বিধিবিধান, খাজনা প্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথম দিকে সাঁওতালরা তাদের আদি বাসভূমি কটক, ধলভূম, মানভূম, বড়ভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ও বীরভূমের পার্বত্য এলাকা ছেড়ে রাজমহল পাহাড়ের সমতলভূমিতে বসতি স্থাপন করে। বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গল কেটে স্থানটিকে তারা চাষাবাদের উপযোগী করে তোলে। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সেখানেও তাদের মালিকানার দাবি নিয়ে হাজির হয়। সাঁওতালরা ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং নিজেদের প্রাকৃতিক অধিকার বজায় রাখার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়।
সাঁওতালরা বিশ্বাস করত, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম জঙ্গল কেটে জমি চাষের উপযোগী করে, জমির মালিকানা তারই। মোগল সম্রাটরা এ ঐতিহ্যকে সম্মান করায় তখন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাস্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে জমিদাররা জমির উপর তাদের মালিকানার দাবি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।
এই স্বাভাবিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ১৮১১, ১৮২০ ও ১৮৩১ সালে সাঁওতালদের মধ্যে বৃটিশ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ, সুসংগঠিত ও ব্যাপক বিদ্রোহটি সংঘটিত হয় ১৮৫৫-৫৬ সালে এবং তা দমন করতে সরকারকে কয়েক দফা সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে হয়।
সাঁওতালরা বাঙালিদের ‘মইরা’ ও ‘দিকু’ নামে ডাকত এবং তাদের শত্রু মনে করত। কেননা এ বাঙালিরাই ছিল জমিদার, মহাজন, দোকানদার ও রেলওয়ে শ্রমিক-ঠিকাদার, যারা কমবেশি সবাই ছিল শোষক ও নির্যাতনকারী।
এসব মইরা ও দিকুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাঁওতালরা ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে সংগঠিত হতে শুরু করে। যখন সাঁওতাল নেতা বীর সিংহকে পাকুড় রাজের কাচারিতে তলব করে তার অনুসারীদের সামনে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করে শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়, তখনই শুরু হয় মূল বিদ্রোহ। একতা ও শক্তির প্রতীক হিসেবে গৃহীত শাল বৃক্ষ স্পর্শ করে সাঁওতালরা শপথ গ্রহণ করে।
১৮৫৫ সালের জুন মাস থেকে বিদ্রোহ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ গণঅভ্যুত্থানের মতো সাঁওতালরাও গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে। ডাক ও রেলওয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তাদের এলাকা থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং রেলওয়ে শ্রমিক নিয়োগকারী ঠিকাদার, যারা সাঁওতাল মেয়েদের ফুসলিয়ে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করত, তাদেরকে পাওয়ামাত্র হত্যা করা হয়। জমিদারকে খাজনা প্রদান পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মহাজনের তমসুক বা বন্ধকীপত্র এক ঘোষণার দ্বারা বাতিল করা হয়।
পিপলিতে সাঁওতালরা মেজর বারোজের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক অভিযানকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে। এ বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে সাঁওতালরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালের ১৯ জুলাই সামরিক আইন জারি করা হয়। সাঁওতালদের দমনের জন্য তিনটি সৈন্যদল পাঠানো হয়। সাঁওতালদের রক্তে সিক্ত হয় রাজমহল পার্বত্য এলাকা। তাদের সবকটি গ্রাম ধ্বংস করা হয়। বন্দি সাঁওতালদের শিকলবদ্ধ অবস্থায় রেলপথ নির্মাণের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।
১৮৫৬ সালের ফেব্রয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সাঁওতালদের অধিকাংশই ধরা পড়ে এবং লোক দেখানো বিচার করে তাদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। অবশেষে ১৮৫৬ সালের মার্চে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে সাঁওতালদের পক্ষ থেকে অনুরূপ কোনো বিদ্রোহ যাতে না হয়, সেজন্য জমির মালিকানা স্বত্ত্ব দিয়ে রাজমহল পাহাড়ে বিপুল সংখ্যক মইরা ও দিকুদের বসতির ব্যবস্থা করা হয়।
এ বিভাগের অন্যান্য সংবাদ