বিজয় অর্জনের গৌরবগাথা
বিবিধ ডেস্ক
🕐 ১:২৭ অপরাহ্ণ, ডিসেম্বর ১৬, ২০১৯
আজ মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করেছে পাকহানাদার বাহিনী। চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশের বিজয়ের সংবাদ যখন প্রকাশিত হয়েছে পত্রপত্রিকায়, সেই সময় বিজয়ের আনন্দের মধ্যে আত্মদানের গল্পগুলোও ফিরেছে মানুষের মুখে মুখে।
গাজীপুর
তানজেরুল ইসলাম
গাজীপুর তৎকালীন জয়দেবপুর হানাদারমুক্ত হয় ১৫ ডিসেম্বর। ১৩-১৪ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা গাজীপুরে সেনানিবাসে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালায়। এতে পাক হানাদার বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে পাকবাহিনী গাজীপুর ছেড়ে পালাতে শুরু করে। জয়দেবপুরের সমরাস্ত্র কারখানা ও রাজেন্দ্রপুর অর্ডিন্যান্স ডিপো থেকে পাক সেনারা ঢাকার পথে চান্দনা চৌরাস্তায় জড়ো হতে থাকে। এ সময় দেশের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ ময়মনসিংহ, শেরপুর ও টাঙ্গাইল থেকেও পাক হানাদাররা চান্দনা চৌরাস্তা থেকে ছয়দানা এলাকা পর্যন্ত জড়ো হতে থাকে। ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর গোলাবর্ষণে পাকবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরে ১৬ ডিসেম্বর ভোররাত থেকে স্বাধীনতার উল্লাস করতে থাকেন মুক্তিযোদ্ধারাসহ মুক্তিকামী জয়দেবপুরবাসী।
টাঙ্গাইল
মহব্বত হোসেন
১৬ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলে শুধু ছিল ‘জয় বাংলা’ স্লোগান। দেশ স্বাধীন হয়েছে। শহরের প্রতিটি রাস্তা আর অলিগলিতে সাধারণ মানুষের আনন্দমুখর মিছিল। তবে ১১ ডিসেম্বরই টাঙ্গাইলের মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়ে যায়। ওইদিন টাঙ্গাইল পাক হানাদার মুক্ত হয়। সেদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের নেতৃত্বে টাঙ্গাইল শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে টাঙ্গাইল পাক হানাদারমুক্ত ঘোষণা করেন মুক্তিযোদ্ধারা। ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিশাল কাদেরিয়া বাহিনী গড়ে ওঠে। এ বাহিনীর সিগনাল গোয়েন্দাপ্রধান বসির উদ্দিন বাচ্চু (ব্যারিস্টার বাচ্চু হিসেবে পরিচিত) ১৬ ডিসেম্বরের অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে বলেন, সেদিন স্রোতের মতো মানুষ ছুটে আসতে থাকে শহরের দিকে। যুদ্ধকালীন সময়ে টাঙ্গাইলের অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী দেশের সীমানা পার হয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।
মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল অঞ্চলে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে রণাঙ্গনে কাদেরিয়া বাহিনীর ১৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও প্রায় ৭০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ছিল। সম্মুখযুদ্ধ আর গেরিলাযুদ্ধ মিলিয়ে অন্তত ৭০টি যুদ্ধে অংশ নেয় কাদেরিয়া বাহিনী। ১২ আগস্ট কাদেরিয়া বাহিনী হানাদারদের অস্ত্রবোঝাই বড় বড় দুটি জাহাজ দখল করে নেয়। এটি জাহাজ মারা যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়। এরপর বাঘা কাদেরের নাম ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। মুক্তিযুদ্ধে এগারটি সেক্টরের বাইরে টাঙ্গাইল অঞ্চলে এই বাহিনী ছিল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আলাদা একটি দল।
১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর পরই দেশ শত্রুমুক্ত করতে টাঙ্গাইলে গঠন করা হয় স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ। চলতে থাকে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ। ২৬ মার্চ গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে টাঙ্গাইল সদর থানায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়।
রাজশাহী
মাসুদ রানা রাব্বানী
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা। ১৬ ডিসেম্বর এসেছিল সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়। কিন্তু রাজশাহীতে স্বাধীনতার সেই সূর্য কিরণের ছোঁয়া লাগে আরও দু’দিন পরে। ১৮ ডিসেম্বর রাজশাহী শহর শত্রুমুক্ত হয়।
মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী ও গেরিলা যোদ্ধাদের ক্রমাগত আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদররা কোণঠাসা হয়ে পড়লেও রাজশাহীতে স্বাধীন দেশের প্রথম পতাকা ওড়ে দুইদিন পর। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় আর আত্মপরিচয়ের ঠিকানা করে নেওয়ার অনুভূতিতে পুলকিত হয়ে ওঠে রাজশাহীর মানুষ। মুক্তিকামী জনতার ঢল নামে প্রতিটি সড়কে।
মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজশাহী অঞ্চল ছিল ৭ নম্বর সেক্টরে। বিদেশি প্রতিনিধিদের পরিস্থিতি জানাতে মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত পার হয়ে আসে। একাত্তরের ১৭ জুন ২৩ জন মুক্তিযোদ্ধা রাজশাহী শহরে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শুরু করেন তাদের অ্যাকশন অপারেশন।
পাকিস্তানি সৈন্য ও দোসরদের নির্যাতন হত্যাযজ্ঞ বাড়তে থাকে। রাজশাহীর নারীরাও অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধে। কেউ সীমান্ত পার হয়ে ভূমিকা রাখলেন, কেউ এ পারেই হয়ে উঠলেন দুঃসাহসিক গেরিলা।
১৮ ডিসেম্বর মুক্ত হয়ে যায় রাজশাহী। রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠে স্বাধীন বাংলার পতাকা তোলেন লাল গোলা সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।
রংপুর
সুশান্ত ভৌমিক
রংপুর বিভাগের আট জেলায় মহান বিজয় দিবসকে সামনে রেখে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ। র্যালিসহ বিভিন্ন আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোসররা ভীত হয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে।
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর দেশের মানুষ প্রস্তুতি গ্রহণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের। এরই অংশ হিসেবে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্বাধীনতাকামী মানুষ। দিনক্ষণ ঠিক হয় ২৮ মার্চ। ঘেরাও অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রংপুরের বিভিন্ন হাট-বাজারে ঢোল পেটানো হয়। আর এ আহ্বানে অভূতপূর্ব সারা মেলে। সাজ সাজ রব পড়ে যায় চারদিকে। যার যা আছে তাই নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয় এ অঞ্চলের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ছাত্র, কৃষক, দিনমজুরসহ সব পেশার সংগ্রামী মানুষ। রংপুরের আদিবাসীরাও তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকে। এক্ষেত্রে মিঠাপুকুর উপজেলার ওরাঁও সম্প্রদায়ের তীরন্দাজ সাঁওতালদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।
নীলফামারী রংপুর অঞ্চলেরই একটি মহকুমা শহর, মুক্তিযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নীলফামারীর অগণিত ছাত্র-জনতা ও সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম শুরু করে। মিটিং, মিছিল ও সভা সমাবেশ হতে থাকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ শুরু হয় এবং শুরু হয় প্রতিরোধ। মহকুমা শহরে রক্ষিত অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ট্রেনিং শুরু হয়। নীলফামারী ৬টি থানা নিয়ে একটি মহকুমা শহর।
৫ এপ্রিল ইপিআর, আনসার ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ হাজার হাজার জনতা ছুরি, বল্লম, বন্দুক, লাঠি নিয়ে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্য এগিয়ে যেতে থাকে। পাক সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্য সৈয়দপুর থেকে নীলফামারী পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে বাংকার করে ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা অপেক্ষা করেন। ৭ এপ্রিল সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক সেনারা ট্যাংক, কামান ও ভারী অস্ত্র নিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে নীলফামারী শহরের দিকে আসতে থাকে।
পাক সেনারা আসার পথে শত শত বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। এ সময় ৬নং সেক্টরের অধীন পাকসেনাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে গেরিলা আক্রমণ শুরু করেন মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। পাক সেনারা পরাস্ত হয়ে পিছু হটতে শুরু করে। ১৩ ডিসেম্বর পাক সেনারা শহরের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং নীলফামারী শহর মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও হাজার হাজার জনতা নীলফামারী শহরে আনন্দ মিছিল করে।
চট্টগ্রাম
মোহাম্মদ ওয়াজেদ
১০ ডিসেম্বর মিরসরাই মুক্ত হয় এবং সেক্টর কমান্ডারের হেড কোয়ার্টার মিরসরাই নিয়ে আসা হয়। ১১ ডিসেম্বর সীতাকু-ে পাকিস্তানি প্রতিরোধ চূর্ণ করে বাংলাদেশ বাহিনী চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় কুমিল্লা-চাঁন্দপুর ফ্রন্টে লাকসাম এলাকামুক্ত করে ব্রিগেডিয়ার সান্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ৮৩ ব্রিগেড চট্টগ্রাম দখলের অভিযানে বাংলাদেশ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও মিত্রবাহিনী কুমিরায় পাকিস্তানি ডিফেন্সের সীমানায় পৌঁছে যায়। কুমিরায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে একটি গভীর খালের ওপরে থাকা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানিরা ব্রিজের দক্ষিণে রাস্তার দু’পাশে শক্তিশালী ডিফেন্স তৈরি করেছিল। রাস্তার পূর্বপাশে পাহাড়ের যক্ষ্মা হাসপাতালে তাদের ভারী মেশিনগান তাক করা ছিল। ১৪ ডিসেম্বর গভীর রাত পর্যন্ত এখানে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যৌথ বাহিনীর তুমুল লড়াই চলে। ভোর ৩টায় যৌথ বাহিনী কুমিরা মুক্ত করতে সক্ষম হয়।’ ১৫ ডিসেম্বর কুমিরার দক্ষিণে পাকিস্তানের কতগুলো অস্থায়ী ডিফেন্স ভেঙে যৌথবাহিনী ভাটিয়ারিতে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রবল প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরি করেছিল। এখানে ১৬ ডিসেম্বর প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। ১৭ ডিসেম্বর সকাল সোয়া ৯টায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।
খুলনা
মো. জামাল হোসেন
মুক্তিযুদ্ধের শেষ সপ্তাহে কোণঠাসা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে জনসম্মুখে আত্মসমর্পণ করেন রেসকোর্স ময়দানে। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুক্ত হয় বাংলাদেশ। ঠিক ওই সময় ব্রিগেডিয়ার হায়াত খানের নেতৃত্বে ৪ সহস্রাধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনারা ‘শিরোমণি ট্যাঙ্ক যুদ্ধ’ নামের বৃহৎ প্রতিরোধের যুদ্ধে মুখোমুখি হয়।
১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও ঠিক ওই সময় একটি বৃহৎ প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয় মুক্তিবাহিনী। ১৬ ডিসেম্বর রাতে খুলনা কেঁপেছে ট্যাংক, কামান, বোমা ও গোলাবারুদের আঘাতে। এসময় পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ হয় খুলনার শিরোমণি, গল্লামারী রেডিও স্টেশন (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা), লায়ন্স স্কুল, বয়রার পোস্ট মাস্টার জেনারেলের কলোনি এলাকা, ৭ নম্বর জেটি এলাকা, নূরনগর ওয়াপদা (পানি উন্নয়ন বোর্ড) ভবন, গোয়ালপাড়া, গোয়ালখালি, দৌলতপুর, টুটপাড়া, নিউ ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনসহ বিভিন্ন এলাকায়। শেষ রাতে খুলনায় প্রবেশ পথে গল্লামারীতে যে যুদ্ধ হয় তাতে ২ জন মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মকভাবে আহত হন।
১৭ ডিসেম্বর ভোরে শিপইয়ার্ডের কাছে রূপসা নদীতে বটিয়াঘাটা ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি লঞ্চ এসে পৌঁছে। কিন্তু শিপইয়ার্ডের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা পাকসেনারা লঞ্চটির ওপর আক্রমণ চালায় এবং গুলিবর্ষণ করে। মুক্তিবাহিনীও লঞ্চ থেকে নেমে শিপইয়ার্ডের ওপারের ধান ক্ষেতে অবস্থান নিয়ে পাল্টা গুলি চালায়। উভয়পক্ষের গুলি বিনিময়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত ও ১৬ জন আহত হন। এ যুদ্ধে পাকবাহিনীরও কয়েকজন নিহত ও আহত হয়।
বরিশাল
এমডি জসিম উদ্দিন
১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিলের আগ পর্যন্ত বরিশাল ছিল হানাদারমুক্ত। বরিশাল শত্রুকবলিত হওয়ার আগেই সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা সরকারের অস্থায়ী সচিবালয়। আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সবাইকে নিয়ে এই সচিবালয় গঠিত হয়। এ ঘাঁটি থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করা হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানোর কাজও হতো এই সচিবালয় থেকে।
যে কোনো মুহূর্তে পাকবাহিনী বরিশাল আক্রমণ করতে পারে এমন খবর বরিশালের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আসতে থাকে। ২৫ এপ্রিল সকালে পাকবাহিনী জল, স্থল ও আকাশ পথে বরিশালের ওপর ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়। প্রথমেই পাকিস্তান নৌ-বাহিনী জুনাহার আক্রমণ করে। জুনাহার নদীর দু’পারে তখন ইরানি ও মাজভী নামে দুটি স্টিমার রাখা হয় এবং সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করছিলেন। অপরদিকে সায়স্থাবাদ এলাকায় আর বরিশাল-ঢাকা সড়ক পথে অবস্থান নেন মুক্তিযোদ্ধারা। গালার আঘাতে স্টিমার ইরানি ও মাজভী ডুবে যায়। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ চালায়। ৩ ঘণ্টা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। পাকসেনাদের ভারী অস্ত্রের মুখে কৌশলগত কারণে মুক্তিবাহিনী পিছিয়ে যায়। তবে ওইদিন বরিশাল শহরে পাকবাহিনী আর ঢুকতে সাহস পায় না। জুনাহার ঘাঁটি আক্রমণের অল্প সময়ের মধ্যে দুপুরে বরিশাল সদর থানার চরবাড়িয়ায় পাকবাহিনী দুটি হেলিকপ্টারে সেনা নিয়ে আসে। জুনাহারে আক্রমণের আধঘণ্টার মধ্যে পাকবাহিনী নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর সমন্বয়ে বরিশাল আক্রমণ করতে থাকে। এসময় তালতলীতে গানবোট নোঙর করে ভারী অস্ত্র দিয়ে গুলিবর্ষণ করে। ওইদিন পাকসেনারা যাকে সামনে পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করে। বসতি ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।
এরপর জুলাই মাস থেকে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবক গেরিলা বাহিনী অস্ত্র নিয়ে বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যাম্প গঠন করেন। মুক্তিযোদ্ধারা শিকারপুর ও দোয়ারিকায় অবস্থনরত পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ করে। ১২৫ জন মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহণে সংঘর্ষ চলে দুপুর পর্যন্ত। ১৩ নভেম্বর মেহেন্দিগঞ্জের পাতারহাট থানা আক্রমণ করেন মুক্তিযোদ্ধরা। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রায় সব থানা মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয়। পাক সেনারা ১৬ নভেম্বর থেকে বরিশাল, পটুয়াখালীর ক্যান্টনমেন্টে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর বরিশাল স্বাধীন হয়।
ময়মনসিংহ
এম. ইদ্রিছ আলী
জাতি হিসেবে বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেশের মুক্তির উদ্দেশে জাতিকে আহ্বান করেন। সে ডাকে সারা দেশের অন্যান্য জায়গার মতো ময়মনসিংহের মানুষও সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের ময়দানে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ময়মনসিংহের তাৎপর্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। যুদ্ধকালে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সন্তান কাদের সিদ্দিকীর ভূমিকা কিংবদন্তিতুল্য।
মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ জেলা বাদে বাকি অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলা ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর এবং নেত্রকোনার সঙ্গে টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জের পশ্চিম অঞ্চল ও কুড়িগ্রামের যমুনার পূর্ব তীর অঞ্চল ছিল ১১নং সেক্টরের অধীন। এর সদর দফতর ছিল মহেন্দ্রগঞ্জে। ৮টি সাব-সেক্টরে বিভাজন করা হয় ১১নং সেক্টরকে। এ সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন নেত্রকোনার কৃতী সন্তান কর্নেল আবু তাহের। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৫ সহস্রাধিক। ভালুকার আফসার উদ্দিন নিজ নামে একটি বাহিনী গঠন করে যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় কোম্পানি গড়ে মুক্তিসেনারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।
২৩ এপ্রিল ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়ে জামালপুর-মুক্তাগাছা হয়ে পাকবাহিনী ময়মনসিংহ দখল করে নেয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে তারা ক্যাম্প স্থাপন করে যুদ্ধের ৯ মাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। দখলদার বাহিনীকে স্থানীয় দালালরা হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, নির্যাতন চালাতে সহযোগিতা করে। পুড়িয়ে দেয় অসংখ্য ঘরবাড়ি। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার বড়গ্রাম গণহত্যা, শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার সোহাগপুর দখলদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
কিন্তু এত কিছুর পরও থামাতে পারেনি মুক্তিকামী বাঙালিদের। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে এ অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকা- ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে মনোবল ভেঙে দুর্বল হতে থাকে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে যায় বহুগুণে। বাড়ে আক্রমণের তীব্রতা। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতায় মরণ কামড় দিয়ে এগোতে থাকেন মুক্তিসেনারা।
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের বেশ আগেই মুক্ত হয়ে যায় ময়মনসিংহ। ৭ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহিনীর সহায়তায় শেরপুর অঞ্চলকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করেন। এইদিনই শেরপুরকে মুক্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পাতাকা উত্তোলন করা হয়। ১০ ডিসেম্বর বিভিন্ন দিক থেকে মুক্তিসেনাদের পাশাপাশি মুক্তিকামী সাধারণ জনতা মিছিল নিয়ে ময়মনসিংহ শহরে জড়ো হন। যৌথবাহিনীর মরণপণ জোড়ালো আক্রমণে টিকতে না পেরে ততদিনে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটেছে। একে একে মুক্ত হতে থাকে ৭ ডিসেম্বর শেরপুর, ৯ ডিসেম্বর নেত্রকোনা, ১০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ ও জামলাপুর। মুক্ত হয় এ অঞ্চল। ১৬ ডিসেম্বর রেডিওর সামনে আত্মসমর্পণের সংবাদ শুনতে অপেক্ষায় থাকেন মানুষ।
১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর আগেই পৌঁছে যায় এ অঞ্চলে। ১৬ ডিসেম্বর সকাল থেকে কী হয় না হয়, আত্মসমর্পণ শেষ হলো কি-না ইত্যাদি সব ধরনের খবর জানতে অধীর অপেক্ষায় থাকেন ময়মনসিংহবাসী। একেকটা রেডিওর সামনে শত শত লোক জড়ো হয়ে পিনপতন নীরবতায় সব খবর শুনতে থাকেন। অবশেষে আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরের খবরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সর্বত্র।
এ বিভাগের অন্যান্য সংবাদ


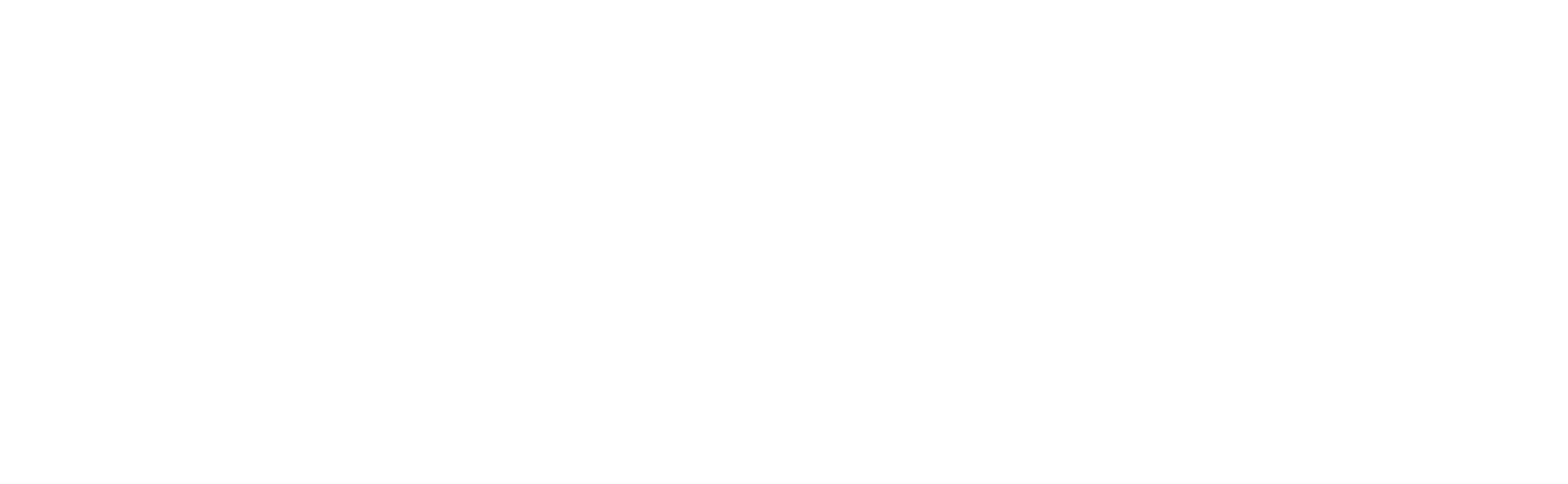


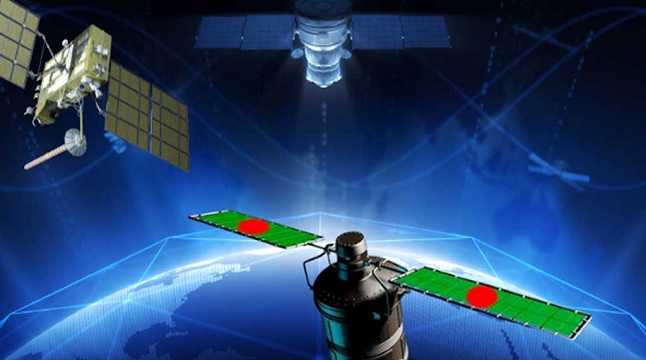




_2.jpg)
.jpg)











